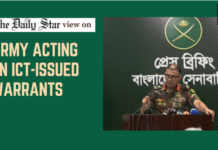ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি খাত অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এই খাতটি বহুদিন ধরে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও জাতীয় গৌরবের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ছিল। কিন্তু খাতটি এখন এ যাবৎকালের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি।
২০২৫ সালে এই খাতে বড় দুটি আঘাত আসে। চীনা স্টার্টআপ ‘ডিপসিক’ জানুয়ারিতে তাদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) মডেল ‘R1’ চালু করে। এটি দ্রুত ডাউনলোডের সংখ্যায় চ্যাট জিপিটিকে ছাড়িয়ে যায়। এ ঘটনাটি নয়াদিল্লিকে গভীর ভাবনায় ফেলে দেয়।
এছাড়া ভারতের বৃহত্তম আইটি কোম্পানি টাটা কনসালট্যান্সি সার্ভিসেস (টিসিএস) জুলাই মাসে তাদের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ছাঁটাইয়ের ঘোষণা দেয়। ২০২৬ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটির ১২ হাজার কর্মী, অর্থাৎ মোট কর্মীদের প্রায় ২ শতাংশ চাকরি হারাবে। এই ঘটনাগুলো আসলে আরো বড় সংকটের ইঙ্গিত দেয়। ভারত তার আইটি খাত থেকে প্রায় ২৮৩ বিলিয়ন ডলার আয় করে।
প্রশ্ন এখন হচ্ছে, এআইয়ের কারণে আইটি খাতে যে বিপর্যয়কর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, ভারত কি তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে? নাকি প্রযুক্তিগত অস্থিরতা ও ভূরাজনৈতিক অনিশ্চয়তার এই ঝড়ে দেশটি হার মেনে বসবে? মনে রাখতে হবে, শুধু এআই ক্ষেত্রে বিপর্যয় নয়, একই সঙ্গে তাদের যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যচাপও সামাল দিতে হবে।
দশকের পর দশক ধরে ভারতের আইটি সেবা খাত উন্নয়নশীল বিশ্বের ঈর্ষার কারণ ছিল। ১৯৯০-এর দশকের অর্থনৈতিক উদারীকরণের পর থেকে এই খাত ইংরেজিভাষী বিপুলসংখ্যক প্রকৌশলীকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বের ‘ব্যাক অফিস’ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
২০২২ সালের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ভারতের মোট সেবা রপ্তানির অর্ধেকেরও বেশি অংশ দখল করে নেয়। এর মাধ্যমে আয়ারল্যান্ডের পর বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম আইটি সেবা রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে ভারত নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। একই সঙ্গে বিশ্ববাজারের ১৫ শতাংশ তাদের দখলে চলে যায়। সাধারণভাবে শিল্পায়নের মাধ্যমে উন্নতি করতে গেলে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, এই খাতটিকে সেসব সমস্যায় পড়তে হয়নি।
উৎপাদনশিল্পের মতো আইটি খাতে বিশাল অবকাঠামোর প্রয়োজন হয় না। শুধু আধুনিক সুযোগ-সুবিধা আছে, এমন কিছু জায়গা হলেই চলে। যেমন : বেঙ্গালুরু ও হায়দরাবাদের সফটওয়্যার পার্কগুলোই এ কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল।
এ খাত কঠোর শ্রম আইনের সীমাবদ্ধতাকেও অতিক্রম করতে পেরেছে। কারণ এ ক্ষেত্রে ভারতের কিছু বিশেষ সুবিধা রয়েছে। এখানে কম খরচে, সহজে প্রশিক্ষণযোগ্য এবং ইংরেজিতে দক্ষ জনবল পাওয়া যায়। এই ব্যাপারটি পূর্ব এশিয়ার লোকদের ভাষাগত দক্ষতার অভাব ও আফ্রিকার জনগণের সার্বিক দক্ষতার ঘাটতির বিপরীতে ভারতকে অনেক এগিয়ে রেখেছিল।
এরপর হার্ডওয়্যার আমদানিতে করমুক্তি ও রপ্তানিতে ভর্তুকির মতো নীতিগুলো এই খাতের উত্থানকে আরো ত্বরান্বিত করে। এর ফলে ‘ইন্ডিয়া ইনক’ এক ধরনের বৈদেশিক মুদ্রা আয়কারী যন্ত্রে পরিণত হয়। প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্য ঘাটতির দীর্ঘস্থায়ী সমস্যাকেও কিছুটা প্রশমিত করে। তবে ভারত কাজের গুণগত মানের চেয়ে পরিমাণের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল। তাদের এই কৌশলটি এখন ভঙ্গুর মনে হচ্ছে।
ভারতের আপাত এই আইটি শক্তির আড়ালে প্রকট উদ্ভাবন ঘাটতির ব্যাপার আছে। ভারত নতুন নতুন উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে খুব একটা মুনশিয়ানা দেখাতে পারেনি। সিলিকন ভ্যালিতে বসে ভারতীয় সিইওরা মাইক্রোসফট, গুগল ও অ্যাডোবির মতো কোম্পানির পরিচালনায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন। কিন্তু ভারত নিজে খুব কম প্রযুক্তিভিত্তিক পণ্য তৈরি করতে পেরেছে।
কোনো ভারতীয় অপারেটিং সিস্টেম, ব্রাউজার বা সামাজিক অ্যাপ পশ্চিমা বা চীনা প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনি। ওয়েবভিত্তিক অনলাইন অফিস স্যুইট ‘জুহু’ এবং ব্যাংকিং সফটওয়্যার ‘ফিনাক্যাল’ নিজ নিজ ক্ষেত্রে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছে; কিন্তু এরা বিরল ব্যতিক্রম মাত্র।
ভারতের গবেষণা ও উন্নয়ন খাতের ব্যয় মোট জিডিপির মাত্র শূন্য দশমিক ৬ থেকে শূন্য দশমিক ৭ শতাংশের মধ্যে সীমিত। এর তুলনায় চীন ব্যয় করে ২ দশমিক ৬৮ শতাংশ এবং যুক্তরাষ্ট্র ৩ দশমিক ৫ শতাংশেরও বেশি। বোঝাই যাচ্ছে, ভারতের বিনিয়োগ এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত কম। ‘সস্তা শ্রম’ নামক সম্পদের অভিশাপেই এই সংকটের সৃষ্টি হয়েছে।
ভারতের কোম্পানিগুলো মজুরির পার্থক্যকে কাজে লাগিয়ে লাভ করে। তারা তুলনামূলকভাবে কম বেতনে প্রোগ্রামার নিয়োগ দেয়, কিন্তু সৃজনশীল দক্ষতাকে কেন্দ্র করে কোনো আলাদা মূল্যায়ন তাদের হয় না। ঘণ্টা অনুযায়ী মজুরি দেওয়ার প্রথা দক্ষতার চেয়ে বরং কম দক্ষ, দীর্ঘক্ষণ ধরে করা কাজের প্রতি-উৎসাহিত করে।
বড় প্রতিভাবান জনশক্তিরা বিদেশে বা বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোয় চলে যায় আর দেশীয় জায়ান্ট যেমন টিসিএসের মতো প্রতিষ্ঠান গবেষণা ও উন্নয়নের চেয়ে ক্লায়েন্ট ব্যবস্থাপনাকেই বেশি গুরুত্ব দেয়। একচেটিয়া ব্যবসায়িক কাঠামো নতুন স্টার্টআপগুলোর বিকাশ রুদ্ধ করে রাখে। এছাড়া ভারতের ভেঞ্চার ইকোসিস্টেমও চীনের তুলনায় খুব দুর্বল।
ডেস্কটপ সফটওয়্যার থেকে শুরু করে মোবাইল অ্যাপ পর্যন্ত প্রতিটি প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রেই ভারত ব্যর্থ হয়েছে। কারণ তারা নতুন উদ্ভাবনের চেয়ে বাইরের প্রযুক্তি আমদানি করেই সন্তুষ্ট থেকেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এই দুর্বলতাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। চ্যাট জিপিটি ও ক্লাউডের মতো টুলসগুলো এখন আইটি আউটসোর্সিংয়ের মূল কাজ—যেমন কোডের ত্রুটি ঠিক করা ও কোয়ারি করা—এগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করছে।
চীনের ডিপসিক-আরওয়ান নাটকীয়ভাবে খরচ কমিয়ে পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে, আর ভারতীয় নির্বাহীরা হাহাকার করে বলছেন, ‘এটা আমাদের দেশ থেকে কেন করা গেল না?’ ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এই মডেলটির ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এর প্রভাবে ভারত জাতীয় এআই কর্মসূচি ত্বরান্বিত করে। এমনকি ডিপসিকের মতো একটি স্থানীয় প্রযুক্তি তৈরির জন্য ১৮ হাজার ৬৯৩টি জিপিইউ একত্র করেছে ভারত।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় দক্ষতার অভাব দেখিয়ে টিসিএসের কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘোষণা থেকে বোঝা যায় পুরো খাতই একটি টালমাটাল অবস্থার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শুল্কনীতি ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের বৈরী অবস্থান। ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের আয়ের অর্ধেকই আসে মার্কিন বাজার থেকে। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন এ বছরের জুলাই থেকে বেশির ভাগ ভারতীয় পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে, যা আগস্টের শেষে দ্বিগুণ হয়ে ৫০ শতাংশে পৌঁছাবে। এই শুল্ক সরাসরি সেবা খাতকে আঘাত না করলেও এর প্রভাব তরঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়বে।
এআইয়ের মাধ্যমে এখন ‘সার্ভিস রিশোরিং’ সম্ভবপর হয়েছে। অর্থাৎ মার্কিন কোম্পানিগুলো নিজেদের দেশেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই কাজ করতে পারবে, যা আগে ভারত থেকে করা হতো। এর ফলে ভারত ব্যাপকভাবে কাজ হারাবে। রাজনৈতিকভাবে এটা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বেশ বিপাকে ফেলছে। আইটি খাতে সরাসরি ৫ দশমিক ৪ মিলিয়ন মানুষ কর্মরত আর পরোক্ষভাবে আরো কয়েক মিলিয়ন মানুষ নির্ভরশীল। এ খাতই ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিচ্ছে।
এই খাতে মন্দা দেখা দিলে বেকারত্ব হঠাৎ বেড়ে যেতে পারে, যা নির্বাচনি সময়ে অস্থিরতা ও অসন্তোষের জন্ম দিতে পারে। অর্থনৈতিকভাবে এই সংকট রুপির মান হ্রাস, মূল্যস্ফীতি ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে চাপ সৃষ্টি করতে পারে। উৎপাদন শিল্পে পিছিয়ে থাকায় এই সংকট সামাল দেওয়ার মতো কোনো অবস্থা ভারতের নেই। যদি এআই ও শুল্কের প্রভাব একসঙ্গে পড়ে, তবে ভারত একটা দক্ষতার সংকটে পড়বে—একদিকে থাকবে অতিরিক্ত ‘কম দক্ষ’ কর্মী, অন্যদিকে তীব্র চাহিদা থাকবে এআইয়ে দক্ষদের জন্য।
নয়াদিল্লির যদিও এ বিষয়টিকে বেশ ভালোভাবেই আমলে নিয়েছে, তবে দেশটির সীমাবদ্ধতাও স্পষ্ট। সরকারের এআই কর্মসূচি বহু ভাষাভিত্তিক মডেল তৈরিতে মনোযোগ দিচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় কম্পিউটিং শক্তির জন্য দেশীয় এআই কোম্পানিগুলোর সঙ্গে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে কাজ করছে। তবু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গবেষক নয়, মূলত কোডার তৈরি করছে।
আর সরকারি জটিলতা বা আমলাতান্ত্রিক বাধা উদ্ভাবনকে ব্যাহত করছে। এই পরিস্থিতি বদলাতে হলে, ভারতকে গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে, শ্রম আইনে নমনীয়তা আনতে হবে এবং একটি প্রাণবন্ত স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ভারতের অভাবনীয় সাফল্য মূলত শিল্পায়নের নানা সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার ফল ছিল। কিন্তু এআই এখন নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করছে। ভারতকে এখন সস্তা শ্রমের সুবিধা থেকে বেরিয়ে এসে উদ্ভাবনে গুরুত্ব হবে।
যথাযথ সংস্কার না হলে এই খাত সেকেলে হয়ে পড়ার ঝুঁকিতে থাকবে। ফলে পুরো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তবে সুদূরদর্শী পরিকল্পনা থাকলে ভারত দৃঢ়ভাবে এ সংকট থেকে উঠে আসতে পারে।
গ্লোবাল টাইমস থেকে ভাষান্তর : এইচ এম নাজমুল হুদা