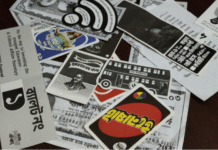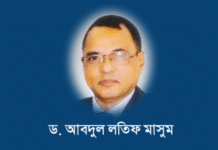Prothom Alo

প্রথম আলোর উপসম্পাদক

নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের বৈঠক বা দেখাসাক্ষাৎ আয়োজনের চেষ্টা বাংলাদেশ বেশ কিছুদিন ধরেই করে যাচ্ছিল। ভারতের তরফে সাড়া পাওয়া যায়নি। গত সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের সময় বাংলাদেশের তরফে এমন চেষ্টার উদ্যোগ ছিল। মার্চে মুহাম্মদ ইউনূসের চীন সফরের আগে মোদির সঙ্গে বৈঠক হোক, সেই চেষ্টাও বাংলাদেশ করেছে, ভারত রা করেনি।
এরপর ব্যাংককে বিমসটেক সম্মেলনের ফাঁকে এমন একটি বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশ ভারতকে অনুরোধ করে। শুরুতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিবৃতি দিয়ে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৈঠকটি হয়েছে। ভারত বৈঠকে বসতে বাধ্য হয়েছে, বিষয়টি নিশ্চয়ই তা নয়, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী মোদি অধ্যাপক ইউনূসের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন।
গত ৫ আগস্ট হাসিনার পতনের পর ভারত যে অবস্থান নিয়েছে, তাতে এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বাংলাদেশের জনগণ তাদের ওপর চেপে বসা দীর্ঘদিনের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়ে যেন বিশাল এক অপরাধ করে ফেলেছে। অথচ ব্যাপারটি হওয়ার কথা ছিল উল্টো। কারণ, ভারত বাংলাদেশে এই স্বৈরশাসন টিকিয়ে রাখতে সরাসরি প্রভাব খাটিয়েছে।
৯ মাস ধরে ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুরাষ্ট্রের মতো আচরণ করছে না। কারণ, শেখ হাসিনার পতনকে ভারত তাদের পররাষ্ট্রনীতি ও কৌশলের সমস্যা বা ভুল হিসেবে বিবেচনা না করে সম্ভবত পরাজয় হিসেবে দেখছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভারতের এই বোধোদয় হচ্ছে না যে বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা একটি দল ও সেই দলের একজন নেতার ওপর ভরসা করা তাদের ঠিক হয়নি। কোনো বড় রাষ্ট্রের এ ধরনের পররাষ্ট্রনীতি বা কৌশল নেওয়ার নজির দেখা যায় না। বাংলাদেশে স্বৈরশাসন টিকিয়ে রাখার নীতি যে তাদের ভুল ছিল, তা ভারত বুঝতে পেরেছে বলেও মনে হয় না।
শেখ হাসিনার পতনের পর তাই তারা উল্টো শক্ত অবস্থান নিয়েছে। বাংলাদেশের নাগরিকদের তারা ভিসা দেওয়া বন্ধ রেখেছে। চিকিৎসার জন্য যারা ভারতে যায়, তাদের জন্যও ভিসা পাওয়া কঠিন হয়ে গেছে। দুই দেশের মধ্যে সরাসরি বাস ও ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ভারতজুড়ে শুরু হয় বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণা। দেশটির অধিকাংশ সংবাদমাধ্যমও এর অংশ হয়ে পড়ে।
মুহাম্মদ ইউনূস ভারতের কাছে যে বিষয়গুলো তুলেছেন, তার মধ্যে হাসিনাকে ফেরত চাওয়া ছাড়া বাকি সব কটি দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা পুরোনো ইস্যু। বিশেষ করে বিভিন্ন সময়ে আশ্বাস দেওয়ার পরও ভারত সীমান্তে হত্যা বন্ধ করেনি। তিস্তার পানি ভাগাভাগি চুক্তি তারা বছরের পর বছর ঝুলিয়ে রেখেছে। গঙ্গার পানি ভাগাভাগি নিয়ে যে চুক্তি হয়েছিল, তার মেয়াদ আগামী বছর শেষ হবে, বাংলাদেশ খুব স্বাভাবিকভাবেই এর নবায়ন চায়।
ভারতের এই রাষ্ট্রীয় অবস্থান সেখানকার জনতুষ্টিবাদী, জাতীয়তাবাদী বা হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির পালে হাওয়া দিচ্ছি ঠিকই, কিন্তু একটি আঞ্চলিক পরাশক্তি হিসেবে এর মধ্য দিয়ে ভারত কূটনৈতিকভাবে কতটা লাভবান হবে, ভবিষ্যৎই তা বলে দেবে।
অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের এমন আচরণের পরও বাংলাদেশ কেন ইউনূস-মোদি বৈঠকে জন্য এতটা তৎপর ছিল, সেই প্রশ্ন কেউ তুলতে পারেন। ভারতে যেমন বাংলাদেশ বিরোধিতা বেড়েছে, বাংলাদেশেও ভারত বিরোধিতা বেড়েছে। এমন একটি পরিস্থিতিতে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করার জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ যে সদিচ্ছা দেখাচ্ছে ও উদ্যোগ নিয়েছে, কূটনৈতিক বিবেচনায় তাকে পরিপক্ব অবস্থান হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ইউনূস-মোদি বৈঠকের ফলাফল কী? বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক যখন সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় চলে এসেছে, তখন এই দুজন একটি বৈঠকে বসেছেন, এটাই সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। বাংলাদেশের দিক থেকে দেখলে বলতে হয়, এই বৈঠক হয়েছে বাংলাদেশের আগ্রহ ও চেষ্টার ফল হিসেবে এবং এর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলাদেশের সদিচ্ছার প্রমাণ দেওয়া গেছে।
বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে ভারত বিরোধিতা থাকলেও সরকারের এই উদ্যোগের প্রতি কোনো বিরোধিতা দেখা যায়নি। অথচ ভারতের কূটনৈতিক মহলের কেউ কেউ বলেছেন, মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে মোদির বৈঠকে বসা ঠিক হয়নি। দ্য টেলিগ্রাফ অনলাইন নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন সাবেক ও অভিজ্ঞ কূটনীতিককে উদ্ধৃত করেছে। একজন বলেছেন, প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে মোদির বৈঠকটি ছিল খারাপ সিদ্ধান্ত।
ইউনূস-মোদি বৈঠকের কিছু দিক আমরা বাংলাদেশ ও ভারতের সংবাদমাধ্যম সূত্রে জেনেছি। এখানেও দুই দেশের সংবাদমাধ্যমের খবরের মধ্যে পাল্টাপাল্টি দেখা গেছে। সবকিছু মিলিয়ে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস কিছু প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদিও ভারতের পক্ষ থেকে কিছু বিষয় তুলে ধরেছেন। এখানে নতুন কোনো ইস্যু নেই, কিন্তু কোন বিষয়গুলো তাঁরা তুলবেন, তা নিয়ে কৌতূহল ছিল।
মুহাম্মদ ইউনূস ভারতে আশ্রয় নেওয়া শেখ হাসিনাকে ফেরত চেয়েছেন, সীমান্তে হত্যা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন, গঙ্গার পানি ভাগাভাগি চুক্তির নবায়ন ও তিস্তা চুক্তি বাস্তবায়নের প্রসঙ্গ তুলেছেন।
অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী মোদি বাংলাদেশের সংখ্যালঘু, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিয়ে ভারতের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি ভবিষ্যতে একটি গণতান্ত্রিক, স্থিতিশীল, শান্তিপূর্ণ, প্রগতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ দেখতে চেয়েছেন।
মুহাম্মদ ইউনূস ভারতের কাছে যে বিষয়গুলো তুলেছেন, তার মধ্যে হাসিনাকে ফেরত চাওয়া ছাড়া বাকি সব কটি দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা পুরোনো ইস্যু। বিশেষ করে বিভিন্ন সময়ে আশ্বাস দেওয়ার পরও ভারত সীমান্তে হত্যা বন্ধ করেনি। তিস্তার পানি ভাগাভাগি চুক্তি তারা বছরের পর বছর ঝুলিয়ে রেখেছে। গঙ্গার পানি ভাগাভাগি নিয়ে যে চুক্তি হয়েছিল, তার মেয়াদ আগামী বছর শেষ হবে, বাংলাদেশ খুব স্বাভাবিকভাবেই এর নবায়ন চায়।

সীমান্ত হত্যা বা তিস্তা চুক্তির মতো সমস্যাগুলো ভারত দ্রুত সমাধান করবে, এমন আশা বাংলাদেশের জনগণ করে না। এগুলো অনেক দিনের সমস্যা এবং এসব সমস্যা নিয়েই পতিত স্বৈরাচারি সরকার ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ‘সর্বোচ্চ পর্যায়’ পার করেছে। বাকি থাকে হাসিনাকে ফেরত দেওয়া। বাংলাদেশের এই অনুরোধ ভারত রাখবে বলে মনে হয় না। এমন একটি পরিস্থিতিতেও সম্পর্ককে সর্বোচ্চ পর্যায়ে না হোক অন্তত স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। বাংলাদেশ তার সদিচ্ছা দেখিয়েছে, বিষয়টি এখন নির্ভর করছে ভারতের ওপর।
মোদি বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিশেষ করে হিন্দুদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি করেন এবং ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ হিন্দু, ফলে তাঁর উদ্বেগের বিষয়টি না বোঝার কিছু নেই। আর বাস্তবতা হচ্ছে রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক যেকোনো বিবেচনাতেই হোক ৫ আগস্টের পর বাংলাদেশে হিন্দু জনগোষ্ঠী এবং তাদের সম্পত্তির ওপর কিছু হামলার ঘটনা ঘটেছে। বাংলাদেশ সরকারের আপত্তি হচ্ছে, যে মাত্রায় বলা হচ্ছে, তা হয়নি।
এখানে ভারতীয় বন্ধুদের এটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভালো যে বিগত হাসিনা সরকারের আমলেও নানা সময়ে দুঃখজনকভাবে এ ধরনের সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে কিন্তু ভারতকে তা নিয়ে তখন এই মাত্রায় সোচ্চার দেখা যায়নি। তবে তখন ভারত চুপ ছিল বলে এখন উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারবে না, তা নয়। ভারতের উদ্বেগ অবশ্যই বিবেচনায় নেওয়ার মতো। মুহাম্মদ ইউনূস তাই ভারতীয় সাংবাদিকদের বাংলাদেশে এসে পরিস্থিতি সরেজমিন দেখার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।
তবে সংখ্যালঘুদের প্রতি ভারত এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্বেগ বাংলাদেশের মানুষের মনে কিছু প্রশ্ন জাগায়। ভারতে সংখ্যালঘুদের কী অবস্থা? সেখানে সবাই নিরাপদ তো? বাংলাদেশের হিন্দুদের নিয়ে যেমন ভারতের উদ্বেগ আছে, মোদির সঙ্গে বৈঠকে ইউনূস তা না তুললেও ভারতের মুসলমান বা সেখানকার সংখ্যালঘুদের নিয়ে বাংলাদেশের মানুষেরও উদ্বেগ আছে।
বাংলাদেশের জনগণের চোখকান খোলা। তারা দেখছে, বিজেপি সরকার ওয়াক্ফ আইনে বদল এনেছে এবং তা নিয়ে ভারতের মুসলমানরা ক্ষুব্ধ। সেখানকার মুসলমানদের অভিযোগ, মুসলিম সম্প্রদায়ের ওয়াক্ফ বোর্ডের সম্পত্তি সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিতেই এই বিল পাস করা হয়েছে। আম আদমি দলের পার্লামেন্ট সদস্য সঞ্জয় সিংয়ের ভাষায়, এই আইনের মাধ্যমে মসজিদ ও দরগার সম্পত্তি দখলের প্রক্রিয়া শুরু হবে।
আগেও এক লেখায় যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডমের (ইউএসসিআইআরএফ) সূচকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম ভারতের ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রসঙ্গে। এবার তারা ২০২৫ সালের প্রতিবেদন দিয়েছে। সেখানে বাংলাদেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা খর্বের প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থা ততটা খারাপ নয়, যতটা শোচনীয় ভারতের। সেখানে ভারতকে রাখা হয়েছে ‘বিশেষভাবে উদ্বেগের’ দেশের তালিকায়।
সেই প্রতিবেদনে ভারতসহ কয়েকটি দেশের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি, ভিসা কড়াকড়ি আরোপ, সহায়তা বন্ধের মতো জোরালো পদক্ষেপ নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। এমনকি সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা ‘র’-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশও করা হয়েছে।
মোদি একটি গণতান্ত্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ দেখতে চেয়েছেন। খুবই ভালো চাওয়া। তবে ২০১৪ সাল থেকে যদি তিনি এ ব্যাপারে জোরালো প্রত্যাশা করে যেতেন এবং বাংলাদেশে একতরফা নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রকাশ্যে সমর্থন না করতেন, তাহলে হয়তো এ দেশের জনগণকে ১০ বছর ধরে চরম অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরশাসনের মধ্য দিয়ে যেতে হতো না।
ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রি প্রধানমন্ত্রী মোদির অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশের প্রত্যাশার একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ইউনূস-মোদি বৈঠক-পরবর্তী বিশেষ প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, যেকোনো গণতন্ত্রে নিয়মিত অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন খুব জরুরি একটি ব্যাপার। আমাদের প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়েও অধ্যাপক ইউনূসকে অবগত করেছেন। আমাদের প্রশ্ন, বাংলাদেশে যে হাসিনার আমলে তিনটি একতরফা নির্বাচন হলো তখন কি ভারতের কাছে মনে হয়নি যে গণতন্ত্রে ‘অন্তর্ভুক্তিমূলক’ নির্বাচন দরকার?
বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের এই দ্বিমুখী অবস্থানের পরও বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ব্যাপারে সদিচ্ছা দেখিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের এই আগ্রহকে শেষ পর্যন্ত ভারত উপেক্ষা করতে পারেনি বলেই সম্ভবত ইউনূস-মোদি বৈঠক হয়েছে। একে আমরা সম্পর্ক স্বাভাবিক করার সূচনা হিসেবে দেখতে পারি। আগেই বলেছি, বাকিটা এখন নির্ভর করছে ভারতের ওপর।
- একেএম জাকারিয়া প্রথম আলোর উপসম্পাদক। ই–মেইল: akmzakaria@gmail.com