
ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী শাসনের পতনের পর সংবিধান সংস্কার নিয়ে আলোচনা নতুন গতি পেয়েছে। এর কারণ হলো, বিদ্যমান সংবিধানকে সুবিধামতো ব্যবহার করেই এই স্বৈরাচারী শাসন তার আইনি বৈধতা তৈরি করেছিল। স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার বিরোধিতা, অর্থাৎ গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা থেকেই সংবিধান সংস্কারের বিষয়টি এখন গুরুত্বসহকারে সামনে এসেছে।
সংবিধান পরিবর্তনের অতীত অভিজ্ঞতা
১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পর বাহাত্তরের সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। এ কারণে বাহাত্তরের সংবিধান নিয়ে অনেকেরই মধ্যেই একধরনের আবেগ-অনুভূতি লক্ষ করা যায়। পরিহাসের বিষয় হলো, এ সংবিধান খুব বেশি দিন অপরিবর্তনীয় ছিল না। প্রথম আওয়ামী লীগ আমলেই (১৯৭২-১৯৭৫) সংবিধান কাটাছেঁড়া করা শুরু হয়।
বাংলাদেশে সংবিধান সংশোধনের প্রক্রিয়া ও এর প্রেক্ষাপট থেকে স্পষ্ট, এসব সংশোধনীর মধ্যে কয়েকটি পরিবর্তন ছিল ‘নির্দোষ’ এবং বাস্তব সমস্যার সমাধানে এসব সংশোধনী করা হয়েছে। অন্য সংশোধনীগুলো আনা হয়েছিল ক্ষমতাসীনদের স্বার্থে।
বাংলাদেশের রাজনীতিতে গণতন্ত্রের সংকট, একদলীয় শাসনব্যবস্থা, সামরিক শাসন, সরকারগুলোর কর্তৃত্ববাদী প্রবণতা—এ সবকিছুই সংবিধানের পরির্তনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। কখনো কখনো শুধু দলীয় স্বার্থে রাজনৈতিক ঐকমত্য ছাড়া সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। এ কারণে সংকট তৈরি হয়েছে, একতরফা ও প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন হয়েছে এবং নির্বাচনব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে।
এসব সংকটের একটি সমাধান হিসেবেই মানুষের মধ্যে সংবিধানে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে। সংবিধানের যেকোনো পরিবর্তন দেশ ও জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে হওয়া উচিত। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, সুষ্ঠু নির্বাচন ও ভোটাধিকার নিশ্চিত করবে—সংবিধানের এমন পরিবর্তনই আমাদের কাম্য।
সংবিধান সংশোধন, না নতুনভাবে প্রণয়ন
গণ–অভ্যুত্থানের পর সংবিধান সংশোধন, পুনর্লিখন কিংবা পুরোপুরি বাদ দিয়ে নতুনভাবে প্রণয়ন—এ রকম কয়েকটি বিকল্প নিয়ে এরই মধ্যে নানা মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। কেউ কেউ বাহাত্তরের সংবিধানকে ভিত্তি ধরেই পরিবর্তনের পক্ষে, কেউ আবার নতুনভাবে সংবিধান প্রণয়নের কথা বলছেন।
সংবিধান সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পাওয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক আলী রীয়াজ গত ২৯ আগস্ট ঢাকায় অনুষ্ঠিত একটি সংলাপ অনুষ্ঠানে সংবিধান পুনর্লিখন নিয়ে তাঁর মতামত জানিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ‘সংবিধান পুনর্লিখনের কথা বলছি এই কারণে যে সংবিধান সংশোধনের উপায় নেই। বর্তমান সংবিধান সংশোধনের উপায় সীমিত। কারণ, সংবিধানের এক-তৃতীয়াংশ এমনভাবে লেখা যে, তাতে হাতই দেওয়া যাবে না। এর মধ্যে এমন সব বিষয় আছে, যেগুলো না সরালে কোনো কিছুই করতে পারবেন না। এ কারণে পুনর্লিখন শব্দটা আসছে। পুনর্লিখনের পথ হিসেবে গণপরিষদের কথা বলছি। আর কোনো পথ আছে কি না, আমি জানি না।’(সমকাল, ২৯ আগস্ট ২০২৪)
লক্ষণীয় হলো, আওয়ামী লীগ আমলে ২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনী পাস করা হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে বাহাত্তরের সংবিধানের অনেক কিছু ফিরিয়ে আনা হয়েছে—আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এমন দাবি করা হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পঞ্চদশ সংশোধনী ছিল আওয়ামী লীগের ক্ষমতা চিরস্থায়ীকরণের একটি উদ্যোগ। গত এক-দেড় দশকে স্বৈরাচারী শাসনের মধ্য দিয়ে সেই উদ্যোগ বাস্তবায়নের চেষ্টা আমরা দেখেছি।
এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, শুরু থেকেই বাহাত্তরের সংবিধান রাষ্ট্রের অনেক অগণতান্ত্রিকতার অন্যতম ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। তবে এই সংবিধানের কিছু ইতিবাচক দিকও আছে, যা অস্বীকার করা যায় না।
আসিফ নজরুল সংবিধান বিতর্ক ১৯৭২: গণপরিষদের রাষ্ট্রভাবনা বইয়ে লিখেছেন, ‘…১৯৭২ সালের সংবিধান একটি উন্নত সংবিধান ছিল। কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও এতে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ন্যায়পাল পদ প্রতিষ্ঠার মতো প্রগতিশীল বিধান ছিল; সব ধরনের শোষণমুক্তির উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য ছিল; মৌলিক অধিকার বলবৎ করাকেও একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে বর্ণনা করার বিধান ছিল; মৌলিক নীতিমালার আলোকে সংবিধান ও আইন ব্যাখ্যা করার সম্ভাবনাময় বিধান ছিল, যার অনেক কিছুই সে সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার কোনো সংবিধানে ছিল না। গণতান্ত্রিক পথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ধারণার নতুনত্বও অভিব্যক্ত হয়েছিল সে সংবিধানে।’
গণ-অভ্যুত্থানে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এখন ‘পুরোনো’ অনেক কিছুকেই পুরোপুরি ‘বাতিল’ বা ‘অসংগতিপূর্ণ’ মনে হতে পারে। এতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সমর্থনও পাওয়া যেতে পারে। তবে সংবিধানের ক্ষেত্রে ‘জনমতের চাপে’ বা ‘হুজুগে’ পরিবর্তন’ নয়, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকা দরকার এবং সেটা জনগণের কাছে স্পষ্ট হওয়া উচিত।
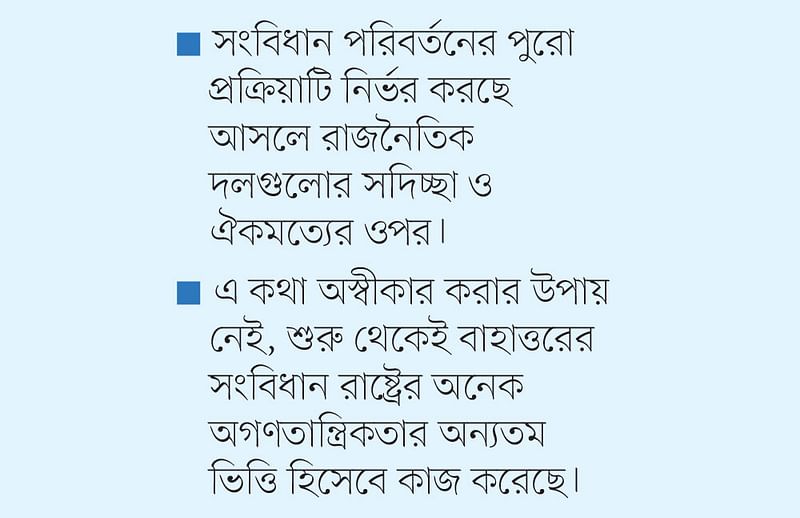
‘পিপলস উইল’ বনাম ‘পপুলিজম’
অনুচ্ছেদ ৭(২) অনুযায়ী, ‘জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে হাসিনার স্বৈরাচারী শাসনের পতনের পর এখন সংবিধান নিয়ে নতুন করে যে আলোচনা শুরু হয়েছে, সেটাকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখতে হবে। তবে এর মধ্যে কিছু আশঙ্কাও রয়েছে।
আশঙ্কা এই কারণে যে দেশে এখন পপুলিজম বা জনতুষ্টিবাদের ব্যাপক জোয়ার বইছে। কোনো কোনো পক্ষ এই জনতুষ্টিবাদী বা পপুলিস্ট চিন্তাভাবনাকে ‘পিপলস উইল’ বা জনগণের আকাঙ্ক্ষা বা অভিপ্রায় হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে বা করবে, এমন ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। তাই যেকোনো দাবি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের চাওয়াকে গুরুত্ব দিলে চলবে না; বরং ন্যায্যতা, সমতা এবং সর্বোপরি গণতন্ত্রের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।
নিখোঁজ গণতন্ত্র: কর্তৃত্ববাদের পথরেখা ও বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বইয়ে অধ্যাপক আলী রীয়াজ গণতন্ত্র নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কিছু কথা বলেছেন। তাঁর মতে, ‘…গণতন্ত্র অর্থ সংখ্যাগুরুর উৎপীড়ন নয়, এমনকি সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনও নয়—গণতন্ত্র হচ্ছে সংখ্যালঘুর রক্ষাকবচ, সহিষ্ণুতার সংস্কৃতি, আইনের চোখে নাগরিকের সমতা, ভিন্নমতের অধিকার, ক্ষমতাসীনদের জবাবদিহির ব্যবস্থা।’
সংবিধান ও গণতন্ত্র
সংবিধান সংশোধন, পুনর্লিখন কিংবা পুরোপুরি বাদ দিয়ে নতুনভাবে প্রণয়ন, যে পদ্ধতিতেই সংবিধান পরিবর্তন করা হোক, এর মূল উদ্দেশ্য হতে হবে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান কায়েম করা। অর্থাৎ দেশের গণতন্ত্র ও নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করা।
গণতান্ত্রিক সংবিধানের মৌলিক ভিত্তি হচ্ছে জনগণের স্বাধীন ও সার্বভৌম সত্তার বিকাশ উপযোগী কিছু সাধারণ রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ করা। এর ওপরই দাঁড়াবে অন্যান্য আইনকানুন, বিধিবিধান এবং সে অনুসারেই রাষ্ট্র চালিত হবে।
বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী, যিনি আইন বিভাগ অর্থাৎ সংসদের নেতা, তিনিই আবার নির্বাহী বিভাগের (সরকার) প্রধান তথা প্রধানমন্ত্রী হন। বর্তমান সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীকে যে একচ্ছত্র ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তা স্পষ্টতই অগণতান্ত্রিক ও সব ধরনের জবাবদিহির ঊর্ধ্বে। এভাবে এক ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রীর এই একচ্ছত্র ক্ষমতাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বৈরতন্ত্রের জন্ম দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রথম কাজ হলো রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গ—আইন বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি করা।
বর্তমান সংবিধান অনুসারে বিচার বিভাগে ‘দ্বৈত শাসন’ (আইন মন্ত্রণালয় ও সুপ্রিম কোর্ট) থাকায় সরকারের পক্ষে সেখানে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ রয়েছে। গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি, বিচার বিভাগ কার্যত নির্বাহী বিভাগের ইচ্ছাপূরণের হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য প্রকৃত অর্থে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রয়োজন। নিম্ন আদালত থেকে শুরু করে উচ্চ আদালত—সব ক্ষেত্রেই বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতে হবে।
সংবিধান সংশোধন ও আইন পাসের ক্ষেত্রে বর্তমানে সংসদকে সীমাহীন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সংবিধানে এমন নিশ্চয়তা থাকতে হবে, যাতে নাগরিকের মৌলিক অধিকার হরণ করে বা সীমিত করে, এমন কোনো সংশোধনী আনা বা আইন করা যাবে না।
বাংলাদেশে স্বৈরাচারী শাসনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো নির্বাচন ও নির্বাচনব্যবস্থাকে ধ্বংস করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করা। গত কয়েকটি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বিষয়টা স্পষ্ট হয়েছে। তাই সংবিধানে এমন কিছু পরিবর্তন আনতে হবে, যা সুষ্ঠু নির্বাচনের বিষয়টি নিশ্চিত করবে। সে ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার বিষয়টি জোরালোভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।
বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত ৭০ অনুচ্ছেদের মতো কোনো কিছু সংবিধানে রাখা যাবে না। ‘ফ্লোর ক্রসিং’(দল পরিবর্তন) বা অনাস্থা ভোটের মতো নির্দিষ্ট দু-একটি বিষয় ছাড়া সংসদ সদস্যদের দলের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা থাকতে হবে। অর্থাৎ দলের বিরুদ্ধে ভোট দিলে সংসদ সদস্য পদ খারিজ হওয়ার বিধান সংবিধান থেকে বাদ দিতে হবে।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে দেখা গেছে, ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সব দলই ক্ষমতাকে স্থায়ী করতে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে। এর কারণে দেশে রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সংকট তৈরি হয়। রাষ্ট্র পরিণত হয় স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী ব্যবস্থায়। সরকার যদি স্বেচ্ছাচারী হয়, দুর্নীতিবাজ হয়, জনস্বার্থবিরোধী কাজ করে, জনগণের ওপর দমন-পীড়ন চালায়, জাতীয় স্বার্থ বিকিয়ে দেয়, তাহলে জনগণের সাংবিধানিক অধিকার থাকবে সেই সরকারকে উচ্ছেদ বা অপসারণের, সংবিধানেই এটা উল্লেখ থাকতে হবে।
সংবিধানের তৃতীয় ভাগ, অর্থাৎ মৌলিক অধিকার অংশে যেসব অধিকারের কথা বলা হয়েছে (যেমন বাক্স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, চলাফেরার স্বাধীনতা), কোনো অবস্থাতেই সেগুলোর ক্ষেত্রে কোনো শর্ত বা আইনি বিধিনিষেধ আরোপ করা যাবে না।
বর্তমান সংবিধানের ২(ক) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। আবার ১২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দেওয়া হবে না। সংবিধানে একই সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতা ও রাষ্ট্রধর্মের যে অসংগতিপূর্ণ ‘সহাবস্থান’ রয়েছে, এটা স্ববিরোধী ও অসংগতিপূর্ণ। এটাকে সংগতিপূর্ণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ‘ধর্মীয় ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা’ শিরোনামে ‘রাষ্ট্র প্রতিটি ব্যক্তিকে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী নিজ নিজ ধর্ম পালন ও বিশ্বাস ধারনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে’—এমনটা করা যেতে পারে। তাহলে ধর্মনিরপেক্ষতা ও রাষ্ট্রধর্ম নিয়ে বিতর্ক এড়ানো যেতে পারে।
এ দেশে বাঙালি ছাড়াও অন্য জাতিসত্তার মানুষ রয়েছে। তাঁরা অনেক দিন ধরেই তাঁদের নিজ নিজ জাতীয়তা অনুসারে সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবি জানাচ্ছেন। তাঁদের এই দাবির যৌক্তিক সমাধান করতে হবে।
বর্তমান সংবিধানে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কিংবা সরকারি কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠাসহ এসব পদের দায়িত্ব, মেয়াদ ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো সংবিধানে উল্লেখ করার মতো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নয়; এ রকম ‘অপ্রয়োজনীয়’ বিষয় বাদ দেওয়াটাই শ্রেয়।
সংবিধানকে ‘প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন’ বলা হলেও তা অন্য কোনো আইনের সঙ্গে তুলনীয় নয়। এর একটি দার্শনিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি থাকতে হয়। সংবিধানকে কেউ কেউ ‘রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অঙ্গীকার’ বলে অভিহিত করেন। সুতরাং সংবিধানে সেসব বিষয়ই থাকা উচিত, যাতে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটে।
প্রয়োজন রাজনৈতিক ঐকমত্য
সংবিধান সংশোধন এবং পুনর্লিখন বা পুরোপুরি বাদ দিয়ে নতুনভাবে প্রণয়ন করা—এ রকম প্রতিটি বিকল্পের জন্য আলাদা পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। সংবিধান সংশোধনের জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সংসদের দরকার হবে।
অন্যদিকে পুনর্লিখন বা নতুন সংবিধান প্রণয়ন করতে হলে প্রয়োজন হবে গণপরিষদ বা সংবিধান সভার (কনস্টিটিউট অ্যাসেম্বলি)। সে ক্ষেত্রে আগে সংবিধান সভার নির্বাচন কিংবা রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংবিধান সভার সদস্য মনোনয়নের আবশ্যকতা রয়েছে।
একটা বিষয় মনে রাখা উচিত, বর্তমানে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকা অন্তর্বর্তী সরকারের সংবিধান সংশোধন বা পুনর্লিখনের কোনো ম্যান্ডেট নেই। তবে সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে তারা পরিবর্তনের একটি রূপরেখা তুলে ধরতে পারে। সংবিধান সভা বা নির্বাচিত সংসদ সেই রূপরেখার ভিত্তিতে নতুন সংবিধান তৈরি করতে পারবে।
এর ফলে সংবিধান পরিবর্তনের পুরো প্রক্রিয়া নির্ভর করছে আসলে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা ও ঐকমত্যের ওপর। শেষ পর্যন্ত তারা সেই সদিচ্ছা ও ঐকমত্য কতটা দেখাতে পারবে, তা জানার জন্য আমাদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।
prothom alo









