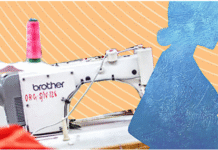ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ : বিশ্বব্যবস্থা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে উত্তাল সময় পার করছে। কোভিড মহামারি শেষ হয়েছে। এরপর ইউক্রেনে হামলার জেরে রাশিয়ার ওপর পশ্চিমা দেশগুলো যেসব বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, সে বিষয়ে সবাই অবগত। তারও আগে চীনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যযুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক পরিসরে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। চীন যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করে পরাশক্তি হতে চায়।
ভূ-অর্থনীতি শব্দবন্ধটি এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে: ভৌগোলিক অবস্থান অর্থাৎ উচ্চ ও নিম্ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিবিশিষ্ট অঞ্চলে কোনো দেশের অবস্থান অথবা জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্র যোগাযোগের মতো বিষয়গুলো অর্থনীতিতে কী প্রভাব ফেলে, সেটাই হলো ভূ-অর্থনীতি। অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসবের প্রভাব নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। আমি অবশ্য ভিন্ন আঙ্গিক থেকে ভূ-অর্থনীতির সংজ্ঞায়ন করব। সেটা হলো, ভূরাজনীতির প্রতিমূর্তি বা সমার্থক হিসেবে ভূ-অর্থনীতি।
বাণিজ্য ও বিনিয়োগের মতো অর্থনৈতিক হাতিয়ার ব্যবহার করে যেভাবে বৈশ্বিক ক্ষমতার রাজনীতি পরিচালিত হচ্ছে এবং যেভাবে তা বৈশ্বিক অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলছে, সেটাই ভূ-অর্থনীতি। বৈশ্বিক অর্থনীতি এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি পরস্পর নির্ভরশীল; চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের অবনতি হলেও তারা এখনো পরস্পরের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য অংশীদার। ‘স্বল্পোন্নত দেশ’ বলতে আমি সেই দেশগুলোকে বুঝিয়েছি, যারা ব্রিকসের বর্তমান সদস্যদেশগুলোর তুলনায় কম উন্নত।
গত শতকের মধ্য আশির দশক থেকে বহুপক্ষীয় ব্যবস্থার অধীনে যেসব বাণিজ্য আলোচনা হয়েছে, তার মধ্য দিয়ে উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশই লাভবান হবে—এমন সম্ভাবনা ছিল। অভিযোগ আছে, এই ব্যবস্থার সুবিধা ধনী দেশগুলোই বেশি পায়। তারপরও নিয়মতান্ত্রিক এই ব্যবস্থার সুবিধা হলো, দেশগুলোর জন্য স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রয়োজনীয় ছিল না। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে অনেক দেশের আলোচনার দক্ষতায় ঘাটতি আছে। এখন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) আলোচনা প্রক্রিয়ায় উন্নতির সম্ভাবনা খুবই কম। এখন বরং যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের ক্ষমতাকেন্দ্রিক লড়াই সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে বৈশ্বিক ব্যবস্থা নতুন রূপ পাচ্ছে, সেই সঙ্গে আঞ্চলিক পর্যায়ে অংশীদারি গড়ে উঠছে। অর্থনৈতিক সহযোগিতার পাশাপাশি এসব আঞ্চলিক অংশীদারির লক্ষ্য হচ্ছে, নানামুখী রাজনৈতিক ও নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ আমলে নেওয়া।
সম্প্রতি শিল্পায়িত দেশগুলোর বাণিজ্যনীতিতে জাতীয়তাবাদী ঝোঁক তৈরি হওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে এটা বেশি দেখা যাচ্ছে। বাণিজ্য উদারীকরণের কারণে শ্রমিকেরা তাঁদের জায়গা হারাচ্ছেন, এই অভিযোগ উঠছে এবং এ নিয়ে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। তাই তাদের বাণিজ্যনীতিতে জাতীয়তাবাদী ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। যদিও অনেক অর্থনীতিবিদের ভাষ্য হচ্ছে, এসব শিল্পায়িত দেশে ক্ষতিপূরণের যথাযথ ব্যবস্থা না থাকায় এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। বাণিজ্য উদারীকরণ বা উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে আমদানির কারণে এমনটা ঘটেনি। পরিহাসের বিষয় হলো, বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থা উন্নত শিল্পায়িত দেশগুলোর জন্য
যুক্তরাষ্ট্র যেকোনো ধরনের বহুপক্ষীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিষয়ে উৎসাহ হারিয়েছে। ২০১৭ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প টিপিপি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নেন। এটি ছিল এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রাধিকার ও মূল্যবোধ প্রবর্তন করার লক্ষ্যে প্রণীত এক চুক্তি, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার জমানায় ২০০৯ সালে এর আলোচনা শুরু হয়। এমনকি বর্তমানে জো বাইডেন প্রশাসন ইন্দো প্যাসিফিক ইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্কের মতো চুক্তির বিষয়ে তেমন একটা আগ্রহ দেখাচ্ছে না, যদিও এই চুক্তির পরিসর টিপিপির মতো অতটা বৃহৎ নয়।
এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র এখন সীমিত পরিসরে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি করছে। দেখা যাচ্ছে, এসব চুক্তি বাইডেনের শিল্পনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। লক্ষ্য হচ্ছে, দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি। যেমন ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করেছে, যার নাম হচ্ছে ব্যাটারির জন্য খনিজ। গত বছর বিশ্বে যত নিকেল উৎপাদিত হয়েছে, তার অর্ধেক হয়েছে ইন্দোনেশিয়ায়। ফিলিপাইন সরকারও একই ধরনের চুক্তি করার দিকে এগোচ্ছে। অতি সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় অর্থনৈতিক চুক্তি করার অনেক কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। এই চুক্তির লক্ষ্য হচ্ছে, ভিয়েতনামকে চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্ক থেকে বের করে নিয়ে আসা।
এদিকে যুক্তরাষ্ট্র বহুপক্ষীয় ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে গেলেও মাঠে নেমেছে চীন। গত বছর রিজিওনাল কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ বা আরসিইপি কার্যকর হয়েছে। এটি চীনের নেতৃত্বে ১৪টি দেশের একটি জোট এবং এর মধ্যে দিয়ে এশিয়ার অর্থনীতি চীনের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়বে। এর অর্থ হলো, উন্নয়নশীল দেশগুলোকে এখন নিজে থেকে আলোচনা এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির জগৎ থেকে সুযোগ খুঁজে নিতে হবে। তবে নিয়মতান্ত্রিক বাণিজ্যব্যবস্থায়ও প্রতিটি দেশকে, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে নিজেদের বাণিজ্য স্বার্থ রক্ষায় সতর্ক থাকতে হয়।
বাংলাদেশ ও জিএসপি
স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদা থাকার পরও বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য অর্থাৎ তৈরি পোশাক যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পায়নি। এর আগে ২০১৩ সালে রানা প্লাজা ধসে যাওয়ার পর বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে শ্রমিকদের আইনসম্মত অধিকারের সুরক্ষা পর্যাপ্ত নয়, এই অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে জিএসপি সুবিধা তুলে নেয়। একটি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে এটি উল্লেখ করা যায় এ কারণে যে সেই ১৯৭৪ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্র এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর বাইরে আরও প্রায় ৯০টি দেশকে শুল্কমুক্ত পণ্য রপ্তানির সুযোগ দিয়ে আসছে। এর বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র ওই সব দেশ থেকে কোনো সুবিধা নেয়নি।
বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাক এর আগেই যুক্তরাষ্ট্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা হারানোর কারণে ওই সময় জিএসপি সুবিধা প্রত্যাহার করার বিষয়টি তেমন একটা গুরুত্ব পায়নি। বস্তুত তখন শুল্কমুক্ত সুবিধা হারিয়েছিল হোম টেক্সটাইল, হস্তশিল্প ও চামড়াজাত পণ্য। আর যে বিষয়টি একেবারেই গুরুত্ব পায়নি সেটি হলো, এই সুবিধা হারানোর কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য কী প্রভাব পড়েছে, সেটি।
ইউরোপ ১৯৭১ সালে প্রথম জিএসপি সুবিধা প্রবর্তন করে। এরপর বিশ্বের অধিকাংশ শিল্পায়িত দেশ এই একপক্ষীয় বাণিজ্যিক সুবিধা দেওয়ার নীতি গ্রহণ করে। মূলত উন্নয়নশীল দেশগুলোর টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের এই জিএসপি সুবিধা যেসব দেশ নিচ্ছে, তাদের উন্নয়নের স্তরের ওপর নির্ভর করত। সাধারণ জিএসপির তুলনায় এলডিসিভুক্ত দেশগুলোকে অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হতো। এর মধ্যে আরেকটি সুবিধা হচ্ছে জিএসপি প্লাস, যে দেশগুলো এলডিসির তালিকা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে বা উন্নয়নের একই পর্যায়ে আছে, সেই দেশগুলোকে এই জিএসপি প্লাস সুবিধা দেওয়া হয়।
জিএসপি ও জিএসপি প্লাস সুবিধা বেশ কিছু শর্তের ওপর নির্ভরশীল, যেমন মৌলিক মানবাধিকার, শ্রমমান, সুশাসন ও টেকসই উন্নয়নের অন্যান্য রীতিনীতি বাস্তবায়ন। যেসব বিষয় আবার সময় সময় খতিয়ে দেখা হয় বা পর্যালোচনা করা হয়।
উদাহরণস্বরূপ পাকিস্তানের কথা বলা যায়, যারা সম্প্রতি বেশ কিছু আন্তর্জাতিক রীতিনীতি অনুসমর্থনের পর জিএসপি প্লাস সুবিধা পেয়েছে। পরিষ্কারভাবেই দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের মতো যেসব দেশ এলডিসি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, তাদের পক্ষে এ ধরনের কঠোর মানদণ্ড বাস্তবায়ন করা চ্যালেঞ্জিং।
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পশ্চিমা দেশগুলো রাশিয়ার ওপর যেসব নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, তার প্রভাব এখন খুবই দৃশ্যমান। বড় ধরনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে এ ধরনের অর্থনৈতিক হাতিয়ার ব্যবহার করা হলে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে তার কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে, সেটা দেখা যাচ্ছে। নিষেধাজ্ঞার কারণে তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় উন্নয়নশীল দেশের দরিদ্র মানুষেরা উচ্চ মূল্যস্ফীতির কবলে পড়েছেন। এই পরিস্থিতি থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য শিক্ষণীয় হলো, এ ধরনের বৈশ্বিক বাজারসংকট মোকাবিলায় আপৎকালীন পরিকল্পনা করা, যেমন বিদেশি মুদ্রার যথেষ্ট মজুত বজায় রাখা।
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের যে তাৎক্ষণিক প্রভাব সারা বিশ্বে দেখা গেছে, চীনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যযুদ্ধের প্রভাব ঠিক অতটা দৃশ্যমান নয়। তবে তার দীর্ঘমেয়াদি ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা আছে। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার সাংঘর্ষিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে।
যেমন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ নিষেধাজ্ঞা দেওয়া থেকে শুরু করে রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ ও শুল্ক আরোপ করেছে। এসব নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপের কারণে উভয় দেশের জিডিপিতে তার প্রভাব পড়েছে; আর অন্যান্য দেশ পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বৈশ্বিক অর্থনীতি প্রবৃদ্ধির হার কমে যাওয়া বা সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটার কারণে এসব দেশ ক্ষতির শিকার হচ্ছে, প্রভাব পড়ছে তাদের রপ্তানিতে। তবে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, এই বাণিজ্যযুদ্ধের মধ্যেও যুক্তরাষ্ট্র ও চীন পরস্পরের বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার। এটা সত্য, যুক্তরাষ্ট্র চীন থেকে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সরিয়ে নেওয়ার কারণে অন্য কিছু দেশ তার সুবিধা নিতে পারে, যদি তাদের সেই প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ থাকে।
দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশও এই বাণিজ্য স্থানান্তরের সুবিধা নিয়েছে। যদিও কোন দেশ কোন ধরনের পণ্য এবং উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় কতটা প্রযুক্তি ব্যবহার করে, তার ওপর বিষয়টি নির্ভর করে। এই চিত্র থেকে বোঝা যায়, স্নায়ুযুদ্ধের সময়ের তুলনায় বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রতিটি দেশ এখন একে অপরের ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল।
সেই সঙ্গে এটাও বোঝা যায়, ভূ-অর্থনীতির পরিস্থিতি আগের চেয়ে জটিল হলেও স্বল্পোন্নত দেশগুলো যথাযথ বাণিজ্য কৌশল প্রণয়নের মাধ্যমে বৈশ্বিক বাণিজ্য ও সরবরাহ ব্যবস্থা থেকে আগের চেয়ে অনেক বেশি সুবিধা নিতে পারে।
আরেক দিকে পাঁচ জাতির জোট ব্রিকসের স্বরূপ ধীরে ধীরে আরও প্রকাশিত হচ্ছে। ভূরাজনীতি ও ভূ-অর্থনীতি যে পরস্পরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, এটি তার আরেকটি জটিল উদাহরণ। ব্রিকস আবার শিল্পায়িত দেশগুলোর জোট জি-৭ ও তার সম্প্রসারিত রূপ জি ২০-এর মতো নয়; ব্রিকস মূলত গঠিত হয়েছে বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে।
সেখানে চীনের অতিরিক্ত অ্যাজেন্ডা আছে। এটা হলো, এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা শক্তি কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করা, যে বিষয়ে আবার ভারত, ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিশেষ আগ্রহ নেই। ব্রিকসের মধ্যকার এই দ্বন্দ্ব ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে দেখা গেছে।
এবারের সম্মেলনে চীন সমমনা দেশগুলোকে জোটে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ২০টি আবেদনকারী দেশের মধ্যে মাত্র ৫টি দেশকে নতুন সদস্যপদ দেওয়া হয়, বাংলাদেশসহ বাকি দেশগুলোর আবেদন খারিজ হয়ে যায়।
প্রথম আলো