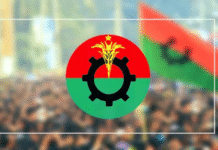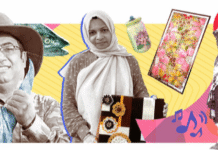১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ তারিখে ঢাকা রাজারবাগ পুলিশ লাইনে যে পুলিশ বাহিনী পাক দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তুলে বীরত্বের ইতিহাস রচনা করেছিল, সেই পুলিশ বাহিনীর বড় অংশই মুক্তিযুদ্ধশেষে স্বাধীন দেশে ফিরে আগের পেশায় থাকতে উৎসাহ বোধ করলো না।৭৫১ জন পুলিশ সদস্য স্বাধীনতার প্রথম প্রহরে লড়াইয়ের ময়দানে প্রাণ দিয়েছিলেন। এসব কারণে স্বাধীনতার পরে সুসংগঠিত একটি বাহিনী হিসেবে পুলিশকে দ্রুত পুনর্গঠিত করা যায়নি। কর্তব্য সম্পাদন কিংবা দেশের অভ্যন্তরে শান্তিরক্ষার জন্য উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রও তাদের হাতে ছিল না। এদিকে দলীয় ‘ক্যাডার’ ও দুর্বৃত্ত কিংবা বিপথগামী মুক্তিযোদ্ধারা যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতো সেগুলো ছিল পুলিশের অস্ত্রের চেয়ে অনেক উন্নতমানের। স্বাধীনতার পর পর বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্ত চোরাচালানের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছিল এবং প্রকাশ্য দিবালোকে চোরাচালান ছিল স্বাভাবিক ঘটনা।
সে পরিস্থিতিতে দুর্বল বেসামরিক প্রশাসনের জন্য সেনাবাহিনীর সাহায্যের দরকার ছিল। কিন্তু সেনাবাহিনীকে বেসামরিক কাজে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে আওয়ামী লীগ সরকার আগ্রহী ছিল না। কারণ, যুদ্ধকালীন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বর আচরণের অভিজ্ঞতা ও আওয়ামী লীগের দীর্ঘ সময় ধরে লালিত বিশ্বাসে তারা মনে করতো, প্রাতিষ্ঠানিক কোনো সেনাবাহিনী ছাড়াই দেশ চালানো সম্ভব। পাকিস্তান আমলে বিপুল সম্পদ সামরিক বাহিনীর জন্য বরাদ্দ হতে দেখে আওয়ামী লীগ মনে করেছিল যে, বড় একটি সামরিক বাহিনী লালন করা বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র ও দরিদ্র একটি দেশের পক্ষে সম্ভব হবে না। এছাড়া, তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সামরিক অভ্যুত্থানের ‘নিয়মিত’ ঘটনা দেখে আওয়ামী লীগ নেতারা সামরিক বাহিনীর মতো একটি সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতাসীনদের জন্য একটি ‘হুমকি’ হিসেবেই মনে করতেন।
এদিকে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল বাংলাদেশে বড় আধুনিক সামরিক বাহিনী প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে। ইতোমধ্যেই ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছিল যে, বাংলাদেশের ওপর যেকোনো আগ্রাসনের সময় ভারতের সক্রিয় সাহায্য পাওয়া যাবে। ভারতের পক্ষ থেকে যুক্তি প্রদর্শন করে প্রায়ই বলা হতো যে, বাংলাদেশের গোটা সম্পদ জাতীয় পুনর্গঠনের জন্যই ব্যয় হওয়া উচিত।
নতুন সরকারের সামরিক বাহিনী সম্পর্কে এমন বিবেচনা ও ভারতীয় ইচ্ছার সমীকরণে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণাধীন একটি আধা-সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে বুঝানো হয়েছিল যে, স্বাধীনতার পরপর শান্তি রক্ষার কাজটা খুব চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। এই শান্তিরক্ষার সমস্যার কথা বিবেচনায় রেখে ভারতীয় উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী ‘রক্ষীবাহিনী’ জাতীয় একটি আধা-সামরিক বাহিনী গঠনের মূল ধারণাটি কলকাতায় প্রবাসী সরকারের চিন্তায় স্থান করে নিয়েছিল।
এই আধা-সামরিক বাহিনীর লক্ষ্য হবে, আইন রক্ষার জন্য পুলিশকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করা এবং প্রয়োজনবোধে সেনাবাহিনীকে সাহায্য করা। কিন্তু এই বাহিনী থাকবে পুরোপুরিভাবে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে। এই বাহিনীর উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলী সম্পর্কে আইনে বলা হয় যে, সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে এই বাহিনীকে অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলার কাজে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য নিয়োগ করতে পারবে।
ভারতীয় উপদেষ্টা এবং সামরিক পরামর্শকদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সমস্ত প্রস্তুতি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ১৯৭২ সালের ৭ মার্চ ‘জাতীয় রক্ষীবাহিনী’ আদেশ প্রণয়ন করা হয় এবং ১ ফেব্রুয়ারি থেকে তা কার্যকর বলে গণ্য করার নির্দেশ দেয়া হয়। ভারতীয় সামরিক বাহিনী যেদিন বাংলাদেশ থেকে চলে যায়, সেদিন থেকেই ‘রক্ষীবাহিনী’ মোতায়েন করা হয়। একটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তেমন আইনগত কাঠামো রক্ষীবাহিনী আদেশে ছিল না।
এটা খুব কৌতূহলোদ্দীপক যে, আইন প্রণয়নের আগেই ‘রক্ষীবাহিনী’ তার কাজ শুরু করে দেয়। পরবর্তীকালে আদেশ জারির মাধ্যমে কেবলমাত্র এদের কর্মতৎপরতাকে পেছনের তারিখ থেকে আইনগত ভিত্তি প্রদান করা হয়। ‘রক্ষীবাহিনী’ প্রধানত যে সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছে, তা হলো বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার, সীমান্তে চোরাচালান রোধ, পণ্যের অবৈধ গুদামজাতকরণ ও কালোবাজারি বন্ধ এবং চূড়ান্তভাবে সরকারের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নিশ্চিহ্ন করা।
এই বাহিনীর প্রায় সকলেই ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। একটা বড় অংশ ছিল ‘মুজিববাহিনী’র। বাকিরা ‘কাদেরিয়া বাহিনী’র সদস্য।
‘রক্ষীবাহিনী’ গড়ে উঠেছিল একই সঙ্গে সরকার প্রধানের এমন এক ‘নিজস্ব’ প্রহরীদল হিসেবে, যাদের কার্যক্রম ছিল ঝড়ো পুলিশের মতো এবং তৈরি হচ্ছিল ‘বিকল্প সেনাবাহিনী’র আদলে। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রক্ষীবাহিনী গড়ে তোলার দায়িত্ব যখন ভারতীয়দের হাতে তখন বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী, বিডিআর ও পুলিশ বাহিনী পুনর্গঠনের কাজটি দেশের নিজস্ব ব্যবস্থাপনাতেই হচ্ছিল। এই বৈপরীত্য ছিল বিস্ময়কর ও প্রশ্নবোধক।
আরো বিস্ময়কর ছিল, পরিকল্পিতভাবেই রক্ষীবাহিনীকে রাখা হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর অধীনে; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে নয়। এই বাহিনীর পোশাক রাখা হয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর মতো। আবার রক্ষীবাহিনীর পরিচালক কর্নেল নূরুজ্জামান ‘বাকশাল’-এর কেন্দ্রীয় কমিটির ১১২ নম্বর সদস্য ছিলেন।
ভারতীয় সেনাবাহিনীর আদলে ছিলো ‘রক্ষীবাহিনী’র পোশাক। অনেকেই মনে করতো, যেহেতু ভারতীয় সেনারা একই পোশাক ব্যবহার করে তাই এই বাহিনীর পোশাকে ভারতীয় সেনার অনুপ্রবেশ ঘটবে। আবার কোনো কোনো মহল বলতো, ‘রক্ষীবাহিনী’র সদস্যদের বেশির ভাগই ভারতীয়। কারণ, ‘রক্ষীবাহিনী’র সদস্যদের মতো কালো মানুষ বাংলাদেশে নেই’। সৈয়দ আলী আহসান যখন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ছিলেন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সাথে রক্ষী বাহিনীর ঝামেলা হয়। এই ঝামেলা মিটাতে রক্ষীবাহিনীর দুই কর্মকর্তা আসেন সৈয়দ আলী আহসানের সাথে দেখা করতে, দু’জনেই ছিলো ভারতীয়।
‘মুজিববাহিনী’র প্রধান প্রশিক্ষক জেনারেল উবানের পরামর্শ ও সহায়তায় ‘রক্ষীবাহিনী’ গঠিত হয় বলে জেনারেল উবান দাবি করেছিলেন। এমনকি তিনি এটাও দাবি করেছিলেন যে, রক্ষীবাহিনীর অফিসারদের ভারতে নিয়ে প্রশিক্ষণ ও সরঞ্জাম দেবার বিষয়ে তিনিই ভারত সরকারকে রাজি করিয়েছিলেন। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর তৎকালীন মুখ্য সচিব পরমেশ্বর নারায়ণ হাকসারের মাধ্যমেই ‘রক্ষীবাহিনী’র প্রধানতম প্রশিক্ষক হিসেবে জেনারেল উবানের নিযুক্তি ঘটেছিল, যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে উবানের পদমর্যাদা ছিল ‘প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উপদেষ্টা’।
‘রক্ষীবাহিনী’র অন্যান্য প্রশিক্ষক হিসেবেও এক বিশেষ চিন্তার ও রাজনৈতিক মতাদর্শের মানুষ নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতীয় শিবিরে ‘মুজিববাহিনী’র প্রশিক্ষকদের মধ্যে যারা সমাজতন্ত্র-বিরোধী মনোভাবাপন্ন ছিলেন বলে দেখা যায়, তাদেরই বাছাই করে রক্ষীবাহিনীর প্রশিক্ষক করা হয়। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি অদ্ভুত ব্যাপার ছিল- এর অফিসারদের এবং ক্ষেত্রবিশেষে সুবেদারদেরও প্রশিক্ষণ দেয়া হতো ভারতে এবং সৈনিকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো ঢাকার সাভারে।
‘রক্ষীবাহিনী’তে লোক নিয়োগে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। কয়েকটি বিশেষ জেলা ছাড়া অন্য এলাকার লোকদের ‘রক্ষীবাহিনী’তে নেয়া হতো না। বিশেষ করে টাঙ্গাইলের ‘কাদেরিয়া বাহিনী’র জন্য ‘রক্ষীবাহিনী’র দ্বার উন্মুক্ত ছিল।
‘রক্ষীবাহিনী’র সাফল্য বর্ণনা করার সময়ও এই বাহিনীর আক্রমণের লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা করা যায়। রক্ষীবাহিনীর সাবেক এক শীর্ষ কর্মকর্তা কাজের সাফল্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, ‘রক্ষীবাহিনীর অভিযানের ফলে দেশের সন্ত্রাসী দলগুলো, বিশেষ করে নকশাল বাহিনী, সর্বহারা, পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল), পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল), সাম্যবাদী দল ও জাসদের ‘গণবাহিনী’র তৎপরতা অনেকটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে।’ অর্থাৎ, মূলত বামপন্থিদের বিরুদ্ধেই ‘রক্ষীবাহিনী’র অভিযান পরিচালিত হয়েছিল।
এই বাহিনী গঠনের সময় বলা হয়েছিল, ‘দক্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের দেশের কাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে’ রক্ষীবাহিনীর সৃষ্টি। অথচ পরিচালকদের মধ্যে মাত্র দু’জনকে নেয়া হয় মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে থেকে: আনোয়ার-উল-আলম শহীদকে নেয়া হয় ‘কাদেরিয়া বাহিনী’ থেকে এবং সারোয়ার হোসেন ছিলেন ‘মুজিববাহিনী’র মাদারীপুর অঞ্চলের একজন কমান্ডার। বাকি গুরুত্বপূর্ণ পরিচালক অধিকাংশই ছিলেন পাকিস্তান প্রত্যাগত সামরিক অফিসার। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে গড়ে ওঠা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অফিসারগোষ্ঠী থেকে কর্নেল নূরুজ্জামান ব্যতীত কারোই ঠাঁই হয়নি রক্ষীবাহিনীর সর্বোচ্চ পরিসরে।
কাজ শুরুর পরেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে রক্ষীবাহিনীর পক্ষপাতমূলক আচরণ সকলের নজরে আসতে থাকে। তা ছাড়া সামরিক বাহিনীকে বঞ্চিত করে রক্ষীবাহিনীকে সরকার উন্নত বেতন, খোরাক, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে বলে প্রচারণা শুরু হয়।
সেনাবাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধা এবং অ-মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে মানসিক দূরত্ব থাকলেও ‘রক্ষীবাহিনী’র কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সকলেই একমত পোষণ করতেন। সকল সদস্যেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, রক্ষীবাহিনীর বাজেট প্রতিরক্ষা বাজেট থেকে অনেক বেশি এবং রক্ষীবাহিনীর রসদ থেকে শুরু করে সকল সরঞ্জামের সুবিধা অন্যান্য বাহিনীর চেয়ে ভাল ছিল বলে ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হতো।
‘রক্ষীবাহিনী’ সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে এক বিশেষ রাজনৈতিক বাহিনী হিসেবে অবর্ণনীয় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। তারা গুম, গ্রেপ্তার, নির্যাতনের এমন সব রেকর্ড তৈরি করে, যা আগের সমস্ত নজিরকে ছাড়িয়ে যায়। ১৯৭৫-এ রক্ষীবাহিনী বিলুপ্ত করার পর ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে রক্ষীবাহিনীর একটি ক্যাম্প উঠে গেলে সেখানে গণকবর আবিষ্কার হয়। সেখানে ৬০টি নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল। অনুমান করা যায়, এই হতভাগ্যরা রক্ষীবাহিনীর হাতে নিহত হয়েছিলেন।
বিশিষ্ট বামপন্থি রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবী হায়দার আকবর খান রনো রক্ষীবাহিনীর হাতে দশ হাজারের বেশি কমিউনিস্ট, বামপন্থি কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছেন বলে দাবি করেছেন। ১৯৭৪ সালের ২৫ জানুয়ারি ‘দৈনিক গণকণ্ঠ’তে প্রকাশিত জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তরের বিবরণে দেখা যায়, কেবল ১৯৭৩ সালে রক্ষীবাহিনী ৪ হাজার ১৯৬ ব্যক্তিকে আটক করেছিল।
কালীগঞ্জে রক্ষীবাহিনীর দু’টি ক্যাম্প ছিল। একটি কালীগঞ্জ বাজারে, অপরটি ছিল গাজীর হাটে (কালার বাজার নামেও পরিচিত)। আর এগুলো নিয়ন্ত্রিত হতো পার্শ্ববর্তী ঝিনাইদহের নারিকেলবাড়িয়া থেকে। সেখানে ছিল রক্ষীবাহিনীর বড় একটি ক্যাম্প। কালার বাজারে রক্ষীবাহিনী গণকবরস্থান গড়ে তুলেছিল। এখানে ২০-২৫ গ্রামের মানুষকে একত্রিত করে শুয়ে পড়তে অর্ডার দেয়া হতো। তারপর সে সব মানুষের ওপর দিয়ে মার্চ করে যেত রক্ষীবাহিনীর সৈনিকরা। নকশালদের প্রতি সহানুভূতি থাকার দায়ে এ শাস্তি দেয়া হতো গ্রামবাসীদের।
রক্ষীবাহিনী অনেক তুচ্ছ ঘটনায় ক্ষমতার অপব্যবহার করে জনরোষ বয়ে এনেছিল। যেমন, ১৯৭৩ সালের ২৯ জুন চট্টগ্রামে ইস্টার্ন রিফাইনারির একটি বাস এই বাহিনীর একটি লরিকে ওভারটেক করলে রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা ওই গাড়ি ঘেরাও করে তাতে গুলিবর্ষণ করে। এতে একজন শ্রমিক ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। আহত হয় অনেকে।
সারা গ্রাম ঘেরাও করে এই বাহিনী অস্ত্র, ‘দুষ্কৃতকারী’ এবং ‘রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ’ অনুসন্ধান করতে শুরু করে এবং এক পর্যায়ে কথিত ‘ভুয়া রেশনকার্ড’ উদ্ধার করতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় তারা বেপরোয়াভাবে হত্যা, লুণ্ঠন এমনকি ধর্ষণও করতে থাকে।
তারা যেকোনো বাড়িতে প্রবেশ করতে পারতো, যে কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারতো। দেশের গোটা গ্রামাঞ্চলে শিবির স্থাপন করে তারা নারী-শিশু নির্বিশেষে যে কাউকে আটক রাখতে পারতো। প্রতিটি অপারেশনের পর তারা জনগণ থেকে আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকে। জনগণের মধ্যে রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে ভীতি ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং জনমনে ক্রমশ ঘৃণাবোধ সঞ্চারিত হয়।
কোনো আদালতে রক্ষীবাহিনীর তৎপরতাকে চ্যালেঞ্জ করা ছিল দুঃসাধ্য। এর প্রধান কারণ, সেনাবাহিনী, পুলিশ কিংবা এ ধরনের সংস্থার মতো নিয়মের নিগড়ে তারা আবদ্ধ ছিল না।
রক্ষীবাহিনীর যেকোনো সদস্য বা অফিসার বিনা ওয়ারেন্টে কেবলমাত্র সন্দেহবশত আইনের পরিপন্থী তৎপরতায় লিপ্ত থাকার অভিযোগে যেকোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার, যেকোনো ব্যক্তি-স্থান-যানবাহন-নৌযান ইত্যাদি তল্লাশি এবং আইনশৃঙ্খলাবিরোধী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, শুধুমাত্র এমন সন্দেহে যেকোনো সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করতে পারতো।
উপরন্তু রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের নজিরবিহীন ‘ইনডেমনিটি’ বা ‘দায়মুক্তি’ দেয়া হয়েছিল। যার অর্থ- সদস্যরা তাদের যেকোনো কাজ সরল বিশ্বাসে করেছেন বলে গণ্য করা হবে এবং এ নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের, অভিযোগ পেশ কিংবা আইনগত কোনো পদক্ষেপ নেয়া যাবে না। নিজেদের কর্তৃত্ব জাহিরের জন্য যখন তারা মফঃস্বল এলাকায় গিয়ে নিজেদের শিবির স্থাপন করতো তখন জেলা প্রশাসন কিংবা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের কাছে ‘আগমনী রিপোর্ট’ দেয়ার প্রয়োজন মনে করতো না।
আদালতের কাছে প্রশ্নোত্তর পর্যায়ে রক্ষীবাহিনীর অফিসাররা স্বীকার করেছেন যে, তাদের কোনো কার্যবিধি কিংবা আচরণবিধি ছিল না। নিজেদের কাজকর্মের কোনো বিবরণী কিংবা কাগজপত্র বা দলিল তারা সংরক্ষণ করতেন না। কোনো গ্রেপ্তার কিংবা তল্লাশির রেকর্ডও তারা রাখতেন না। তাহলে তারা কিভাবে কাজ করছেন- আদালতের এমন প্রশ্নের জবাবে রক্ষীবাহিনীর একজন সিনিয়র ডেপুটি লিডার হাফিজ উদ্দিন উদ্ধতভাবে জবাব দিয়েছিলেন, ‘আমরা যেভাবে কাজ করা ভালো মনে করি সেভাবেই করি।’ প্রশ্নোত্তর পর্যায়ে হাফিজ উদ্দিন জানিয়েছিলেন, অস্ত্রশস্ত্র বা গোলাবারুদের হিসাবের জন্য কোনো রেজিস্টারও তাদের ছিল না।
নিজেদের এরা ‘অপরাজেয় শক্তি’ মনে করতো। বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারের অভিযান পরিচালনাকালে তারা যেখানে খুশি সেখানে শিবির স্থাপন করতো। সন্দেহভাজন লোকদের ধরে শিবিরে নিয়ে আসতো। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য যেকোনো রকম নির্যাতনের পন্থা অবলম্বন করতো। কোনো রসিদ না দিয়ে তল্লাশিকালে তারা জনগণের সম্পত্তি জব্দ করার নামে হরণ করতো। ঘরে ঘরে ঢুকে লুট করতো ঘড়ি, ট্রানজিস্টার বা রেডিওসহ অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী। প্রাণের ভয়ে কেউ তাদের আচরণের প্রতিবাদ করার সাহস পেতো না। এমন খবরও পাওয়া যায় যে, বাজারে গিয়ে দোকানে দোকানে ঘুরে তারা টাকা সংগ্রহ করতো। গৃহস্থের ঘরে গিয়ে নিয়ে আসতো হাঁস-মুরগি। কোনো লোক তাদের কাজকর্মের বিরোধিতা করলে তাকে গুলি করে হত্যা করে তার লাশ নদীতে নিক্ষেপ করতো। সরকারের বিরোধী যে কাউকে তারা ‘দেশবিরোধী’ বলে সাব্যস্ত করতো এবং এভাবে অসংখ্য লোককে হত্যা করেছে তারা। ফলে দুর্ভাগ্যজনকভাবে সরকারের একটি ‘ফ্যাসিস্ট বাহিনী’ হিসেবেই ‘রক্ষীবাহিনী’ তার পরিচিতি অর্জন করে।
মুজিব সরকারের পরিকল্পনা ছিল ‘বাকশালে’র প্রত্যেক জেলা গভর্নরের অধীনে ‘রক্ষীবাহিনী’র একটি করে ইউনিট মোতায়েন করা। ফলে দ্রুত এই বাহিনীর বিকাশ ঘটানো হচ্ছিল। ১৫ আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানের পূর্বমুহূর্তেও জেলা গভর্নররা প্রশিক্ষণরত ছিলেন এবং ১৪ আগস্ট বিকেলেও এই গভর্নরদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন রক্ষীবাহিনীর একজন কর্মকর্তা।
১৯৭৫ সালের ৬ অক্টোবর খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বাধীন সরকার এক অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে ‘রক্ষীবাহিনী’কে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার ঘোষণা দেয়। এ সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশিত হয় ৯ অক্টোবর। এই নির্দেশনায় রক্ষীবাহিনীর যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র, ব্যাংক ব্যালেন্স, যানবাহন ইত্যাদি সেনাবাহিনী অথবা অন্যান্য প্রতিরক্ষা বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করার ঘোষণা দেয়া হয়। এ প্রক্রিয়ায় ঢাকার সাভার, চট্টগ্রামের ভাটিয়ারী, খুলনার গিলতলা, সিলেটের বটেশ্বর ইত্যাদি স্থানে বিপুল ভূ-সম্পদের মালিকানা লাভ ছাড়াও সেনাবাহিনীতে রক্ষীবাহিনীর আত্তীকরণ বাংলাদেশে সেনা আমলাতন্ত্র বিস্তৃত করার এক উপলক্ষ হয়েছিল।
সেনাবাহিনীতে রক্ষীবাহিনীর আত্তীকরণ শুরু হয় ১৯৭৫-এর ১২ অক্টোবর। খুব ধীরে এই আত্তীকরণ সম্পন্ন হচ্ছিল। অফিসারদের স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্তীকরণ করা হয়। পুরো পদক্ষেপটি আইনগতভাবে সঠিক ধারায় এগোলেও প্রশাসনিকভাবে ছিল অভিনব এবং বিস্ময়কর। তারা এমন একটি বাহিনীকে দেশের সুশৃঙ্খল প্রতিরক্ষা কাঠামোতে একীভূত করে নেয়, যে বাহিনী স্বরাষ্ট্র বা প্রতিরক্ষা কোনো মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ছিল না, যে বাহিনী গড়ে উঠেছিল ভিন্ন একটি দেশের সেনা কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতা ও তত্ত্বাবধানে, যে বাহিনীর জনবলের বিরাট এক অংশের সামরিক জীবনের শুরু হয়েছিল বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার তত্ত্বাবধানে এবং যে বাহিনীর বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিশ্বাসযোগ্য ও বিবেচনাযোগ্য অভিযোগ ছিল। এতসবের পরও কোনো ধরনের প্রকাশ্য তদন্ত বা জবাবদিহিতার মুখোমুখি না করেই এবং তার সদস্যদের মেধা, যোগ্যতা ও অতীত রাজনৈতিক সম্পৃক্তি সম্পর্কে জনমনে প্রশ্ন থাকার পরও রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীর মতো সুশৃঙ্খল একটি বাহিনীতে একীভূত করা হয়।
জিয়াউর রহমান নিজের জীবন দিয়ে এটা প্রমাণ করে গেছেন যে, এই সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না। জিয়াউর রহমানকে হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে অন্তত: চারজন ছিলেন ‘রক্ষীবাহিনী’ থেকে আত্তীকৃত।
এই ঘটনাবলীর আরেকটি কাকতালীয় দিক হলো, মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ ঢাকায় শেরেবাংলা নগরে সেনাবাহিনীর যে মিলব্যারাকে নিহত হয়েছিলেন, সেটি ছিল রক্ষীবাহিনীরই প্রধান কার্যালয়। মাত্র কয়েকদিন আগে যা সেনাবাহিনীতে আত্তীকৃত হয়েছিল এবং যেখানে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি ইউনিট অবস্থান করছিল।
একটি রক্ষীবাহিনী ব্যাটালিয়ন, যেটি ২২ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট হয়েছিল, সেটি ৩ নভেম্বর ১৯৭৫-এর অভ্যুত্থানে তার অধিনায়কের নির্দেশে অংশগ্রহণ করেছিল। দু’বছর পর বগুড়া সেনানিবাসেও শৃঙ্খলাবহির্ভূত কর্মে লিপ্ত হয়েছিল। ৪৮ ঘণ্টার মতো সময় ধরে বিশৃঙ্খলায় জড়িয়ে থাকার কারণে এ ব্যাটালিয়নটিকে ডিস্ব্যান্ড করা হয় বা ভেঙে দেয়া হয়।
৬ অক্টোবরের মাত্র চার সপ্তাহ পর ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান ছাড়াও লে. কর্নেল হাওলাদার, ক্যাপ্টেন দীপক প্রমুখ ‘রক্ষীবাহিনী’ কর্মকর্তা ১৯৭৫-এর ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। শেষোক্ত জনই ৪ নভেম্বর সাফায়াত জামিলের নেতৃত্বে বঙ্গভবনে ঢুকে মন্ত্রিসভার বৈঠকের মধ্যে প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদকে গুলি করতে উদ্যত হয়েছিলেন। ৩ নভেম্বরের অসফল অভ্যুত্থান যে ‘ভারতীয় সমর্থনপুষ্ট’ হিসেবে পরিচিতি অর্জন করেছিল তার পেছনে প্রধান প্রমাণ হিসেবে কাজ করে ওই অভ্যুত্থানে রক্ষীবাহিনী থেকে সদ্য রূপান্তরিত সেনা পদাতিক ব্যাটালিয়নগুলোর অপারেশনাল উপস্থিতি। ঢাকার মিরপুর ও সাভারে অবস্থানকারী এরকম পাঁচটি রূপান্তরিত ব্যাটালিয়নকে এই অভ্যুত্থানে সংশ্লিষ্ট করা হয়।
সীমাহীন ‘ক্ষমতা চর্চা’ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধারাবাহিকতায় রক্ষীবাহিনীর অভ্যন্তরীণ নিয়ম-কানুন ও শান্তি-শৃঙ্খলা অচিরেই ভেঙে পড়ে। পদমর্যাদার ক্ষেত্রে সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে এরা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে কলহ ও সংঘর্ষে লিপ্ত হতো। এসবের মধ্যে ছিল উন্মত্ততা, সেন্ট্রিকে আঘাত করা, কর্তব্য পালনকালে জুয়া খেলা, অধঃস্তনদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ইত্যাদি। এভাবে জনগণের কাছে ভাবমূর্তি হারাবার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষীবাহিনী থেকে সদস্যদের পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাও দিনে দিনে বেড়ে চলছিল।
রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন তারা পরে যুক্তি দেখিয়েছেন, সর্বহারা পার্টি, গণবাহিনী ও মার্ক্সবাদী-লেলিনবাদী নামধারী উগ্র বামদলের নৈরাজ্য আর খুনোখুনি ঠেকাতে এই শক্তি প্রয়োগের দরকার ছিল। উগ্র বামপন্থিরা শাসকদলের কর্মী-সমর্থকদের বেপরোয়াভাবে খুন করছিল বলে তাদের অভিযোগ। বস্তুতপক্ষে এসব উগ্র বামদল যত না শাসকদলের লোক মেরেছে তার চেয়ে অনেক বেশি বামপন্থিদের মেরেছে শাসকদল। এই ধরনের সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায়, শাসকদলই প্রথম হত্যা শুরু করে। সর্বোপরি যদি শাসকদল গণতন্ত্রকে সম্মান প্রদর্শন করতো, যদি আইনের প্রতি তাদের আনুগত্য থাকতো, তাহলে বিরোধীদলে সশস্ত্র তৎপরতার বিকাশ তো দূরের কথা, জন্মও নিতে পারতো না।
মুজিব আমলে রক্ষীবাহিনীসহ অন্যান্য নির্যাতনকারী বাহিনীর কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সাপ্তাহিক ‘হলিডে’ ছিল বেশ সোচ্চার। ‘হলিডে’তে এক প্রতিবেদনে লেখা হয়- ‘তুলনা করতে পছন্দ না করলেও এই বাহিনীর কাজের সঙ্গে অনেকেই ভারতের সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ বা সিআরপি’র কাজের মিল খুঁজে পেয়েছে। এই বাহিনী সন্ত্রাসবাদ আক্রান্ত পশ্চিম বাংলায় তৎপরতা চালিয়ে আসছে। রক্ষীবাহিনীর নির্দয়-নির্বিচার অপারেশন, যেখানে সংবেদনশীলতার লেশমাত্র নেই, তাকে সিআরপি’র সমগোত্রীয় বলে প্রতিপন্ন করেছে। জাতীয় রক্ষীবাহিনী মূর্তিমান সন্ত্রাস। একে গঠন করা হয়েছে জনগণকে দমনে, বিপ্লবী রাজনীতি উৎখাতকরণে এবং বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী ও তার মুরুব্বী ভারতের স্বার্থ রক্ষায় লাঠিয়ালের কাজ করতে।’
মুজিব শাসনামলে গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ যে সব কারণে সরকারের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল, তার মধ্যে একটি ছিল রক্ষীবাহিনীর কার্যক্রম। বস্তুত গণমাধ্যমকে ‘মুক্ত’ অবস্থায় রেখে দিলে রক্ষীবাহিনীকে কোনোভাবেই এতটা ‘মুক্ত হস্তে’ তাদের কার্যক্রম চালাতে দেয়া সম্ভব হতো না। রক্ষীবাহিনীর ‘অবাধ’ ভূমিকার স্বার্থেই গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল।
এই কারণে গণমাধ্যমের ওপর রক্ষীবাহিনীরও আক্রোশ ছিল। চুয়াত্তরের ১৯ মার্চ রক্ষীবাহিনী ‘গণকণ্ঠ’-র প্রেসের যন্ত্রপাতি খুলে নিয়ে যায়; যা ছিল গণমাধ্যমের প্রকাশনা বন্ধে ওই সময়কার এক অভিনব নজির। রক্ষীবাহিনী, মুজিববাহিনী ও সমজাতীয় বাহিনীগুলোর হত্যা, সন্ত্রাস ও নির্যাতন সম্পর্কে দেশি-বিদেশি পত্রিকায় বেশ কিছু রিপোর্ট ছাপা হয়েছিল। এসব রিপোর্ট ছাপার ‘অপরাধে’ দেশের বহু দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে কিংবা বন্ধ করে দিতে বাধ্য করা হয়েছে। বিদেশি অনেক সাংবাদিককেও অপদস্থ হতে হয়েছে। ১৯৭৫-এর মে মাসে ‘রিডার্স ডাইজেস্ট’-এ এক প্রতিবেদন ছাপা হয়। সেখানে লেখা হয়-
“জনগণের মধ্যে শেখ মুজিবের যাদুকরী ইমেজ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এই পটভূমিতে শেখের পদক্ষেপগুলোও ক্রমেই নির্দয় হচ্ছে। স্বাধীনতার পর থেকে এযাবৎকাল অন্তত দু’হাজার আওয়ামী লীগবিরোধী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী খুন হয়েছেন। শেখ মুজিব দু’টি বেসামরিক সংগঠনের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। একটি হচ্ছে তার ভাগ্নের নেতৃত্বাধীন এক লাখ সশস্ত্র একগুঁয়ে যুবকের সংগঠন ‘যুবলীগ’। এটি ‘জাতীয় শুদ্ধি অভিযানে’ নিয়োজিত। অপরটি হচ্ছে তার (মুজিব) নিজস্ব নিরাপত্তাবাহিনী- নিষ্ঠুর ‘রক্ষীবাহিনী’। শেষোক্ত বাহিনীটি যেকোনো কারণে যখন-তখন অত্যাধুনিক অস্ত্র উঁচিয়ে মিল-কারখানায় প্রবেশ করে, শ্রমিক নেতাদের উপর খবরদারি করে। গ্রাম এলাকায় আকস্মিক কারফিউ জারি করে জনগণের মধ্যে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালায়। এরা লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় নির্মম নির্যাতন চালিয়ে থাকে, যার পরিণতিতে এযাবৎ বহু লোকের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে।”
‘রক্ষীবাহিনী’ নামের এই খুনে বাহিনীর সদস্যদের হাতে কত মানুষ গুম কিংবা খুন হয়েছে, তার সত্যিকার হিসাব হয়তো কখনোই পাওয়া যাবে না।