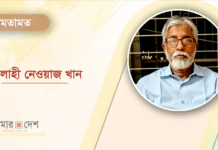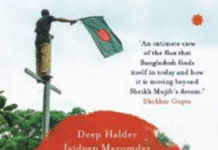Prothom Alo

লেখক ও গবেষক

আবু (আবু জামাল রেজা) ক্লাস এইট পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে ছিল। এক অজানা কারণে তাড়াহুড়ো করে গরমের ছুটির মধ্যেই টিসি নিয়েই মেহেরপুরের গাংনী চলে যায়। পানি উন্নয়ন বোর্ডে (তখন ওয়াপদা বলা হতো) কাজ করতেন আবুর মামা। মামার কাছে থেকেই গল্পের ‘ফটিকের’ মতো আমাদের চৌকস বন্ধু পড়াশোনা করত। আবু নিজেই নিজের নাম রেখেছিল ফটিক। রবীন্দ্রনাথ তার ছিল মুখস্থ।
পরে জেনেছিলাম, ওর মামার চাকরিটা হঠাৎ করেই নট হয়ে যায়। পশ্চিম পাকিস্তানি বসের গায়ে হাত তুলতে যাওয়ার অভিযোগে। বসই তাঁকে ভয়ংকর (গালি) কিছু বলে উত্ত্যক্ত করেছিলেন। সেটা কেউ শোনেননি; কিন্তু তেড়ে মারতে যাওয়ার পক্ষে অনেক সাক্ষী ছিল। একদম জিনেদিন জিদান (ফরাসি ফুটবলার) মামলা।
জিদানকে দেওয়া মা–বোন তুলে গালিটা কেউ দেখেননি; কিন্তু তাঁর ঢুসটা সবাই দেখেছিলেন। শাস্তি হয়েছিল জিদানের, কিছু হয়নি উত্ত্যক্তকারীর। যা–ই হোক, আবু তার বিধবা মায়ের কাছে গ্রামে ফেরত গেলেও আমাদের চিঠি দেওয়া–নেওয়া চলত। তখনকার দিনে পেনফ্রেন্ড বলে একটা কথা চালু ছিল। আমরা ক্রমে ক্লাসফ্রেন্ড থেকে পেনফ্রেন্ড হয়ে উঠলাম।
১৯৬৯ সালের এপ্রিলে আবুর চিঠিতে জানতে পারি, ‘পাকিস্তান দেশ কৃষ্টি’ একটি অতিরিক্ত বই আমাদের পড়তে হবে। পূর্ব পাকিস্তানিদের খাঁটি পাকিস্তানি বানানোর আইয়ুবি খায়েশ তখন ইয়াহিয়া বাস্তবায়ন করছেন। বইয়ের একটা মলাট পাঠিয়েছিল পরের চিঠিতে। দেশে তখন ইয়াহিয়ার মার্শাল ল। সিনেমার টিকিট হাফ করে দিয়ে ছাত্রদের মনজয়ের চেষ্টা করছেন ইয়াহিয়া। ছাত্র আন্দোলনের মুখে আইয়ুব শাহির পতন হয়েছে মাত্র (২৫ মার্চ, ১৯৬৯) এর মধ্যে আবার নতুন চক্রান্ত!
ক্লাস নাইনের আবু বুঝে ফেলে, পাকিস্তানিদের এই নতুন চক্রান্ত ছাত্রদের একাই রুখতে হবে। ইয়াহিয়ারা যে নির্বাচনের হালুয়ার–রুটির মৌতাত ছড়িয়েছে, তাতে রাজনৈতিক দলগুলো এখন শুধু নির্বাচনের জিকিরই করবে। অন্য কোনো আন্দোলন করে নির্বাচনের চাঁদকে তারা মেঘের আড়ালে ফেলে দেওয়ার ঝুঁকি নেবে না। শেষ পর্যন্ত স্কুলের পথে নামে কিশোরেরাই এককভাবে সারা দেশে। সেটাই ছিল কিশোর নেতৃত্বের প্রথম আন্দোলন।
আবুর নেতৃত্ব ছিল দেখার মতো। তখনকার প্রধান রাজনৈতিক দলের ছাত্রসংগঠনগুলোর একটাও (ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, ইসলামী ছাত্র সংঘ) সেদিন স্কুলের কিশোরদের পাশে এসে দাঁড়ায়নি। উনসত্তরের গণ–অভ্যুত্থানের পরপরই কিশোরদের সেই আন্দোলন সামরিক শাসকেরা থামাতে চাইলেও পারেনি। জুন, ১৯৬৯-এ দেশ ও কৃষ্টি বই পাঠ্যতালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। আবু অনেক আগে থেকেই পরিস্থিতি বুঝতে পারত।
একাত্তরের ৭ মার্চের পরই আবু চিঠি দিয়ে জানিয়ে রেখেছিল, পরিস্থিতি বেগতিক দেখলে আমরা যেন তাদের গ্রামে চলে যাই। আমাকে সে–ই খুঁজে বের করে ভবেরপাড়ার বৈদ্যনাথতলায় ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১।
যুদ্ধফেরত আবুর সঙ্গে যোগাযোগ ক্রমে ক্ষীণ হতে থাকে। পড়াশোনায় তার আর ফেরা হয় না। চাষবাস আর খেতখামারে ডুবে যায়। ছোট ভাই–বোনদের ‘মানুষ’ করার কাজে নিজেকে নিবেদিত করে। আবুর এ রকম এক নাতিদীর্ঘ পরিচিতি দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এটা জানিয়ে রাখা, খেতখামার নিয়ে পড়ে থাকলেও আবু মোটেও ‘আবুল টাইপ’ মানুষ নয়। খুবই রাজনীতি সচেতন এক বুঝমান মানুষ। নিজে থেকেই সে আমাকে দেশ–গ্রামের নানা তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করে।
মেহেরপুর অঞ্চলে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের আবাদকে জনপ্রিয় করে তোলার পেছনে খামারি আবুর অবদান সবাই মনে করেন। নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক দল আর তাদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের খিদের কথা জিজ্ঞাসা করতেই আবু ফিরে গেল রবীন্দ্রনাথে—তোর মনে আছে, বড়দের দেখাদেখি স্কুলে যাওয়ার জন্য শিশু রবীন্দ্রনাথ একদিন ভোঁ কান্না জুড়ে দিয়েছিলেন। তখন তাঁদের গৃহশিক্ষক রবি বাবুর এমন কান্নায় অতিষ্ঠ হয়ে কষিয়ে এক চড় মেরে বলেছিলেন, ‘এখন স্কুলে যাইবার জন্য যেমন কাঁদিতেছ, না যাইবার জন্য ইহার চাইতে ঢের বেশি কাঁদিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন—এ কথা কিন্তু পরে সত্যি হয়েছিল।
রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘সেই শিক্ষকের নামধাম আকৃতিপ্রকৃতি আমার কিছুই মনে নাই—কিন্তু সেই গুরুবাক্য ও গুরুতর চপেটাঘাত স্পষ্ট মনে জাগিতেছে। এত বড় অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী জীবনে আর-কোনোদিন কর্ণগোচর হয় নাই।’(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবন্ধ, জীবনস্মৃতি, শিক্ষারম্ভ)।
গত নভেম্বরে সরকারের হিসাবেই বলা হয়েছিল, ১ হাজার ৪১৬ ইউপি চেয়ারম্যান পলাতক, যা মোট ইউনিয়ন পরিষদের এক-তৃতীয়াংশ। এই চেয়ারম্যানদের অনেকের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করা হয়েছে। অন্য ৩ হাজার ১৬৪ জন চেয়ারম্যান নিয়মিত অফিস করছেন বলা হলেও তৎকালীন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় উপদেষ্টা এ এফ হাসান আরিফ বলেছিলেন, যেখানে ১০ থেকে ১২ জন থাকার কথা, সেখানে হয়তো ২-৩ জন আছেন।
ছায়ানটের একান্ত ভক্ত (বর্তমান ভবন নির্মাণের জন্য আবু এক বিঘা জমি বিক্রি করে নির্মাণ তহবিলে দান করার কথা আমরা অনেকেই জানি) স্বাভাবিকভাবে সন্জিদা খাতুনের চলে যাওয়ায় তাঁর মন খারাপ। তাই রবীন্দ্রনাথের স্কুলে যাওয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের নির্বাচনের তুলনা নিয়ে বাহাসে না গিয়ে মিনমিন করে বললাম, কিন্তু নির্বাচন ছাড়া কেমনে কী হবে? বাংলা ভাষায় কোনো গালি না থাকায় আবু আমাকে গালি না দিয়ে বলে, তোর মাথা গেছে। আমি তো নির্বাচনকে না বলিনি; বলছি কোনটা আমাদের প্রায়োরটি। রাহাজানি–ডাকাতি–ছিনতাই ঠেকানো, সোজা কথায় অস্ত্র উদ্ধার। বাহাত্তরের মতোই অস্ত্র চলে গেছে এখন বাজে মানুষের হাতে। গত আগস্টে থানা ফাঁড়ি লুটের সময় অস্ত্র যারা নিয়ে গিয়েছিল, অস্ত্রের ধর্ম অনুযায়ী সেগুলোর বেশির ভাগই এখন তাদের কাছে নেই। অস্ত্রের আবার ধর্ম কী? অনেকটা কবুতরের মতো, যার টাকা নেই, তার কাছে সে থাকে না। তাই তো বলে সুখের পায়রা।
আগস্টের আগে কাদের হাতে কাঁচাপয়সা ছিল? সেই কাঁচাপয়সার মালিকদের কাছে অস্ত্রপাতি সুরসুর করে চলে যাচ্ছে–গেছে। এগুলো দিয়েই তারা এখন বাণিজ্য করছে রাজনীতিও করছে। চুরি–ডাকাতির যেমন একটা বাণিজ্যিক দিক আছে, তেমন তার একটা রাজনৈতিক দিকও আছে। বিডি মেম্বার ছানা মিয়ার কথা মনে আছে? সে চোর পুষত তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য। সবাই জানত, ছানা মেম্বারের সঙ্গে কাইজ্যা–ফ্যাসাদ করলে বাড়িতে গোয়ালে চুরি হয়। অস্ত্র উদ্ধারের কাজ তো চলছে! পুলিশ–আর্মি–র্যাব দিয়ে অস্ত্র উদ্ধার খুব কঠিন কাজ।
শেখ মুজিবের মতো জনপ্রিয় নেতা আর রক্ষী বাহিনীর প্রাণন্ত চেষ্টার পরও ১৯৭২–৭৩-এর অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার সম্ভব হয়নি, হাতবদল হয়েছিল মাত্র। স্থানীয় সরকার ছাড়া অস্ত্র উদ্ধার সম্ভব নয়। আইয়ুব খান ১৯৬৯–এর মার্চে বিদায় হলেও কার্যত ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত এ দেশে কোনো কার্যকর স্থানীয় সরকার ছিল না। অধিকৃত বাংলাদেশে পাকিস্তানিরা স্থানীয় সরকারের কাজ করতে চেয়েছিল পছন্দের লোকদের নিয়ে গড়া শান্তি কমিটি দিয়ে। ফলাফল আমরা জানি।
দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পর স্থানীয় সরকারের চেয়ারে বসানো হলো তথাকথিত রিলিফ কমিটিকে। মজাফফর ন্যাপের দুই–একজন কদাচিৎ দু-একটা কমিটিতে থাকলেও সবই ছিলেন মধুসন্ধানী আওয়ামী লীগের লোকজন। তাঁরা না চেয়েছেন অস্ত্র উদ্ধার করতে, না পেরেছেন ত্রাণ বিতরণ করতে। শেখ মুজিব এঁদেরকেই বলেছিলেন ‘চাটার দল’; খুঁজেছিলেন, ‘আমার কম্বল কই?’ ফলাফল ছিল দুর্ভিক্ষ আর সারা দেশে সশস্ত্র হানাহানি, পাটের গুদামে রহস্যজনক আগুন।
প্রকৃতপক্ষে অস্ত্র উদ্ধার বেগবান হয় ১৯৭৬–৭৭ সালে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের পর। ইউনিয়ন আর পৌর পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যত সহজে নিজ নিজ এলাকার দুই নম্বরি লোকদের, অবৈধ অস্ত্রধারীদের চিহ্নিত করতে পারবেন, অন্য কারও পক্ষে সেটা তত সহজ হবে না। আবু জানাল, আমার অভিজ্ঞতা বলে, স্থানীয় সরকার নির্বাচনের ঘোষণা দিলেই পুলিশের কাছে খবর যাওয়া শুরু হবে। ওই যে বলে না, ‘গোপন সূত্রে খবর পেয়ে’, ওই সব সূত্র অটোমেটিক কাজ করা শুরু করবে। ইউনিয়ন পরিষদ তো বাতিল হয়নি, মনে করিয়ে দিই—ইউপি তো আছে। আবু বলে যায়, ওটা এখন ‘কাজির গরু কেতাবে আছে গোয়ালে নাই’।
গত নভেম্বরে সরকারের হিসাবেই বলা হয়েছিল, ১ হাজার ৪১৬ ইউপি চেয়ারম্যান পলাতক, যা মোট ইউনিয়ন পরিষদের এক-তৃতীয়াংশ। এই চেয়ারম্যানদের অনেকের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করা হয়েছে। অন্য ৩ হাজার ১৬৪ জন চেয়ারম্যান নিয়মিত অফিস করছেন বলা হলেও তৎকালীন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় উপদেষ্টা এ এফ হাসান আরিফ বলেছিলেন, যেখানে ১০ থেকে ১২ জন থাকার কথা, সেখানে হয়তো ২-৩ জন আছেন।
তিনি তখন স্বীকার করেছিলেন, এত ইউনিয়ন পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়ার মতো কর্মকর্তা নেই। ফলে যেসব ইউনিয়নে চেয়ারম্যান অনুপস্থিত; কিন্তু বেশির ভাগ মেম্বার উপস্থিত, সেখানে প্যানেল চেয়ারম্যান গঠন করে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আর যেসব ইউনিয়নে চেয়ারম্যানের পাশাপাশি বেশির ভাগ মেম্বারও অনুপস্থিত, সেখানে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। দিনের শেষে পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। যাঁরা গত ১৫ বছর ভোট করতে পারেননি বা বারবার হেরেছেন, টাকা অথবা পেশির কাছে কিংবা কেনা মার্কার কাছে। তাঁরা বদলা নিতে ফৌজদারি মামলার আসামি বানিয়ে দিয়েছেন ইউপি চেয়ারম্যান–মেম্বারদের। তাঁরা আছেন দৌড়ের ওপর। যাঁদের টেঁকের জোর আছে বা ফন্দিফিকির জানা আছে, তাঁদের কেউ কেউ উচ্চ আদালত থেকে আগাম জামিন নিয়েছেন; কিন্তু শেষরক্ষা হচ্ছে না। তোমাদের কাগজেই তো দেখলাম, জামিনের ২৮ দিন পর আদালতে হাজিরা দিতে গিয়ে আবার আটক হয়েছেন রাজশাহীর বাঘা উপজেলার তিন ইউপি চেয়ারম্যান। গত ২৫ ফেব্রুয়ারির ঘটনা। বাংলাদেশের পুরোনো থানাগুলোর মধ্যে চট্টগ্রামের আনোয়ারা অন্যতম। এই থানা গঠিত হয় ১৮৭৬ সালে আনোয়ারায় (বর্তমানে উপজেলা) ১১টি ইউনিয়ন। সেখানেও প্রায় সব চেয়ারম্যান পলাতক। এঁরা সবাই বিস্ফোরকসহ নানা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি। যিনি পালাতে পারেননি, তাঁর ঠাঁই হয়েছে জেলে। ১১টির মধ্যে মাত্র ৩টি ইউনিয়নে (বটতলী, হাইলধর ও পরৈকোড়া) প্যানেল চেয়ারম্যান থাকায় টিমটিম করে দিনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। বাকি ৮টি ইউনিয়নের কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়েছে ইউএনও আর এসি ল্যান্ডের মধ্যে। এ রকম জোড়াতালি দিয়ে চলছে স্থানীয় সরকার, একে চলা বলে না।
তাহলে উপায় কী? আবু বলে চলে, তোমরা যদি অস্ত্র উদ্ধার চাও, ক্ষমতাচ্যুতদের নাশকতা বন্ধ করতে চাও, খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাও, তাহলে অবিলম্বে ইউপি নির্বাচনের ব্যবস্থা করো। জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ—এমনকি পৌর করপোরেশন–সভাগুলো প্রশাসক দিয়ে চালিয়ে নেওয়া যাবে; কিন্তু ইউপি প্রশাসক দিয়ে চলার নয়।
ভোলার ঘটনা আরও ঘটবে। ভোলায় ইউপি প্রশাসককে জেলেরা যে দাবড়ানি দিয়েছেন, তা অনেক কাগজেই আসেনি। সব খবর আসেও না। কিন্তু মানুষের ধৈর্যের বাঁধ সিমেন্টের না। এটা মনে রাখতে হবে। আমার মনে হয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত বর্তমান উপদেষ্টা মার্চে তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া স্ট্যাটাসে যথার্থই বলেছেন, ‘জনগণ প্রাত্যহিক নানা সেবার প্রয়োজনে স্থানীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীল। জনপ্রতিনিধি না থাকায় সেবা ব্যাহত হচ্ছে। তাই জনগণের প্রাত্যহিক দুর্ভোগ নিরসনে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের বিষয়ে বারবার বলছি। নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকৃত জনপ্রতিনিধি দিয়ে স্থানীয় সরকার পরিচালনাই সর্বোত্তম।’
শুভস্য শীঘ্রম। অন্যথায় যারা সবার আগে, পারলে কালকেই জাতীয় নির্বাচনের জন্য বেচাইন হয়ে গেছে, তাদের জন্য শিশু রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষকের অমর বাণী মনে করিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কীই–বা করার আছে, ‘এখন স্কুলে যাইবার জন্য যেমন কাঁদিতেছ, না যাইবার জন্য ইহার চাইতে ঢের বেশি কাঁদিতে হইবে।’
● গওহার নঈম ওয়ারা লেখক ও গবেষক
gawherwahra@gmail.com