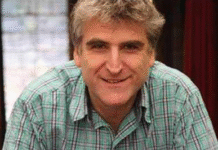ড. মইনুল ইসলাম : ‘রবার ব্যারন’ শুনতে শোভন নয়। আক্ষরিক অর্থ করলে দাঁড়ায় ‘ডাকাত ব্যবসায়ী’। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৮৭০ থেকে ১৯১৪ সালের পুঁজির বিকাশে এদের ভূমিকা খুব আলোচিত। এর সঙ্গে বাংলাদেশের রাঘববোয়াল ব্যবসায়ীদের অবিশ্বাস্য ধনসম্পদ আহরণের পদ্ধতির আশ্চর্যজনক মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।
ড. মইনুল ইসলাম : ‘রবার ব্যারন’ শুনতে শোভন নয়। আক্ষরিক অর্থ করলে দাঁড়ায় ‘ডাকাত ব্যবসায়ী’। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৮৭০ থেকে ১৯১৪ সালের পুঁজির বিকাশে এদের ভূমিকা খুব আলোচিত। এর সঙ্গে বাংলাদেশের রাঘববোয়াল ব্যবসায়ীদের অবিশ্বাস্য ধনসম্পদ আহরণের পদ্ধতির আশ্চর্যজনক মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।
যুক্তরাষ্ট্রের সব নেতৃস্থানীয় ব্যবসায়ীকে ‘রবার ব্যারন’ বলা হয় না। দুর্বৃত্তায়িত ব্যবসা কৌশল (রবার) এবং তদানীন্তন মার্কিন রাজনীতির ওপর তাদের অপরিসীম প্রভাবের কারণে তাদের সামাজিক প্রতিপত্তিকে (ব্যারন) ফোকাস করা হয়েছে।
স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের ৫২ বছরে যেসব ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি ধনবান হয়েছেন, তাদের সবাইকে রবার ব্যারনদের বাংলাদেশী সংস্করণ আখ্যায়িত করা সমীচীন হবে না। তবে দেশের অধিকাংশ ধনকুবেরের ক্ষেত্রে অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন এবং ক্ষমতাসীন শাসক মহলের পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।
এ রকম নেতৃস্থানীয় ধনকুবের ‘রবার ব্যারন’ ছিলেন জন ডি রকফেলার, কর্নেলিয়াস ভ্যান্ডারবিল্ট, এন্ড্রু কার্নেগি, এন্ড্রু মেলন, জন জ্যাকব এস্টর, জে কুক, জেমস বুখানান ডিউক, জেপি মরগান, হেনরি মরিসন ফ্ল্যাগলার, জন সি অসগুড, চার্লস এম শোয়াব, চার্লস ক্রকার, হেনরি ক্লে ফ্রিক, ড্যানিয়েল ড্রু, জে গৌল্ড, জেমস ফিস্ক, জন ওয়ার্ন গেইটস, ইএইচ হ্যারিম্যান, হেনরি ব্রেডলি প্ল্যান্ট, জোসেফ সেলিগম্যান, জন ডি স্প্রেকেলস, চার্লস এইরকেস এবং লেলান্ড স্ট্যানফোর্ড। তাদের ধনসম্পদের আহরণ পদ্ধতি ছিল দুর্বৃত্তায়িত। তারা ঠিকমতো সরকারের কর দিতেন না, অথচ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাধন্য ছিলেন। ১৮৭০-১৯১৪ পর্যায়ে তারা মার্কিন রাজনীতিকে প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। তাদের ছল-চাতুরি ও ধূর্ত কূটকৌশলের কারণে মার্কিন শেয়ারবাজার ওয়াল স্ট্রিট এবং অনেক মার্কিন ব্যাংক বেশ কয়েকবার পুঁজি লুণ্ঠন ও টালমাটাল সংকটের শিকার হয়েছিল।
দৈনিক বণিক বার্তার ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ সংখ্যার প্রধান প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল ‘আর্থিক সংকটের সময় দেশে বিলিয়নেয়ার আরো বেড়েছে’। ওই খবরে সুইজারল্যান্ডের ইউবিএস ব্যাংকের ২০২৩ সালের সর্বশেষ তথ্য উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, ২০২২ সালে বাংলাদেশে ১১০ কোটি থেকে সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকার বেশি পরিমাণ সম্পদ রয়েছে এমন ধনকুবেরের সংখ্যা ২০২১ সালের ৫০৩ জন থেকে বেড়ে ২০২২ সালে ৫২৯ জনে দাঁড়িয়েছে। ২০২২ সালে ৫ কোটি থেকে ১০ কোটি ডলার (৫৫০ কোটি থেকে ১ হাজার ১০০ কোটি টাকা) পর্যন্ত সম্পদ ছিল এমন ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ৪০ জন।
প্রায় দেড় দশক ধরে ব্যবসায়িক কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সম্পদশালীদের তথ্য সংগ্রহ করে থাকে সুইজারল্যান্ডের জুরিখভিত্তিক ক্রেডিট সুইস ব্যাংক। এ সম্পদশালীদের পরিসংখ্যান নিয়ে তারা একটি ডাটাবেজ তৈরি করেছে, যা প্রকাশিত হয় ‘গ্লোবাল ওয়েলথ রিপোর্ট’ শিরোনামে। ২০২২ সালে ক্রেডিট সুইস ব্যাংককে অধিগ্রহণ করেছে আরেক সুইস ব্যাংক ইউবিএস। ফলে ২০২৩ সালে এবার সম্পদশালীদের সর্বশেষ ডাটাবেজ প্রকাশ করেছে ইউবিএস। এ সর্বশেষ তথ্যে বাংলাদেশে ৫০ কোটি ডলার বা সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকার বেশি সম্পদ রয়েছে ২২ জনের কাছে। অন্যদিকে এ তথ্য মোতাবেক ২০২২ সালে ৫০ লাখ থেকে ১ কোটি ডলারের সম্পদ ছিল ১ হাজার ১৫৬ জনের কাছে।
এ তথ্যগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যাক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা সংস্থা ‘ওয়েলথ এক্স’-এর ২০১৮ সালের প্রকাশিত বাংলাদেশের ধনকুবেরদের সংখ্যার প্রবৃদ্ধির চিত্রটি। ২০১৮ সালের ১১ ও ১২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল ‘বিশ্বে ধনকুবেরের সংখ্যার প্রবৃদ্ধির হারের শীর্ষে বাংলাদেশ’। এ সংবাদে জানানো হয়েছে, ‘ওয়েলথ এক্স’-এর প্রতিবেদন ওয়ার্ল্ড আল্ট্রা ওয়েলথ রিপোর্ট-২০১৮ মোতাবেক ২০১২ থেকে ২০১৭ এ পাঁচ বছরে অতিধনী বা ধনকুবেরের সংখ্যা বৃদ্ধির দিক দিয়ে বিশ্বের বড় অর্থনীতির দেশগুলোকে পেছনে ফেলে সারা বিশ্বে এক নম্বর স্থানটি দখল করেছিল বাংলাদেশ। বাংলাদেশের ধনকুবেরদের সংখ্যার বার্ষিক ১৭ দশমিক ৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধির খবরটি সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, যা নাকি বিশ্বে সর্বোচ্চ। ২০০১-০৫ এর পাঁচ বছরে পাঁচবার বাংলাদেশ দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জন করেছিল। আবার ২০১৮ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জন করল ধনকুবেরের সংখ্যা বৃদ্ধির দৌড়ে। মার্কিন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ‘ওয়েলথ এক্স’-এর ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে ওই সময় ধনকুবের ছিল ২৫৫ জন। ধনাঢ্যরা এ দেশে যেভাবে নিজেদের আয় এবং ধন-সম্পদ লুকোনোতে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করে থাকেন তাতে হয়তো দেশে ধনকুবেরের প্রকৃত সংখ্যা আরো অনেক বেশি হবে। অথচ ২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশে নাকি আবারো সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে! আমি বলব, ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের ক্রমবর্ধমান প্রতাপের কারণে ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ৪৮ বছর ধরে বাংলাদেশে কয়েকশ রবার ব্যারনের উত্থান ঘটেছে। এ উত্থানের প্রধান সিঁড়ির ভূমিকা পালন করেছে নিচের প্রক্রিয়াগুলো:
১. ব্যাংক ঋণের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ; ২. বৈদেশিক ঋণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর পুঁজি লুণ্ঠন; ৩. সরকারের গৃহীত ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পগুলোর ব্যয় অযৌক্তিভাবে অতিমূল্যায়নের মাধ্যমে পুঁজি লুণ্ঠন; ৪. অস্বাভাবিকভাবে প্রকল্প বিলম্বিতকরণের মাধ্যমে পুঁজি লুণ্ঠন; ৫. ব্যাংকের মালিকানার লাইসেন্স বাগানো এবং ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডে নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের মাধ্যমে ব্যাংক ঋণ লুণ্ঠন; ৬. প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ ও প্রাইভেট টেলিভিশন স্থাপনের ব্যবসা; ৭. শেয়ারবাজার কারচুপি ও জালিয়াতির মাধ্যমে পুঁজি লুণ্ঠন; ৮. একচেটিয়ামূলক বিক্রেতার বাজারে যোগসাজশ ও দাম নিয়ন্ত্রণ; ৯. রিয়াল এস্টেট ব্যবসায়ে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও অত্যধিক দাম বৃদ্ধি; ১০. ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যাংক ঋণ খেলাপ ও বিদেশে পুঁজি পাচার; ১১. প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বখরা-ভাগাভাগির মাধ্যমে ব্যাংক ঋণ লুণ্ঠন; ১২. একের পর এক অযৌক্তিক মেগা প্রকল্প থেকে রাজনৈতিক মার্জিন আহরণ; ১৩. রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।
ওপরে যে ১৩টি প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে আমার মতে, বাংলাদেশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ব্যাংক ঋণ লুণ্ঠন। এ দেশের একটি ব্যবসা-গ্রুপকে ২২ হাজার কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ প্রদান করা হয়েছে বলে পত্রপত্রিকায় খবর বেরিয়েছে। আর একজন ব্যক্তি দেশের সাতটি ব্যাংকের ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেছে বলে জনশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে সরকারের কোনো পদক্ষেপ চোখে পড়ছে না। বরং তার বিরুদ্ধে তদন্ত চালানোর জন্য হাইকোর্টের একটি বেঞ্চের ‘সুয়োমোটো’ রুলকে সুপ্রিম কোর্টের ‘চেম্বার-জজের’ আদেশে থামিয়ে দেয়া হয়েছে। আরেকজন বাংলাদেশী বিলিয়নেয়ার সিঙ্গাপুরের ৪১তম ধনাঢ্য ব্যক্তি ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি কীভাবে এত অর্থ বিদেশে পাচার করলেন তা তদন্ত করার কোনো সরকারি তাগিদ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এ দেশের সরকারের শীর্ষ নেতৃত্বের আত্মীয়স্বজন বেশ কয়েকটি ব্যাংকের মালিক হয়ে গেলেও তারা কীভাবে মালিক হওয়ার শর্ত ন্যূনপক্ষে ২০ কোটি টাকা জমা দিলেন তার হদিস মিলছে না। বিংশ শতাব্দীর আশির দশক থেকে ‘ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপের’ মাধ্যমে ব্যাংক ঋণ লুণ্ঠনের অপসংস্কৃতি এ দেশে গেড়ে বসতে শুরু করে। ১৯৯১-৯৬ মেয়াদের বিএনপি সরকারের সময় খেলাপি ব্যাংক ঋণের সমস্যা সংকটে পরিণত হয়। ২০২৩ সালে প্রায় ১৬ লাখ কোটি টাকা ব্যাংক ঋণের মধ্যে খেলাপি ঋণের পরিমাণ সাড়ে ৪ লাখ কোটি টাকার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, যদিও বাংলাদেশ ব্যাংক কতগুলো টেকনিক্যাল কারণে খেলাপি ঋণ অনেক কম দেখাতে বাধ্য হয়। আমি নিশ্চিত যে এ দেশের রবার ব্যারনদের সিংহভাগ প্রধানত ব্যাংক ঋণ লুণ্ঠনের মাধ্যমে ধনকুবেরে পরিণত হয়েছেন। এ ব্যাংক ঋণের সিংহভাগ তারা বিদেশে পাচার করে চলেছেন।
বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬১টি। ১৯৮২ সালে স্বৈরাচারি এরশাদ সরকারের সময় নয়টি ফার্স্ট জেনারেশন প্রাইভেট কমার্শিয়াল ব্যাংক স্থাপনের অধ্যায় শুরু হয়। ১৯৯১-৯৬ মেয়াদে খালেদা জিয়ার আমলে ১০টি সেকেন্ড জেনারেশন ব্যাংক লাইসেন্স পায়। আর ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে শেখ হাসিনার সময় ১৩টি থার্ড ও ফোর্থ জেনারেশন ব্যাংক চালু হয়। প্রতি আমলেই ক্ষমতাসীন দল বা জোটের শীর্ষ নেতৃত্বের আত্মীয়-স্বজন, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, দল বা জোটের নেতারা কিংবা রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীরা ব্যাংকের লাইসেন্স বাগাতে সমর্থ হয়েছেন। এ অবস্থায় বর্তমান সরকারের মেয়াদে আরো ১৮টি ব্যাংকের লাইসেন্স প্রদানকে প্রয়াত অর্থমন্ত্রী মুহিত ‘রাজনৈতিক বিবেচনায় দেয়া হয়েছে’ বলে স্বীকার করেছেন। ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ৪৮ বছর ধরে ক্ষমতাসীন বাংলাদেশের প্রতিটি সরকার ‘ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের’ পূজারী ছিল। এরই অকাট্য প্রমাণ হলো, এই ব্যাংকের মালিকানা বণ্টনের মোচ্ছব, যেটা নিকৃষ্ট ধরনের রাজনৈতিক দুর্নীতি। বিনা মূলধনে কোটিপতি হওয়ার এত বড় যজ্ঞ অন্য কোনো দেশে চালু আছে কিনা আমার জানা নেই। ১৯৯১ সালের পর ৩২ বছরের মধ্যে ৩০ বছর ধরে ভোটে নির্বাচিত সরকারগুলো পালাক্রমে ক্ষমতাসীন হয়ে আসার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের মাধ্যমে রবার ব্যারন সৃষ্টিতে কোনো ভাটার টান পরিদৃষ্ট হয়নি, যদিও দলীয় রঙবদল ঘটে চলেছে রবার ব্যারনদের।
দেশে এতগুলো ব্যাংক থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যাংক আমানতের সংকটে না পড়ার পেছনে প্রধান ভূমিকা পালন করে চলেছে আনুমানিক ১ কোটি ৫৫ লাখ প্রবাসী বাংলাদেশীর রেমিট্যান্স প্রবাহ। আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে হোক বা হুন্ডির মতো অপ্রাতিষ্ঠানিক চ্যানেলে হোক, যেভাবেই রেমিট্যান্স দেশে আসুক না কেন তার সিংহভাগ ব্যাংকগুলোয় আমানত হিসেবে জমা পড়ে। কিছুদিন আগে অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন, প্রায় অর্ধেক রেমিট্যান্স এখন হুন্ডি পদ্ধতিতে দেশে আসছে। আমি মনে করি, বাংলাদেশের সিংহভাগ রেমিট্যান্স প্রেরকরা হুন্ডি পদ্ধতি ব্যবহার করছেন। অতএব, ২১-২২ বিলিয়ন ডলার যদি ফরমাল চ্যানেলে দেশে রেমিট্যান্স আসে তাহলে কমপক্ষে আরো ২১-২২ বিলিয়ন ডলার বা তার চেয়েও বেশি রেমিট্যান্স হুন্ডি পদ্ধতিতে দেশের অর্থনীতিতে ঢুকছে। বাংলাদেশ ব্যাংক গত ১৮ সেপ্টেম্বর জানিয়েছে, ১ কোটি টাকার বেশি আমানত রক্ষাকারী ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সংখ্যা দেশে এখন ১ লাখ ১৩ হাজার ৫৫৪। এসব অ্যাকাউন্টের উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রামীণ এলাকার ব্যাংক শাখাগুলোয়। প্রায় ১৬ লাখ কোটি টাকা ব্যাংক ঋণের মধ্যে প্রায় সাড়ে ৪ লাখ কোটি টাকা খেলাপি ঋণ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো যে বড়সড় সংকটে পড়ছে না তার পেছনে ফরমাল চ্যানেলে কিংবা হুন্ডি পদ্ধতিতে প্রেরিত রেমিট্যান্স থেকে উদ্ভূত বিশাল আমানত প্রবাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এক অর্থে, এ বিপুল রেমিট্যান্সের অর্থ বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের একটা তাৎপর্যপূর্ণ বিকল্পের ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, এ দেশের ব্যাংকগুলো কয়েকশ ‘রবার ব্যারন’ সৃষ্টি করতে পারছে প্রবাসীদের কষ্টার্জিত আয় ও রেমিট্যান্সের কারণেই। আর এই রবার ব্যারনরা ব্যাংক ঋণ বিদেশে পাচার করার ‘কালচার’ সৃষ্টি করে এখন অর্থনীতিকে টালমাটাল অবস্থায় নিয়ে গেছে।
ড. মইনুল ইসলাম: অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
বনিক বার্তা