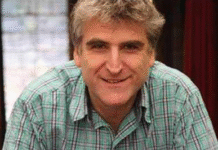- ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান
- ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ০৬:৫০
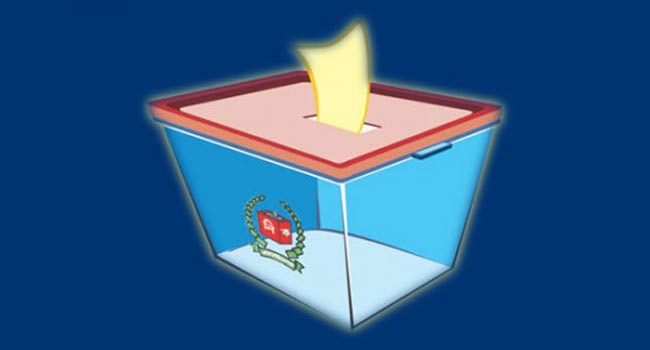
ইতিহাস প্রমাণ করে বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্রমনা। কারণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপট তৈরি করার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা-উত্তরকালের রাজনৈতিক গতিধারা যেমন, ছয় দফা ফর্মুলা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, গোলটেবিল বৈঠক, ১৯৬৯ সালে প্রস্তাবিত সংবিধান সংশোধনী বিল ইত্যাদির ভূমিকা ছিল পরোক্ষ। মূলত এ দেশের স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের রায় পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী না মানার কারণে। স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের পর বাংলাদেশের জনগণ প্রত্যাশিত গণতন্ত্রের পথে প্রথম যাত্রা শুরু করে।
কিন্তু ১৯৭৫ সালের ৪ জানুয়ারি তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বাকশাল তৈরি করে কর্তৃত্ববাদী শাসনের সূচনা করেছিলেন। বাংলাদেশের মানুষ তা মেনে নেয়নি। সৈনিক-জনতার নজিরবিহীন সমর্থনে শহীদ জিয়ার হাত ধরে দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের পথচলা শুরু হয়। কিন্তু আশির দশকে দেশ আবার স্বৈরশাসকের কবলে নিপতিত হয়। আবারো বাংলাদেশীরা এরশাদ স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। রাজনৈতিক দল, ছাত্র-শিক্ষক-জনতাসহ দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করে দেশকে স্বৈরাচার মুক্ত করার ক্ষেত্রে আপসহীন নেতৃত্বের মুখ্য দায়িত্ব¡ পালন করেন বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা শহীদ জিয়ার সুযোগ্য সহধর্মিণী গণতন্ত্রের মাতা বেগম খালেদা জিয়া। এর পর থেকে সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন-চর্চার শুভ সূচনা হয়। অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে পঞ্চম জাতীয় সংসদে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয়।
আপনারা সবাই অবগত আছেন, মইনউদ্দিন-ফখরুদ্দীনের নেতৃত্বাধীন ১/১১-এর সরকার ১৯৯৬ সালে প্রণীত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সব ধারা ভূলুণ্ঠিত করে দু’বছর ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখেন। পরবর্তী সময়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে আওয়ামী লীগ ১/১১-এর সরকারকে তাদের আন্দোলনের ফসল হিসেবে দায়মুক্তি দিয়েছিল। ওই সময় বিদেশীদের দৌড়ঝাঁপ ছিল চোখে পড়ার মতো। আওয়ামী লীগ সেটি নিয়ে নাখোশ ছিল না। কিন্তু এখন গণতন্ত্রের পক্ষে বিদেশীদের ইতিবাচক কোনো ভূমিকাকেও তারা সহ্য করতে পারছে না। বিষয়টি পরিষ্কার হলো যে, বিদেশীদের কথা তাদের পক্ষে গেলে ‘জায়েজ,’ বিপক্ষে গেলে ‘নাজায়েজ’। গত ২৩ আগস্ট ২০২৩-এ জোহানেসবার্গে ব্রিকস সম্মেলন চলাকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে বৈঠক করেছেন চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং। চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি অনুযায়ী, বৈঠকে চীনা প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ‘চীন বাংলাদেশের…বহিরাগত হস্তক্ষেপের বিরোধিতাকে সমর্থন করে, যাতে দেশটি অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও স্থিতিশীলতা বজায় রেখে উন্নয়ন ও প্রাণসঞ্চার করতে পারে।’
এই বক্তব্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে চীনের একধরনের হস্তক্ষেপ কি না সে বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার প্রধানের কোনো মন্তব্য জানা যায়নি। আওয়ামী লীগের সব পর্যায়ের নেতাকর্মী প্রতিনিয়ত অভিযোগ করে যাচ্ছেন, বিএনপি বিদেশীদের কাছে দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য ধরনা দিচ্ছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল সম্প্রতি ভারতের নয়াদিল্লি সফরে গিয়েছেন। ফিরে এসে শনিবার (১৮ ডিসেম্বর) বাংলাদেশ-ভারত সম্প্রীতি পরিষদের বিশেষ সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, ‘বাংলাদেশ-ভারতের সম্পর্কের ভিত্তি রক্তের। তাই দু’টি দেশের সম্প্রীতি রক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সকলকে এ ব্যাপারে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন’। তার এই বক্তব্যই প্রমাণ করে, বর্তমান সরকার দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বহিঃশক্তির অন্তর্ভুক্তি চায়না বলে যে দাবি করে, তা সঠিক নয়। বরং অনেকেই মনে করেন, তারা দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে, বিশেষ করে নির্বাচনের প্রাক্কালে বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ আমন্ত্রণ করে এসেছেন তাদেরকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার জন্য।
স্বাধীনতার পর মোট ১১ বার জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায়, ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ থেকে শুরু করে ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ছয়টি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি সংক্রান্ত নির্বাচন কমিশনের হিসাব নিয়ে তীব্র মতভিন্নতা নেই। প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট পড়েছে ২৬.৫ শতাংশ, দ্বিতীয়টিতে পড়েছে ৫১.৩ শতাংশ, তৃতীয়টিতে পড়েছে ৬১.৩ শতাংশ, চতুর্থটিতে পড়েছে ৫২.৫ শতাংশ, পঞ্চমটিতে পড়েছে ৫৫.৪ শতাংশ, সপ্তমটিতে পড়েছে ৭৫.৪৯ শতাংশ। তাই দেখা যায়, ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি নিয়ে কমিশন প্রদত্ত হিসাব নিয়ে সন্দেহ শুরু হয়। কিন্তু ২০১৪-এর ৫ জানুয়ারির নির্বাচন ভোটারবিহীন ও ২০১৮, ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন নৈশ ভোটের নির্বাচন হিসেবে জনগণ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়। নির্বাচন কমিশন ২০১৪তে ভোটার উপস্থিতি নথিভুক্ত করেছে ৪০ শতাংশ; প্রকৃতপক্ষে কোনো কোনো স্থানে যা ছিল মূলত ১০ শতাংশও কম। দেশবাসী জানেন, ২০১৪ সালে নির্বাচনে ১৫৩ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন, যা ছিল বিশ্ব-রেকর্ড। একাদশ সংসদ নির্বাচনে কত শতাংশ ভোট পড়েছে তা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। তবে পরে ৮০ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে বলে দাবি করা হয়েছে (গোলাম সামদানী, ‘কেমন ছিল দেশের ১১টি জাতীয় সংসদ নির্বাচন’, সারাবাংলা, ডিসেম্বর ৩১, ২০১৮)। ১৯৯১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত চারটি নির্বাচন হয়েছে। উল্লিখিত পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, প্রতিবারই ভোটাররা ক্ষমতাসীনদের হটিয়ে বিরোধী দলকে ক্ষমতায় বসিয়েছেন। নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন হওয়ায় ভোটাররা তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পেরেছেন; কিন্তু ২০০৮ সালের পর এই শক্তি কেড়ে নেয়া হয়েছে।
আওয়ামী লীগ সরকার জুন ৩০, ২০১১ সালে ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে সংযোজিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করে দেয়। দেশ কার্যত একদলীয় বাকশাল ব্যবস্থায় আবারো ফিরে যায়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যই তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করেছে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিলের পর আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত স্থানীয় কিংবা জাতীয় কোনো নির্বাচনই বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, স্বচ্ছতা, অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিযোগিতার মানদণ্ডে এসব নির্বাচন কোনো পর্যায়েই পড়ে না। দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন কতটা নিকৃষ্ট হতে পারে ২০১৪-এর ভোটারবিহীন জাতীয় সংসদ নির্বাচন এ ক্ষেত্রে একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।
জাতির জন্য আরেকটি কলঙ্ক তিলক হয়ে থাকবে নৈশ ভোট খ্যাত ২০১৮-এর নির্বাচন। ভোটের আগের রাতেই ব্যালটবাক্স ভরে রাখা এবং প্রশাসনের সর্বস্তরের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে ভোটারবিহীন একটি নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার অভিযোগে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছিল (১৫ জানুয়ারি ২০১৯, প্রথম আলো)। সুশাসনের জন্য নাগরিকসহ (সুজন) নানা সংস্থার কর্মরত বুদ্ধিজীবী ও গবেষকবৃন্দও প্রমাণসহ প্রায় অভিন্ন অভিযোগ করেছেন। অভিযোগের দীর্ঘ তালিকা এখনো বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংরক্ষিত আছে এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেক বিদেশী বিশেষজ্ঞ ও পর্যবেক্ষক ওই নির্বাচনকে বিশ্বে ‘সবচেয়ে ব্যর্থ’ নির্বাচন বলে অভিহিত করেছেন।
বাংলাদেশে গত এক যুগের বেশি সময় যাবৎ যে তথাকথিত ‘নির্বাচন’ ও ‘গণতন্ত্রের’ চর্চা হচ্ছে তা ব্যাখ্যা করার জন্য এই পরিভাষাগুলো যথার্থ বলে প্রতীয়মান হয়। এই সরকারের আমলে দেশে নির্বাচনব্যবস্থা কেবল ধ্বংসই হয়নি, এ ব্যবস্থাকে নিয়ে করা হচ্ছে রঙ্গ-তামাশা। সাধারণ ভোটারদের মনে তাই নির্বাচনব্যবস্থা নিয়ে একটা আশঙ্কাবোধ কাজ করছে। নির্বাচন কমিশনও পুরোপুরি অকার্যকর হয়ে গেছে। এর মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণগুলোর একটি হলো, দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব¡ পালনে ব্যর্থতা। এ বিষয়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী একসময় বলেছিলেন ‘রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকলে নির্বাচন কমিশন যত শক্তিশালী হোক না কেন, তাতে নির্বাচন নিরপেক্ষ হতে পারে না’ (দৈনিক ইত্তেফাক ১৬ জুন ১৯৯৪)। অথচ তার বর্তমান অবস্থান কী, তা কারো অজানা নয়।
এ প্রসঙ্গে যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান দ্য ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (ইআইইউ) এবং সুইডেনের গোথেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্যারাইটিজ অব ডেমোক্র্যাসি (ভি-ডেম) ইনস্টিটিউটের প্রতিবেদনের উল্লেখ করা যায়। ইআইইউ’র মাপকাঠিতে বাংলাদেশ একটি ‘হাইব্রিড শাসনব্যবস্থার দেশ। ‘হাইব্রিড’ শাসনব্যবস্থার দেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হয়, দুর্নীতি ব্যাপক বিস্তার লাভ করে ও আইনের শাসন দুর্বল হয়। ভি-ডেম ইনস্টিটিউটের প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রতীয়মান হয় বাংলাদেশে গণতন্ত্র বিকাশে উদার ধারার ব্যাপক অবনতি হয়েছে। ১৭৯টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৭ (স্কোর .১১)। এর অর্থ হলো, এ দেশে গণতন্ত্র অপসৃয়মাণ। এ প্রসঙ্গে আরো বিভিন্ন নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করা যায়; যাতে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ এখন এক চরম কর্তৃত্ববাদী শাসনের কবলে নিপতিত। জার্মান প্রতিষ্ঠান ‘বেরটেলসম্যান স্টিফটুং’ বিশ্বের ১২৯টি দেশের ওপর সমীক্ষা চালায়।
২০১৮ সালের ২৩ মার্চ প্রকাশিত রিপোর্টে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশকে স্বৈরতান্ত্রিক দেশ বলে তুলে ধরে। নিউ ইয়র্ক-ভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন ‘হিউম্যান রাইটস ওয়াচ’ (এইচআরডব্লিউ) অনেক আগেই বিবৃতি দিয়ে বলেছে, বাংলাদেশ সরকার আরো কর্তৃত্বপরায়ণ হয়ে উঠছে। বিশেষ করে ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে বাংলাদেশ অধিকতর স্বৈরশাসনের পথে এগোচ্ছে। গত বছর ৩০-৩১ জুলাই জেনেভায় জাতিসঙ্ঘের ‘নির্যাতন বিরোধী কমিটি’র ৬৭তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বলা হয়েছিল, গুম, রিমান্ড, বিচারহীনতা, ধর্ষণ, ভোটারদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা, নির্বাচনী সহিংসতা, তথ্যপ্রযুক্তি আইন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মতো আরো অনেক বিষয়ে তীব্র প্রশ্নবাণের মুখে পড়তে হয়েছিল বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের সদস্যদের। এমন জবাবদিহিতার মুখে উত্তর দিতে গিয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের সদস্যরা রীতিমতো খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন।
ওই অধিবেশনের বাংলাদেশ অংশটি পর্যালোচনা করলে বাংলাদেশে কর্তৃত্ববাদী শাসনের চেহারাটাও ফুটে ওঠে। কর্তৃত্ববাদে ব্যক্তি হয়ে ওঠে রাষ্ট্রের সমার্থক। ফরাসি সম্রাট চতুর্দশ লুই ( ১৬৪৩-১৭১৫) সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন, ‘আমিই রাষ্ট্র।’ গণতন্ত্রের নামে এখন বাংলাদেশে যা চলছে তা চতুর্দশ লুই-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্টিফেন ওয়াল্টের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কর্তৃত্ববাদী শাসনের দশটি লক্ষণ রয়েছে। লক্ষণগুলো হচ্ছে : ভীতি অথবা উৎকোচের মাধ্যমে তথ্যব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ; তাঁবেদার তথ্যব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা; প্রশাসন ও নিরাপত্তাব্যবস্থার দলীয়করণ; নিজ স্বার্থে নির্বাচনী ব্যবস্থায় জালিয়াতি; বিরোধী রাজনীতিকদের ওপর নজরদারির জন্য গোয়েন্দা সংস্থার ব্যবহার; অনুগত ব্যবসায়ীদের পুরস্কার, অবাধ্য ব্যবসায়ীদের শাস্তি; বিচারব্যবস্থা হাতের মুঠোয় নিয়ে আসা; শুধু এক পক্ষের ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ; ভীতি ও আতঙ্ক ছড়ানো; বিরোধী রাজনীতিকদের সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার। স্টিফেন ওয়াল্ট কর্তৃত্ববাদী শাসনের যে রূপরেখা তুলে ধরেছেন, তার সাথে বাংলাদেশের বর্তমান শাসন মিলে যাচ্ছে। কর্তৃত্ববাদী শাসকরা স্বৈরতন্ত্রকে বৈধ করতে মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে, গণতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করে নিজেদের সুবিধামতো। গণতন্ত্রের আগে বা পরে সুবিধামতো শব্দও জুড়ে দেয়। বাংলাদেশে ‘আগে উন্নয়ন, পরে গণতন্ত্র’ এমন একটি প্রচারণা সামনে নিয়ে আনা হয়েছে। রাজনৈতিক স্বার্থে গণতন্ত্রকে উন্নয়নের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। পাকিস্তান আমলে আইয়ুব খান ‘মৌলিক গণতন্ত্রের’ কথা বলেছিলেন। আর বর্তমান সরকার বলছে ‘উন্নয়নের গণতন্ত্র’। এভাবে কর্তৃত্ববাদী শাসনে গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা হারিয়ে যায়। সর্বক্ষেত্রে কর্তৃত্ববাদী শাসকের সার্বভৌমত্ব কায়েম হয়। বাংলাদেশে তা-ই হয়েছে।
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কিংবা আন্তর্জাতিক মিডিয়ার পর্যবেক্ষণ-মতামতের পাশাপাশি দেশের মানুষের অভিজ্ঞতাটা কম কষ্টকর নয়। যেমন, কর্তৃত্ববাদী শাসন কী, তা এই করোনা-মহামারীতে মানুষ অনেক স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ২৬টি পাটকল বন্ধের নির্মম সিদ্ধান্ত কেবল ২৫ হাজার শ্রমিকের জন্যই নয়, পাটশিল্পের সাথে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে যুক্ত লাখ লাখ মানুষের জন্য চরম হুমকিস্বরূপ। করোনা-মহামারীতে একের পর এক স্বাস্থ্য খাতের দুর্নীতির কাহিনী উঠে আসছে। করোনার মধ্যে গার্মেন্টস-এ শ্রমিক ছাঁটাই অব্যাহত ছিল। কর্তৃত্ববাদী শাসনের অন্যতম বড় একটি অনুষঙ্গ হলো লুটপাট। বাংলাদেশ যেন লুটেরাদের স্বর্গরাজ্য। প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার হচ্ছে। ওয়াশিংটন-ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ‘গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি’ (জিএফআই)-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে গড়ে পাচার হয়ে যাচ্ছে প্রায় ৬৪ হাজার কোটি টাকা। খেলাপি ঋণ ইত্যাদিও এ ক্ষেত্রে অতি প্রাসঙ্গিক। ক্যাসিনো সম্রাট থেকে পাপিয়া, ট্রাংক আর সিন্দুকে থরে থরে সাজানো টাকা, এসব বিষয় মানুষ ভোলেনি, ভোলার নয়। সরকারের সমালোচনা করায়, করোনা-মহামারীর সময় থেকে শুরু করে অদ্যাবধি বেশ কয়েকজন শিক্ষক, লেখক, সাংবাদিক, শিক্ষার্থী, অ্যাকটিভিস্টকে বাড়ি থেকে তুলে এনে ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনে মামলা ঠুকে দেয়া হয়েছে। তাদের জামিন দেয়া হচ্ছে না।
সাংবাদিক, লেখকরা ‘সেল্ফ-সেন্সরশিপে’ বাধ্য হচ্ছেন। আইনজ্ঞদের মতে, এই আইনের প্রায় সবগুলো ধারা ও উপধারা নাগরিকের মতপ্রকাশের সুরক্ষা ও স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার ও অন্যান্য নাগরিক অধিকারকে সীমিত ও ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষুণ্ন এবং নাগরিকের জনবান্ধব কর্মকাণ্ডকে অপরাধীকরণ করেছে। আইন প্রণয়নের সময় নাগরিক সমাজের যথাযথ অংশগ্রহণ এবং মতামত প্রদানের পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকার কারণে আইনটি সুরক্ষা প্রদানের পরিবর্তে কেবল নিয়ন্ত্রণমুখী নিপীড়নমূলক চেহারা ধারণ করেছে এবং এই আইনের মাধ্যমে মামলা করার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে যেমন দমন করা হচ্ছে তেমনি যেকোনো ধরনের বিরুদ্ধমতকে দমন করতে ভূমিকা পালন করছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী খাদিজাতুল কুবরার জামিন না হওয়া, বিচারের নামে ইতোমধ্যে অবিচারের ৩৬৫ দিন অতিবাহিত হওয়াই এর প্রমাণ। তথ্য যাচাইকারী প্রতিষ্ঠান ‘রিউমার স্ক্যানার’ তাদের ফেসবুক পেজে লিখেছে, ‘প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে ৫০ লাখ টাকা চিকিৎসা সহায়তা নিয়ে মির্জা ফখরুলের বিদেশ ভ্রমণ দাবিতে ভাইরাল, চেকটি ভুয়া।’ অথচ ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের চরিত্র হননকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করলেও ‘সরকারের সমালোচনাকারীদের খুঁজে বের করে কারাগারে আবদ্ধ রেখে জুলুম নির্যাতন করা হচ্ছে।
ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের নাম বদলে সাইবার সিকিউরিটি আইন করতে যাচ্ছে সরকার। কারাভোগ-এর পাশাপাশি অর্থদণ্ড যুক্ত হওয়া ছাড়া সাইবার সিকিউরিটি আইনের সাথে ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনের মধ্যে কার্যত মৌলিক তেমন কোনো পার্থক্য নেই। মোটকথা, কর্তৃতবাদী সরকারের ইচ্ছামাফিক চলছে সবকিছু। শৃঙ্খলা রক্ষার নামে পুলিশি নির্যাতন ও বিচারের নামে ফরমায়েশি রায়ের শিকার শিক্ষার্থী খাদিজা থেকে শুরু করে বিএনপির মহাসচিব, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, ও চেয়ারপারসন পর্যন্ত সবাই। এই সরকার টিকে থাকলে ক্রমেই তা আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। এমন দিন আসবে যে, নিজ দলের সাধারণ কর্মী-সমর্থকরাও জুলুম নির্যাতন থেকে রেহাই পাবেন না।
লেখক : প্রফেসর, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়