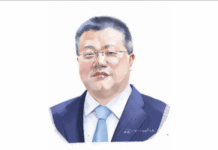‘ফ্রিডম ফ্রম ফিয়ার’

- ড. আবদুল লতিফ মাসুম ১৩ নভেম্বর ২০১৯

ফ্রিডম ফ্রম ফিয়ার বা ভীতি থেকে স্বাধীনতা মানবজাতির মৌলিক অধিকারের একটি। জাতিসঙ্ঘ চূড়ান্ত মানবাধিকার সনদ গ্রহণের আগেই এটি মৌলিক বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এর একটি পটভূমি রয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট ১৯৪১ সালে তার ‘স্টেট অব ইউনিয়ন’ বক্তৃতায় একে চারটি অনিবার্য স্বাধীনতার একটি বলে উল্লেখ করেন। পরবর্তীকালে তার বক্তৃতাটি ‘স্বাধীনতার চারটি সনদ’ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। স্মরণ করা যেতে পারে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপনিবেশ থেকে জাতিগুলোর স্বাধীনতা অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সময়ান্তরে তারাই আবার স্বাধীনতাবিরোধী ‘সাম্রাজ্যবাদী’ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। যা হোক, ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর যখন জাতিসঙ্ঘ ‘সার্বজনীন মানবাধিকার’ ঘোষণা করে, তখন ‘ভীতি থেকে মুক্তি’র বিষয়টি গৃহীত সনদের মুখবন্ধে স্থান পায়। ভীতি থেকে স্বাধীনতা বিষয়টি পৃথিবীব্যাপী তত্ত্ব ও তথ্য হিসেবে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়। ১৯৯৯ সালে মার্কিন ঐতিহাসিক ডেভিড এম কেনেডি বিষয়টির ওপর একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটির নাম ‘ফ্রিডম ফ্রম ফিয়ার : দি আমেরিকান পিপল ইন ডিপ্রেশন এন ওয়ার, ১৯২৯-১৯৪৫’। জানলে অবাক লাগবে, মিয়ানমারের আজকের রোহিঙ্গাদের নিপীড়নকারী অং সান সু চি ১৯৯১ সালে জনগণের মুক্তির লক্ষ্যে যে গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন তার নাম ‘ফ্রিডম ফ্রম ফিয়ার’। অন্যান্য মৌলিক স্বাধীনতাগুলো হচ্ছে- ১. বাক তথা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ২. স্বাচ্ছন্দ্যে ধর্ম-কর্ম করার স্বাধীনতা, ৩. ক্ষুধা থেকে মুক্তির স্বাধীনতা এবং চতুর্থটি হচ্ছে ৪. ভীতি থেকে স্বাধীনতা। মানবজাতি যে ক্রমেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে সভ্যতার সর্বোৎকৃষ্ট অবদান হিসেবে গ্রহণ করেছে, তার ভিত্তি হচ্ছে ওই চারটি স্বাধীনতার রক্ষাকবচসহ মৌলিক মানবাধিকারগুলো।
১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মানুষের মৌলিক অধিকার অস্বীকার করার কারণে সৃষ্টি হয় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে বাংলাদেশের মানুষ তাদের ‘জীবন প্রণালী’ হিসেবে গ্রহণ করে। প্রবর্তিত হয় সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যস্থা। স্বল্পকালের মধ্যে ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে প্রণীত সংবিধানে মৌলিক মানবাধিকারগুলো নিশ্চিত করা হয়। সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ২৬ অনুচ্ছেদ থেকে ৪৭ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত সবিস্তারে এসব মৌলিক স্বাধীনতার উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশে রচিত সংবিধান নাগরিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে একটি ভালো সংবিধান বলে সুনাম কুড়িয়েছে। কয়েকটি ধারা- জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষণ, গ্রেফতার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ, জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ, বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণ, চলাফেরার স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ে নাগরিকের মৌলিক অধিকার সংবিধান নিশ্চিত করেছে। প্রায় ৫০ বছর ধরে বাস্তব ও তত্ত্বের দ্বন্দ্বে সংবিধানের প্রায়োগিক অবস্থান যে প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে, সচেতন নাগরিক মাত্র নিশ্চয়ই তা অনুধাবন করেন।
এই জাতির দুর্ভাগ্য, স্বাধীনতার চেতনার দাবিদাররা ব্যক্তি স্বাধীনতাকে ক্রমেই সঙ্কুচিত করেছে। দুই বছর যেতে না যেতেই মূল সংবিধানের চেতনাবিরোধী দ্বিতীয় সংশোধনী আইন ১৯৭৩ উপস্থাপিত হয়। ‘অভ্যন্তরীণ গোলযোগ বা বহিঃআক্রমণে দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবন বাধাগ্রস্ত হলে জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধান’ সংযোজিত হয়। ১৯৭৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর সংশোধনীটি উপস্থাপন করেন। অবিলম্বে তা কার্যকর করা হয়। ১৯৭৪ সালে স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট বা বিশেষ ক্ষমতা আইন ঘোষিত হয়। এতে যে কাউকে অনির্দিষ্টকালীন সময়ের জন্য আটক রাখার বিধান করা হয়। অথচ এটি ছিল সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৩-এর হুবহু বিপরীত। ৩৩-এর (১)-এ বলা হয়েছিল, ‘গ্রেফতার করতে কোনো ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেফতারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত বক্তিকে তাহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাহার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।’
অনুচ্ছেদ ৩৩-এর (২)-এ বলা হয়েছে, ‘গ্রেফতারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে (গ্রেফতারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না।’ সংবিধানের এই অনুচ্ছেদের কার্যকারিতা কী পর্যায়ে পৌঁছেছে তা নাগরিক সাধারণ চোখ-কান খোলা রাখলে সহজেই দেখতে পাচ্ছেন। আবার সংবিধান সংশোধনীর দিকে তাকানো যাক। স্বাধীনতার যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও নিঃশেষ হয়ে যায়, বহুদলীয় রাজনীতির পরিবর্তে একদলীয় রাজনীতির প্রবর্তন এবং বাকশাল গঠন করা হয় সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি ১০ মিনিটের মধ্যে ড. তালুকদার মনিরুজ্জামান কথিত ‘সাংবিধানিক ক্যু’টি অনুষ্ঠিত হয়। দেশে একদলীয় শাসন কায়েম হয়। সামরিক শাসনের অবসানে গণতন্ত্রের শুভ সূচনা হয়। দেশের সবচেয়ে নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে বাকশালের প্রবক্তারা জয়লাভের খায়েশ পোষণ করলেও মানুষ তাদের প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৯৬ সালে মানুষকে বিভ্রান্ত করে তারা জয়লাভ করে। ২০০১ সালে জাতীয়তাবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে তারা বুঝতে পারে জনগণের ভোটে তাদের ক্ষমতায় ফিরে আসা সম্ভব নয়। শুরু হয় ষড়যন্ত্র ও ভীতির রাজত্ব। ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর দেশী-বিদেশী শক্তির যৌথ ষড়যন্ত্রে রাজপথে লগি-বৈঠার তাণ্ডব সৃষ্টি করে ভীতির নিকৃষ্ট মহড়া প্রদর্শিত হয়। পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র মোতাবেক সামরিক বাহিনীকে ক্ষমতায় আনা হয়। দুই বছরের সামরিক ভীতির রাজত্বের পর দলীয় ভীতির রাজত্বের সূচনা ঘটে। ২০০৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভীতির রাজত্ব তারা স্থায়ী রূপদানে সক্ষম হয়। গত ১২ বছরে দেশে হত্যা, ধর্ষণ, গুম, মামলা, হামলার এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়। সংবিধানের ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হয়। অথচ এটা ছিল ‘আন্দোলনের ফসল’। ভবিষ্যতে আর কোনো দল যাতে ক্ষমতায় যেতে না পারে, সে জন্য এ সংশোধনী আনা হয়। এর পর ২০১৪ সালের নির্বাচনে তারা ফাঁকা মাঠে গোল দেয়। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরের ‘নিশীথ রাত’-এর নির্বাচনে তারা পুলিশি ব্যবস্থায় জয়লাভ করে। এর সবগুলোই ভীতির রাজত্বের এক-একটি মাইলফলক।
সব রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সিভিল সোসাইটি, পেশাজীবী নেতৃবৃন্দ এবং সীমিত স্বাধীনতার গণমাধ্যম একমত যে, সারা দেশে ‘ভীতির রাজত্ব’ কায়েম করা হয়েছে। মিছিল দেখলেই পুলিশ হামলা চালায়। বিক্ষোভ দেখলেই তা অতি সাধারণ কারণে হলেও পুলিশ লাঠিপেটা করে। মানববন্ধনের মতো নিরীহ কর্মসূচি পুলিশ ছত্রভঙ্গ করে দেয়। বিরোধী দল সভা-সমাবেশের অনুমতি পায় না; অথচ সংবিধান মোতাবেক এ ধরনের কর্মসূচি পালন অনুমতির অপেক্ষা রাখে না। লাখ লাখ মামলায় বিরোধী নেতৃবৃন্দ জর্জরিত। অন্যায়-দুর্নীতির মামলা শাসকগোষ্ঠীর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বেগম খালেদা জিয়া অন্তরীণ। সম্প্রতি নিজেদের লালিত-পালিত সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিবাজদের আটক করে টলায়মান সিংহাসন রক্ষার যে প্রয়াস লক্ষ করা গেছে, তাও বিধিবদ্ধ ও আইনানুগ প্রক্রিয়ায় অগ্রসর না হওয়ার কারণে আরেক ভীতির রাজত্ব কায়েম হয়েছে। শাসক দলের শিক্ষার্থী অংশের তাণ্ডবে গোটা শিক্ষাব্যবস্থা যখন বিপর্যস্ত, তাদের দুর্নীতিবাজ ও দুঃশাসক ভিসিদের অন্যায় অপকর্মে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যখন এক রকম উত্তাল তখন নিয়মতান্ত্রিকভাবে এসবের মোকাবেলার পরিবর্তে আবারো ভীতির রাজত্বের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সুশীলসমাজ ভীতির আতঙ্ক ও আশঙ্কায় শঙ্কিত বোধ করছে।
আন্দোলনের নামে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যারা উসকানি দিচ্ছে, সেসব ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার হুমকি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, উসকানি দিয়ে শিক্ষার্থীদের ভুল পথে নেয়াকে কেউ মেনে নিতে পারে না। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উসকানি দিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। সবাইকে মনে রাখতে হবে, উচ্চশিক্ষার এসব প্রতিষ্ঠান সরকারি অর্থে পরিচালিত হয়। গত ৯ নভেম্বর রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জাতীয় শ্রমিক লীগের ১৩তম জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা- বাসস জানায়, প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘উসকানি দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিপথগামী করে আবার মিষ্টি মিষ্টি কথা বলা কখনোই মেনে নেয়া যায় না। আর তা যদি করতে হয়, তাহলে নিজেদের অর্থ নিজেদের জোগান দিতে হবে।’ তিনি বলেন, নিজেদের বেতন নিজেরা দেবে এবং নিজেদের খরচ নিজেরা চালাবে, সরকার সব টাকা বন্ধ করে দেবে। শেখ হাসিনা বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। সরকার কেন টাকা খরচ করবে, সেটাও চিন্তা করতে হবে, তারা কোনটা করবে? বিশ্বের আর কোথাও বাংলাদেশের মতো এত স্বল্প খরচে উচ্চশিক্ষার সুযোগ নেই।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, একজন বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া শিক্ষার্থীর মাসে শিক্ষা ব্যয় দেড় শ’ টাকার বেশি হয় না। যদি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যান, তবে দেখবেন কত লাখ টাকা লাগে প্রতি সেমিস্টারে। দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা খরচ হয় একজন শিক্ষার্থীর পেছনে। প্রকৌশল বা কারিগরি শিক্ষায় আরো বেশি টাকা খরচ হচ্ছে। কাজেই সেখানে শৃঙ্খলা থাকতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কী, আমরা তা বুঝি না। যারা পড়াশোনা নষ্ট করে সেখানে ধর্মঘট করে দিনের পর দিন কর্মঘণ্টা নষ্ট করবেন, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা ব্যাহত করবেন, তারাই সব বুঝবেন। আমরা বুঝব না, এটা তো হয় না। তিনি বলেন, অর্থ সরকার দেবে। সব উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। আর সেখানে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবে না, এটা হতে পারে না। তিনি আরো বলেন, দেশের আইনে আছে, কেউ যদি কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে এবং সেটি যদি প্রমাণিত না হয়, তাহলে অভিযোগকারীর ওই আইনে বিচার হয়, সাজা হয়। কাজেই যারা কথা বলছেন, তারা আইনগুলো ভালোভাবে দেখে নেবেন। তিনি বলেন- কথায় বলে স্বাধীনতা ভালো, কিন্তু তা বালকের জন্য নয়। এটাও মাথায় রাখতে হবে। দাবি মেনে নেয়ার পরও ক্ষেত্রবিশেষে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন প্রধানমন্ত্রী। আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেন, যে বাংলাদেশে ’৭৫-এর পর, হত্যা, ক্যু, ষড়যন্ত্রের রাজনীতি চলত; সেই বাংলাদেশ প্রায় এক দশকে অনেক এগিয়েছে। আজ যারা বড় বড় কথা বলেন, তাদের কোনো দিন ওই সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুনিনি; বরং তাদের পদলেহন করতেই দেখেছি। এটাই হলো বাস্তবতা। প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পর শিক্ষা-উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরীও একই ধরনের মন্তব্য করেন। উল্লেখ্য, কয়েক সপ্তাহ ধরে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন চলছে। বুয়েটে শিক্ষার্থীরা ক্লাসে ফেরেননি। অচলাবস্থা কাটেনি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ^বিদ্যালয়ের অব্যাহত আন্দোলন চলছে। পাবনা প্রযুক্তি বিশ^বিদ্যালয়ে উপাচার্য ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন চলছে। রোকেয়া বিশ^বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তিন দফা দাবিতে বিক্ষোভ ও মহাসড়ক অবরোধের মতো কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। দুই হলের শিক্ষার্থীদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার পর কুয়েট বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য কারা দায়ী, এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুব যে গবেষণার দরকার আছে এ রকম নয়। গণমাধ্যম তথা সংবাদপত্রের পাতা উল্টালে প্রতিদিন এর প্রমাণ পাওয়া যায়। নিজেদের শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার্থীরা লাঞ্ছিত হচ্ছেন। তারা সেখানের শাসক দলের টর্চার সেলে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। শিক্ষকরা অপমানিত হচ্ছেন। অধ্যক্ষকে পুকুরে ফেলে দিচ্ছে তারা। চাঁদাবাজি ছাড়া কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সাধিত হচ্ছে না। শাসক ছাত্রসংগঠনের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাণ হারাচ্ছেন নিরপরাধ শিক্ষার্থীরা। এককথায় নৈরাজ্য আর অরাজকতার লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে সামান্য বিরোধিতা ও ভিন্নমত পোষণের যে কোনোই অধিকার নেই, সেটি আবরার নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন। এর প্রতিবাদে জেগে উঠেছে সম্মিলিত শক্তি। শিক্ষার্থীদের কোনো বিশেষ দল বা সংগঠন এসব আন্দোলনে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেনি এবং নেতৃত্ব দেয়নি। সাধারণ ছাত্রসমাজ তাদের সতত ন্যায়বোধ এবং প্রতিবাদী চরিত্র থেকেই এসব অন্যায়ের বিরোধিতা করছে। বাংলাদেশে ছাত্রসমাজের এই প্রতিবাদী চরিত্র ইতিহাসের মতোই পুরনো। তারাই সৃষ্টি করেছে ’৫২, ’৫৪, ’৬২, ’৬৬ ও ’৬৯। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র-যুবাদের অংশগ্রহণই ছিল মুখ্য। সুতরাং অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা তাদের রক্তের উত্তরাধিকার। দুর্ভাগ্যের বিষয় ছাত্র-যুবাদের এই সাধারণ ও স্বাভাবিক প্রতিবাদকে সহজে গ্রহণ না করে এর মধ্যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র খোঁজা দুঃখজনক বৈকি! পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক আমলে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সব কিছু অবদমনের চিত্র আমরা দেখেছি। শক্তি প্রয়োগ কেবল শক্তি প্রয়োগের উসকানি দেয়। একজন যখন আঘাতপ্রাপ্ত হয়, অপমানিত হয়, নির্যাতিত হয়; তখন কাউকে বলে দিতে হয় না তুমিও রুখে দাঁড়াও। এমনিতেই শিক্ষাঙ্গনে একান্ত দলীয় প্রশাসক বসানো হয়েছে। তারা বিন্দু-বিসর্গও পর্যন্ত ছাড় দিতে নারাজ। বহিষ্কার, শাস্তি, দলীয় গুণ্ডাদের নির্যাতন এবং পুলিশি হয়রানি ও মামলায় শিক্ষার্থীরা দুর্দশাগ্রস্ত; তার ওপর রাষ্ট্রের অভিভাবকদের ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে স্বাধীনতা কেড়ে নেয়ার হুমকি খুবই দুর্ভাগ্যজনক।
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বুদ্ধিজীবী বলা হয়। বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনে এসব বুদ্ধিজীবীর গৌরবময় ভূমিকা ছিল। স্বায়ত্তশাসনের রূপরেখা ৬ দফা প্রণয়ন, অর্থনীতির ধারণা প্রতিষ্ঠিতকরণ, সংহতির ব্যর্থতা প্রমাণ এবং প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান সর্বজনস্বীকৃত। একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে তাদের মতো করে গড়ে উঠতে না দেয়ার দায়ও তাদের। ১৯৭২ থেকে এ পর্যন্ত একটি স্বকীয় ও বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে তারা দলীয় ভাষ্যকার তৈরি করেছেন। প্রতিবাদীরা ওই ঘরানায় টিকতে না পেরে সামরিক জান্তার পিছু হেঁটেছেন, এ কথাও সত্য। ১৯৯০-পরবর্তী গণতান্ত্রিক শাসনকালে মানুষের আশা ছিল ‘একটি সমৃদ্ধ বুদ্ধিজীবী শ্রেণী’- গণতন্ত্রের দীক্ষাকে যারা এগিয়ে নেবেন। কিন্তু তার বিপরীত চিত্রই প্রকাশ হয়েছে। এখন এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে ভীতি দ্বারা স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। বুদ্ধিজীবীদের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। তারা সাদাকে সাদা আর নীলকে নীল বলতে পারেন না। অথচ সমাজের মেধাবী অংশ হিসেবে তাদের সেই উত্তরাধিকার থাকার কথা। বঙ্গবন্ধু তাদের সেই উত্তরাধিকার দিয়েছেন। ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাদেশ ঔপনিবেশিক চরিত্রকে পাল্টে দেয়। বুদ্ধিজীবী ড. মস্তফা নুরুল ইসলাম সাক্ষ্য দিচ্ছেন, বঙ্গবন্ধু বুদ্ধিজীবীদের স্বকীয় স্বাধীন ভূমিকা সম্পর্কে আশ্বস্ত হতে চেয়েছেন। তাই আসুন অনেক চড়াই-উতড়াই পেরিয়ে, গ্লানি-দুঃখ-বিষাদ অতিক্রম করে আমরা দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করি- ‘উই ওয়ান্ট ফ্রিডম ফ্রম ফিয়ার’।
লেখক : অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
Mal55ju@yahoo.com