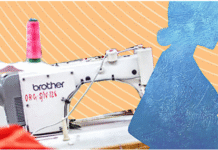সন্দেহ নেই বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বর্তমানে বাংলাদেশের সনাতন সমাজব্যবস্থা, রাজনৈতিক অর্থনীতি, প্রাকৃতিক পরিবেশ এক যুগসন্ধিক্ষণে রয়েছে। কঠিন সময় পার করছে মানুষ ও প্রকৃতির মেলবন্ধন পরিস্থিতি। আস্থা-অনাস্থার অনুভব, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনের টালমাটাল মোহনায় সবাই। জনগণের উপলব্ধিতে জমছে নিত্যনতুন বিস্ময়, অনির্বচনীয় সব আচার-আচরণ এবং পদ্ধতি প্রক্রিয়ার হরেকরকম উত্থান-পতন। স্থান-কাল-পাত্রভেদে সবাই যাতে নাটকীয়তায় মেতে থাকে তেমনিভাবেই যেন চলছে সাজানো সব কিছু। কূটকৌশল শাস্ত্রে এটিকে ‘স্বার্থজড়িত মূল বিষয় থেকে দৃষ্টি ফেরানোর উৎকৃষ্ট উপায়’ কিংবা বঙ্গীয় বাগধারায় যাকে ‘ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের’ সাথে তুলনা করা হয়।
এই বিশাল ব্যাপক পরিবর্তনের পেছনে সংস্কার কর্মযজ্ঞের ব্যবহার অপব্যবহার অপপ্রয়োগ অপপ্রয়াসের মাত্রাগত ওঠানামা যেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে তেমনি বৈষম্যবিহীন বাংলাদেশ নির্মাণের আকিঞ্চন আকাক্সক্ষা মনোযোগে মানোমালিন্যের সুর শোনা যাচ্ছে। কৃষিজমিতে ধান ফল ফসল উৎপাদনের চেয়ে সেখানে লোনাপানি তুলে পরিবেশ বিপন্ন করে মাছ চাষের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আপাত আর্থিক লাভ ঘটায় বটে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে টেকসই উন্নয়নের জন্য তা কতটা কার্যকর বা কতটা সুবিবেচনাপ্রসূত প্রয়াস তা পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা উঠে আসে। যেকোনো সংস্কার প্রয়াস তখনই তাৎপর্যবহ হবে যখন দেখা যাবে ন্যূনতম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ব্যতীত, বর্জন ও অর্জনের মধ্যে দূরত্ব দৃশ্যগোচর হয়ে মানবসম্পদসহ দেশজ সম্পদ ও সেবা উৎপাদন নিরাপত্তা ও নির্ভরতার সাথে অব্যাহত রয়েছে। সবক্ষেত্রে রোপিত দুর্নীতি যেমন সুনীতিকে বাজার থেকে ঝেটিয়ে লাঠিয়ে ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছে তেমন হাইব্রিড ভাব ভাবনারা অনুভবের হাটে মাঠে-ঘাটে নানান ফন্দি-ফিকির এঁটে চলেছে। অনেকের অসাবধান অশালীন উচ্চারণে সামাজিক সৌহার্দ্যরে পরিবেশ পঙ্কিলতায় ভরে যাচ্ছে।
এ কথা ঠিক, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটানো ধ্রুপদ ও ধীরগতির কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা দিয়ে সম্ভব নয়। জমিতে আগে একটি ফসল (আমন ধান) ফলানো হতো এখন তিন তিনটি ফসল ফলানো হচ্ছে। ক্ষয়িষ্ণু জমির উর্বরা শক্তি ঠিক রাখার জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে উচ্চ ডোজের সার ও কীটনাশক। এক দিকে বর্ধিত উৎপাদনের উপকারিতা অপর দিকে, প্রক্রিয়াগত স্বল্পসময়ে অধিক উৎপাদনের মওকায় প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি, মানব ও জীবদেহে সংক্রামিত রোগব্যাধির প্রকোপে দেশে এবং বিদেশী মুদ্রার ব্যয় (বাজেটের প্রায় ২০ শতাংশ) বাড়ছে। উপকার এবং অপকারের সালতামামি সমন্বয় করে দেখা যায়, তথাকথিত উন্নয়নের জন্য মূল্য দিতে হচ্ছে সবাইকে। অথবা কোনো উন্নয়নই বিনা বাক্য ব্যয়ে কিংবা লেনদেনে হয় না।
নগরায়ণ বাড়ছে। গ্রামের মানুষ জীবন ও জীবিকার টানে নগরে পাড়ি জমাচ্ছে। শহরে সেই মানুষের ঠাঁই দেয়ার সামর্থ্য নেই, ফলে শহরের উপকণ্ঠের গ্রামও শহরে রূপান্তরিত হচ্ছে দ্রুত। গ্রামের টাটকা ফল-ফলারি মাছ, গোশত, দুধ- সবই এখন শহরে বর্ধিত চাহিদা মেটাতে চলে যাচ্ছে। গ্রামের মানুষ শহরে গিয়ে গ্রামের সামগ্রীর চাহিদা সৃষ্টি করছে আর যারা গ্রামে থাকছে তারা আর পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার পাচ্ছে না। তারা অধিক লাভের আশায় তাদের সনাতন চাষপদ্ধতি বাদ দিয়ে আধুনিক চাষবাস ব্যবহার করে হাইব্রিড উন্নয়নের পথে পা বাড়াচ্ছে। কেননা, স্ফীতকায় নগরের চাহিদা মেটাতে হচ্ছে তাদের। আর গ্রামের মানুষ শহরে এসে বন্দিত্ব বরণ করছে সীমাবদ্ধ নাগরিক জীবনে। তাদের খেলার মাঠ নেই, সাঁতার কাটার পুকুর নেই, উদার উন্মুক্ত বাতাস সেবনের সুযোগ নেই। যন্ত্রের মতো নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত হতে গিয়ে তাদের পারিবারিক ঐক্য, পাড়া প্রতিবেশীর প্রতি মমতা, সামাজিক সখ্য সবই হারাতে হচ্ছে। একে কি যথার্থ জীবনযাপন বলে? প্রত্যেকের জীবন যার যার তার তার। গ্রামের জীবন আর শহরের জীবনের মধ্যে সমান্তরাল সাযুজ্য হারানোয় এখন শহরে বড় হচ্ছে যে শিশু সে গ্রামকে আর জানতে পারছে না- টাটকা ফল-ফসলের পরিবর্তে জাঙ্ক ফুড, প্রক্রিয়াজাত ফুড গ্রহণ করতে করতে নগরায়ণের সীমাবদ্ধ সময় ও পরিসরে তার জীবনকে যেন ই-পদ্ধতি প্রক্রিয়ার ছকে বেঁধে ফেলছে। একসময় সুযোগ পেলেই সব সম্পর্ক ছিন্ন করে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে। জীবন ও জীবিকার সন্ধানে মানবের বিশ্ব ভ্রমণ নতুন কোনো বিষয় নয়, দেশ-দেশান্তরে মানুষ প্রত্যাবাসিত হয়েছে, পাচার হয়েছে। ভারতবর্ষের মানুষ সুদূর আফ্রিকার মরিশাস, ফিজি, এমনকি ল্যাটিন আমেরিকার ত্রিনিদাদ টোবাগোতেও গেছে। সিল্ক রুট দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ ভারতবর্ষ হয়ে সুদূর চীন ও সাইবেরীয় হিমাঞ্চলে প্রবেশ করেছে। আজ আমরা টেকনাফ দিয়ে ছোট যানে মানুষকে মালয়েশিয়া যেতে দেখে কিংবা থাইল্যান্ডের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাংলাদেশীদের বন্দী জীবনযাপনের খবরে শিউরে উঠছি; কিন্তু কেন এই বীড়ফঁং তা ভেবে দেখছি না।
তাদের যাতে এভাবে যেতে না হয়, কিভাবে উন্নত উপায়ে নিরাপত্তার সাথে সম্মানের সাথে এই প্রত্যাবাসন হয় সেটি আধুনিক যুগের নেতৃত্বকে দেখতে হবে। টেকসই উন্নয়নের কথা যদি বলি, মানবসম্পদ পাচারের এই প্রবণতা সঠিক ধারায় আনা দরকার। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এই যোগাযোগের দুয়ার খুলতে কূটনৈতিক উদ্যোগ আধুনিক সরকারের তরফে যেমন জরুরি তেমনি যারা যাবেন তারা যেন যথা প্রশিক্ষিত ও প্রবুদ্ধ হয়েই বিদেশে পাড়ি- জমান সে জন্য দেশে উপযুক্ত শিক্ষা ও বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টির বিকল্প নেই।
শিক্ষা মানুষকে চক্ষুষ্মান করে; শিক্ষায় মানুষের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা শক্তি জেগে ওঠে। শিক্ষা মানুষের দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে, তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ, সবাক, সকর্ম করে তোলে। মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার যেমন বিকল্প নেই, জাতীয় জীবনমানের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষায় বিনিয়োগেরও তাই কোনো বিকল্প নেই।
একটি বৃক্ষের সুস্থ ও সবল হয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে হলে প্রাথমিক পর্যায়ে তার প্রকৃত পরিচর্যা প্রয়োজন। দেখভালের প্রয়োজনীয়তা এ জন্য জরুরি ও আবশ্যক। গাছটির কোনো অংশ ক্ষতিগ্রস্ত, জরাগ্রস্ত, দুর্দশাগ্রস্ত হলে পরে তা অপরাপর অংশে সংক্রমণের আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠবে এবং একসময় গোটা গাছই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
ইদানীং পরীক্ষাব্যবস্থাকে মূল্যায়নমুখী দেখার পরিবর্তে পাস বা গ্রেডনির্ভর ভাবা হচ্ছে; আর এর পরিসংখ্যান পরিব্যাপ্তির প্রাগ্রসরমানতায় পরিতৃপ্তিবোধ দেখা যায়। মশহুর ইংরেজ কবি স্যামুয়েল টেইলর কোলরিজের এনশিয়েন্ট মেরিনার যেমন সমুদ্রে চারিদিকে থৈ থৈ করা পানি দেখেও তার তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারেননি (ডধঃবৎ ধিঃবৎ বাবৎুযিবৎব হড়ৎ ধহু ফৎড়ঢ় ঃড় ফৎরহশ)। তেমনি লক্ষকোটি শিক্ষিতের মধ্যেও চাকরিতে উপযুক্ত প্রার্থী মিলছে না। বাইরের শিক্ষিত লোক এসে চাকরির বাজার মাত করছে বেকারের ভারে ন্যুব্জ এই অর্থনীতিতে। উচ্চতর শিক্ষায়তনে ভর্তির দুয়ারে গিয়ে অনেককেই অপারগতায় ঠাঁয় দাঁড়ানো দেখতে হচ্ছে।
শিক্ষার তো মূল্যবোধ জাগ্রত করার কথা, মূল্যবোধের অবক্ষয়ের উপলক্ষ হওয়ার কথা নয়। শিক্ষার্থীর মনে ভালো-মন্দ জ্ঞানের বিকাশ, দায়-দায়িত্ববোধ, স্বচ্ছতা ও নৈতিকতার আচরণের উদগাতা ও উপলব্ধির উপলব্ধি, পারঙ্গমতা তথা দক্ষতা ও যোগ্যতা সৃষ্টির জন্য যদি না হয় শিক্ষা; বরং শিক্ষা যদি হয় ঠিক বিপরীত তাহলে তার চেয়ে দুঃখজনক অবস্থা আর কী হতে পারে? প্রযুক্তি শিক্ষা প্রৎকর্ষতা অর্জনের জন্য, প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে নতুন পথে নতুন উদ্যমে সময় ও সামর্থ্যকে সাশ্রয়ী করে তুলে অধিক সক্ষমতা অর্জনের জন্য। শিক্ষা ও প্রযুক্তি যদি অসৃজনশীল, অপচয় অপব্যয় অপঅভ্যাস গড়ে তোলার পথ পায় তাহলে তো সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।
ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ বছরে, ১৮৯৯ সালে, সেই ঔপনিবেশিক শাসনামলে, এ দেশেরই একজন সরকারি স্কুল পরিদর্শক, আহ্ছানউল্লাহ (পরবর্তীকালে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লাহ) তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, মাইলের পর মাইল হেঁটে, নিজের সাথে আহারাদি পাচকসহ পরিপাকের উপায়-উপকরণ বয়ে নিয়ে তিনি স্কুল পরিদর্শন করতেন। পরিদর্শিতদের পক্ষ থেকে তাকে কোনো প্রকার পরিষেবার সুযোগ তিনি দিতেন না। দায়িত্বশীলতার সাথে প্রণীত তার প্রতিবেদন সুদূরপ্রসারী মূল্যায়নধর্মী ফলাফল নিয়ে আসত। ঠিক এই অবস্থার বিপরীতে এই অতি সাম্প্রতিককালেই যদি শোনা যায়, দেশের কেন্দ্রীয় শিক্ষা নিরীক্ষা ও পরিদর্শন অধিদফতরের কর্মকর্তা খোদ ঢাকায় বসে ৬০০ কিলোমিটার দূরের কোনো শিক্ষায়তনের প্রধান শিক্ষককে তার ‘পরিদর্শন ছক’ পূরণ করে ‘টাকা’ নিয়ে কেন্দ্রে আসতে বলতেন। টাকার পরিমাণ অনুযায়ী নাকি মিলত তার সুপারিশ সনদ-প্রতিবেদন যাই-ই বলি না কেন। যিনি নিজে এত বড় দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছেন তিনি কিভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতার জবাবদিহির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দেবেন? তার তথাকথিত প্রতিবেদনের ওপরই ওই বিদ্যায়তনের গেজেট ও এমপিওভুক্তি, সরকারি তহবিল থেকে শিক্ষকদের পুরো বেতনপ্রাপ্তি কত কিছু নির্ভর করে।
পল্লী অঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠদান পরিবেশ, ব্যবস্থাপনার সুযোগ সুবিধার সাথে শহরের শিক্ষায়তনগুলোর মধ্যে দূরত্ব বেড়েই চলেছে, মফস্বল থেকে পাস করা মেধাবী ছাত্ররাও শহরের শিক্ষায়তন থেকে পাস করাদের সাথে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না। এভাবে দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যে মেধার বিকাশ সীমিত ও শর্তসাপেক্ষ হয়ে পড়ছে। দেশের ভবিষ্যৎ মানবসম্পদ তৈরির ক্ষেত্রে এই বৈষম্য সৃষ্টি উদ্যোগ তথা অপয়া অবস্থা দেশ ও জাতির জন্য অশেষ দুর্ভোগ বয়ে আনতে পারে। মেধাশূন্য বিপুল জনগোষ্ঠী সম্পদ না হয়ে সহস্র সমস্যার শৈবালদামে পরিণত হয়ে দেশ ও জাতির বহমানতা ব্যাহত করতে থাকবে।
সেবার ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. এ পি জে আবদুল কালাম বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। স্থানীয় একটি টেলিভিশন চ্যানেলের তরফ থেকে ৮৩ বছর বয়সী এই চিরতরুণ তত্ত¡বিদকে প্রশ্ন করা হয়েছিল- গোটা উপমহাদেশের টেকসই উন্নয়ন অভিপ্সায় তার বার্তা কী? তিনি পরামর্শে সোজাসাপটা বলেছেন- ১, বাড়িতে পিতা-মাতা ও ২, প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষককে দায়িত্বশীল হতে হবে, তাদেরকে দায়িত্বশীল পেতে হবে। তাদেরকে দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ পেতে হলে তাদের প্রতি বলিষ্ঠ সুনজর দিতে হবে। জাপানে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষককে সবিশেষ সযত্ন ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখার জন্য রাষ্ট্র সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। পরিবারে পিতা-মাতা কোনোভাবেই ভবিষ্যৎ পরিবার দেশ ও সমাজে উপযুক্ত সদস্য সরবরাহে অমনোযোগী হতে পারেন না। সন্তানকে উপযুক্ত আদর্শ, মূল্যবোধ ও চেতনাদাতা হিসেবে তারা তাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব পালনে পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতির স্বার্থে অবশ্যই মনোযোগী হবেন। আর সরকার পরিবার, সংসার, সমাজ ও দেশে অনুকূল পরিবেশ সৃজনে, নিয়ন্ত্রণে, উদ্বুদ্ধকরণে, প্রণোদনে, প্রযত্ন প্রদানে অর্থনৈতিক রাজনীতি নিষ্ঠায়, ন্যায়নির্ভরতায়, স্বচ্ছতায়, জবাবদিহিতে, সুস্থ সাংস্কৃতিক সৌহার্দ্য-সখ্যতার পরিবেশ নিশ্চিত করবেন। সে নিরিখে মানবসম্পদ তথা সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে নবযুগের যে শিক্ষার দরকার সেই শিক্ষার পথে আমরা আছি, উঠব ও থাকব কি না আসন্ন বাজেটে তার যেন পরিকল্পনা প্রকাশ পায়।
লেখক : সাবেক সচিব, এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান