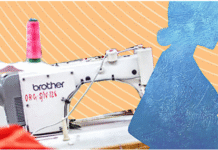- ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন
- ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১

বহু দিন ধরে একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট বিভিন্ন নামী-দামি কোম্পানি ও ব্র্যান্ডের ওষুধ নকল, ভেজাল পন্থায় তৈরি ও বাজারজাত করে আসছে। এ খাতে লেনদেন হচ্ছে কোটি কোটি টাকা। দেশের বিভিন্ন জেলায় রয়েছে নকল ওষুধ তৈরির কারখানা ও গোডাউন। গোয়েন্দা, র্যাব, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, ওষুধ প্রশাসন ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত অভিযানে যে চিত্র ফুটে উঠেছে তাকে ভয়াবহ বললে কম হবে। ভেজাল ও নকল ওষুধ সেবন মানুষের মৃত্যুঝুঁকি করোনার চেয়ে বাড়িয়ে দিচ্ছে। রোগাক্রান্ত মানুষ সুস্থ হওয়ার জন্য ওষুধ সেবন করে কিন্তু নব ও নিম্নমানের ওষুধ খেয়ে আরো অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। ভালো চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সুনাম ক্ষুণ্ন হচ্ছে। রোগী ও রোগীর স্বজনরা চিকিৎসকের ওপর আস্থা হারিয়ে উন্নত চিকিৎসার প্রত্যাশায় বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন। জেল, জরিমানা, গোডাউন সিলগালা করেও এই অপতৎপরতার সিন্ডিকেট ভাঙা যাচ্ছে না। অপরাধের সাথে যুক্ত কেউ গ্রেফতার হলে আদালতের প্রভাবশালী ও বড় আইনজীবীর প্যানেল নিয়োগ করে জামিনে বেরিয়ে যায় এবং আবার শুরু করে ভেজাল ব্যবসা। অসাধু ওষুধ ব্যবসায়ীদের টাকার অভাব নেই, বিনিয়োগের পুরোটাই লাভ। ভেজাল ওষুধের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে ময়দা, চকপাউডার ও প্রিজারভেটিভ যা মানহীন সোডিয়াম বেনজোয়েট ও বেনজয়িক এসিড থেকে তৈরি। ভেজাল ওষুধের ইনগ্রিডিয়েন্টসে মূলত প্রয়োজনীয় কোনো সক্রিয় উপাদান থাকে না। নন-ফার্মাসিউটিক্যালস গ্রেডের কেমিক্যাল ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া নিম্ন গ্রেডের মেইন স্টার্চ, স্টেরয়েড ও ডাই (রঙ) ব্যবহার করা হয়, যা মানবদেহের ভাইটাল অর্গানগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করে দিতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে ‘এটি গণহত্যার শামিল’।
ডেঙ্গু, করোনা, ক্যান্সার, ফুসফুস প্রদাহ, মস্তিষ্কের যন্ত্রণা, লিভার সিরোসিস, হৃদরোগ, কিডনি-ব্যাধি, স্নায়ুবৈকল্য, আইসিইউ, এইচডিইউ, সিসিইউয়ের মেডিক্যাল সরঞ্জামসহ প্রায় সব রোগের নব ও ভেজাল ওষুধে বাজার সয়লাব। নকল জীবন রক্ষাকারী ওষুধেরও দেদার বিকিকিনি চলছে। ঢাকার মিটফোর্ড ও চট্টগ্রামের হাজারি গলি ওষুধের পাইকারি বাজার। এই দুই বাজারে দৈনিক বিক্রির পরিমাণ ১০ কোটি টাকার বেশি। সরকারি ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ ও আমদানি নিষিদ্ধ বিভিন্ন ওষুধও এখানে পাওয়া যায়। এসব ওষুধ কিনে মানুষ প্রতিনিয়ত প্রতারিত হচ্ছেন, পড়ছেন মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ গত ৩ সেপ্টেম্বর রাজধানীর ডেমরার কাজলা, আরামবাগ ও মিটফোর্ড এলাকায় অভিযান চালিয়ে নকল ওষুধ তৈরি ও বিক্রির অভিযোগে সাতজনকে গ্রেফতার করেছে। জব্দ করা হয়েছে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নকল ওষুধ ও ওষুধ তৈরির সরঞ্জাম। তারা এখন পুলিশ রিমান্ডে আছে। মফস্বলের ওষুধ ফার্মেসিগুলোকে টার্গেট করে একটি অসাধু চক্র সারা দেশে ভেজাল ও নকল ওষুধ ছড়িয়ে দিচ্ছে। এ ধরনের ওষুধ মারণফাঁদ যা মাদকের চেয়েও ভয়াবহ। ২০১৯ সালের জুনে এক মামলার শুনানিতে ওষুধ প্রশাসন অধিদফতর হাইকোর্টকে জানায় যে, বিগত তিন মাসে ৩৪০.৭৫ মিলিয়ন টাকার ভেজাল ও মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ ধ্বংস করা হয়েছে। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জরিমানা আদায় করা হয়েছে ১৭.৪৯ মিলিয়ন টাকা। মামলা দায়ের করা হয়েছে ৫৭২টি। এটি তিন মাসের হিসাব। গোটা বছর কী হয় ও হচ্ছে; তা সহজে অনুমেয়। বাংলাদেশী মানুষের জীবন আসলে চ্যালেঞ্জের মুখে।
২০১৫ সালে হাজারি গলির ফার্মেসির মালিকরা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান ব্যর্থ করে দেন। গলির ভেতরে প্রবেশ করার আগেই মালিক-কর্মচারীরা অভিযান পরিচালনাকারীদের ওপর চড়াও হন। একযোগে বন্ধ করে দেয়া হয় সব দোকান।
গ্রেফতারদের মুক্তির দাবিতে মিছিল ও সমাবেশ করে বাংলাদেশ কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট সমিতি। চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। মিটফোর্ড ও হাজারি গলির সব ওষুধ ব্যবসায়ী অসাধু এ কথা অসত্য। এমন সৎ ব্যবসায়ীও আছেন যারা ন্যায্য ও সাশ্রয়ী মূল্যে ভোক্তাদের মানসম্মত ওষুধ সরবরাহ করে থাকেন। এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে জানা যায়, ওষুধের দ্বিতীয় বৃহত্তম পাইকারি বাজার চট্টগ্রামের হাজারি গলিতে রয়েছে ভেজাল, মেয়াদোত্তীর্ণ, অনুমোদনহীন ওষুধের ৪৫টি গোডাউন। প্রশাসনের কাছে এর তালিকা রয়েছে। এখান থেকে লাখ লাখ টাকার নকল-ভেজাল ও ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ সরকারি ওষুধের হরদম চলছে বেচাকেনা। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল ও জেনারেল হাসপাতালের রোগীদের জন্য বরাদ্দকৃত সরকারি ওষুধগুলো হাজারি গলির বিভিন্ন দোকানে বিক্রি হচ্ছে। এসব ওষুধ আবার চলে যাচ্ছে চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় ফার্মেসিগুলোতে, যার কারণে ফার্মেসিতে অভিযান চালালেই মিলছে বিক্রি নিষিদ্ধ ও মানহীন ওষুধ। গত বছর ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়ে ৩০টি ফার্মেসিকে ২৯টি মামলায় ১০ লাখ ৯৩ হাজার টাকা জরিমানা করে। চলতি বছরও অভিযান চালিয়ে দুই লাখ ৮০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয় (পূর্বদেশ, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২১)।
সাভার, ঢাকার ডেমরা ও কাজলা, নীলফামারী, পিরোজপুর ও রাজশাহীতে রয়েছে নকল ওষুধ তৈরির কারখানা। অসাধু ব্যবসায়ীরা দেশজুড়ে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে বিপণনের উদ্দেশ্যে। যেসব ওষুধের কাটতি বেশি এবং চিকিৎসকরা অধিকহারে ব্যবস্থাপত্র দেন ওইগুলোই নকল ব্যবসায়ীদের প্রথম টার্গেট। এর মধ্যে মোনাস, সেকলো, প্যারাসিটামল, ন্যাপ্রক্সেন প্লাস, সেফ-৩, এক্স ক্যাল, নভোর্যাপিড পেনফিল, এমটিএক্স প্রভৃতির নাম শীর্ষে। পাঠকের মনে আছে, ১৯৮২ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ভেজাল প্যারাসিটামল সিরাপ সেবনে কিডনি অকেজো হয়ে ৭৬ শিশুর মৃত্যু হয়। বিষয়টি সে সময় ব্যাপক আলোড়ন তোলে। পরে তদন্ত ও ল্যাব পরীক্ষায় ধরা পড়ে, পলিক্যাম ল্যাবরেটরিজসহ পাঁচ কোম্পানির তৈরি করা প্যারাসিটামল সিরাপে বিষাক্ত পদার্থ ডাই-ইথিলিন গ্লাইকলের উপস্থিতি ছিল।
ভেজাল ও নকল ওষুধ তৈরি ও বিপণনের বিরুদ্ধে দেশে যেসব আইন আছে, তা অপর্যাপ্ত ও পুরনো। ১৮৬০ সালে প্রণীত ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২৭৪, ২৭৫ ও ২৭৬ ধারায় ছয় মাসের কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। ১৯৪০ সালে প্রণীত ড্রাগস অ্যাক্টের (Act No. XX111, 1940) ৪ অধ্যায়ের ২৭ নম্বর ধারায় শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে কারাদণ্ড তিন বছর ও অর্থদণ্ড। তবে অর্থদণ্ড কত তা ধারায় উল্লেখ নেই। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ (২৬ নম্বর আইনের) ৪১ ধারায় এ অপরাধে অনূর্ধ্ব তিন বছর কারাদণ্ড বা দুই লাখ টাকা জরিমানা বা উভয়দণ্ড। আইনের দুর্বলতার ফাঁকে অপরাধী কিভাবে পার পেয়ে যায় তার নজির এ দেশে অনেক। ভেজাল প্যারাসিটামল সিরাপ খেয়ে ৭৬ শিশুর মৃত্যু হলে ১৯৯৩ সালে পলিক্যাম ল্যাবরেটরিজ লিমিটেডের পরিচালকসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা হয় এবং ২০১৯ সালে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত পরিচালককে এক বছরের কারাদণ্ড প্রদান এবং ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। রায়ের পর আপিল করার শর্তে তাকে আবারো জামিন দেয়া হয়। অন্য তিন আসামি ল্যাবরেটরিজের ব্যবস্থাপক, ফার্মাসিস্ট এবং এক কর্মকর্তাকে আদালত খালাস দেন। তদারকি প্রতিষ্ঠান কেন এত দিন অভিযুক্ত ল্যাবরেটরিজ থেকে প্যারাসিটামল সিরাপের স্যাম্পল সংগ্রহ করে ল্যাবে পরীক্ষা করেননি, কেউ এই প্রশ্ন সিরিয়াসলি তোলেননি বা আদালতে কেউ উপস্থাপন করেননি। আমাদের দেশে আইনগুলো সংশোধনপূর্বক আরো কঠিন অথবা সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান রেখে নতুন আইন তৈরি করতে হবে। চীনে ওষুধ ও খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল ও নকলের অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের বিধান আছে। নতুন আইন তৈরি করা যেমন জরুরি, তার চেয়ে বেশি জরুরি আইনের সঠিক প্রয়োগ। কোটি কোটি মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবন নিয়ে ‘কানামাছি খেলা’ চলতে পারে না।
সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মনজিল মোরসেদ জানান, বাংলাদেশে নকল বা ভেজাল ওষুধের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলার বিধান আছে। আর এ আইনে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু এখনো এ আইনে নকল ও ভেজাল ওষুধের ব্যাপারে কেউ শাস্তি পেয়েছেন, এমন নজির নেই। এ আইনে মামলা হয় খুবই কম। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করে ছেড়ে দেয়া হয়। এ দিকে নকল ও ভেজাল ওষুধ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে নজরদারির দায়িত্বপ্রাপ্ত হলো, ওষুধ প্রশাসন অধিদফতর (নয়া দিগন্ত, ২২ আগস্ট, ২০২১)। প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে ওষুধ প্রশাসন জেলায় ও থানায় পর্যাপ্ত অভিযান পরিচালনা করতে সক্ষম হচ্ছে না। একটি জেলায় একজন সহকারী পরিচালক দায়িত্বে থাকেন। পুরো জেলা নজরদারি করা মাত্র একজন কর্মকর্তার পক্ষে সম্ভব হয় না। ভেজাল ও মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধের বিরুদ্ধে কোনো জেলায় যদি কোনো কর্মকর্তা পুলিশ, র্যাব ও ম্যাজিস্ট্রেট নিয়ে বারবার অভিযান পরিচালনা করেন তা হলে অসাধু ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট ওই কর্মকর্তাকে ‘ম্যানেজ’ করার জন্য তোড়জোড় চালায় বা বদলি করানোর জন্য উপর মহলে তদবির শুরু করে দেয়।
সাবেক ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ার আলম অভিযান চালিয়ে ২০১৫ থেকে ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত প্রায় ৮০ কোটি টাকার নকল ও ভেজাল ওষুধ জব্দ করেন। সর্বোচ্চ এক কোটি টাকা জরিমানা করা হয়। মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধে ল্যাবে লাগিয়ে মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়া হয়। আবার কিছু চক্র নিজেরাই নকল ওষুধ তৈরি করে। নিম্নমানের কোম্পানি ও নামসর্বস্ব কোম্পানিও নকল ও ভেজাল ওষুধ উৎপাদন করছে। বিশেষ ক্ষমতা আইনে বেশ কিছু মামলাও দেয়া হয়েছে। সেগুলো বিচারাধীন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক আ ব ম ফারুক বলেন, ‘সারা বছর নকল ও ভেজাল ওষুধ উৎপাদন করা হচ্ছে। এর ১০০ ভাগের মধ্যে এক ভাগও উদ্ধার হয় না। মনিটরিংয়ে যোগ্য মানুষ নেই। ওষুধ প্রশাসন অধিদফতর অযোগ্যতার পরিচয় দিয়ে আসছে। তাদেরও শাস্তির আওতায় আনতে হবে। তিনি বলেন, নকল ও ভেজাল ওষুধ উৎপাদন গণহত্যার শামিল’ (ইত্তেফাক, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১)।
স্মর্তব্য, বাংলাদেশে ওষুধ খাত একটি বিকাশমান শিল্প। একসময় চাহিদার প্রায় ৮০ শতাংশ ওষুধ আমদানি করা হতো বিদেশ থেকে। ওষুধ শিল্পে একচেটিয়া প্রভাব ছিল বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর। প্যারিসভিত্তিক বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানি সানোফি-অ্যাভেন্টিসের বাংলাদেশ শাখা ৫৪ দশমিক ৬ শতাংশ শেয়ার দেশীয় ওষুধ কোম্পানি বেক্সিমকো ফার্মা লিমিটেডকে বিক্রি করে দিয়েছে। ২০১৮ সালে যুক্তরাজ্যভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানি গ্যাক্সোস্মিথক্লাইন (জেএসকে) বাংলাদেশে তাদের ওষুধ কারখানাটি বন্ধ করে দিয়েছে। বর্তমানে ৯৮ ভাগ ওষুধ দেশেই উৎপাদিত হচ্ছে। জাতীয় অর্থনীতিতে ওষুধ শিল্পের ভূমিকা ও অবদান বেড়ে চলেছে। গুণগত মান ও কার্যকারিতার কারণে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশী ওষুধের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরীণ ৯৮ শতাংশ চাহিদা মিটিয়ে ১৬০টি দেশে রফতানি হচ্ছে বাংলাদেশের ওষুধ। বিশ্বের ৪৮ দেশের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে বাংলাদেশের ওষুধ। দেশীয় ৪৬ কোম্পানির ৩০০ ধরনের ওষুধপণ্য বিশ্ববাজারে রফতানি করা হয়। রফতানিতে শীর্ষ সাত দেশ হচ্ছে মিয়ানমার, শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, আফগানিস্তান, কেনিয়া ও ভেনিয়া। মোট ওষুধ রফতানির ৬০.৩২ শতাংশ এসব দেশে। স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস বর্তমানে যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়াসহ মোট ৩৯টি দেশে ওষুধ রফতানি করে আসছে। স্কয়ার পূর্ব আফ্রিকার ছয়টি দেশের সাড়ে ২৫ হাজার কোটি টাকার ওষুধের বাজার ধরতে কেনিয়ায় কারখানা তৈরি করেছে। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, তাইওয়ান ও ব্রাজিলসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ওষুধ নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন রয়েছে বেক্সিমকোর। বর্তমানে কুয়েতসহ ৫৪টি দেশে বেক্সিমকোর ওষুধ রফতানি হচ্ছে। এ ছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ওষুধের বাজার ধরার লক্ষ্য নিয়ে বেক্সিমকো মানসম্মত ওষুধ তৈরির জন্য মালয়েশিয়া, সৌদি আরব ও শ্রীলঙ্কায় যৌথ বিনিয়োগ প্রকল্পে শেয়ার কিনেছে ৩০ থেকে ৪২ শতাংশ। এরই মধ্যে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে গেছে। নেপালসহ পৃথিবীর যেসব দেশের শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি নিয়ে বেরোচ্ছেন, তারা বাংলাদেশী ওষুধের সাথে পরিচিত হওয়ায় নিজ দেশে এগুলোর ব্যবস্থাপত্র দিচ্ছেন। ফলে ওষুধের বাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে।
একশ্রেণীর অসাধু ব্যক্তির অপতৎপরতার কারণে সম্ভাবনাময় এ শিল্পকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। ভেজাল ও নকল ওষুধ এই সুনাম ও আস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। এসব খবর আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় প্রকাশ পাচ্ছে, যা আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। সুতরাং ভাঙতে হবে চক্র ও সিন্ডিকেট। এর উৎসমুখে হাত দিতে হবে। ফার্মেসিতে অভিযান পরিচালনা যথেষ্ট নয়। পাশাপাশি নকল ও ভেজাল ওষুধ উৎপাদনকারী ও বিপণনকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। মিটফোর্ড পাইকারি ব্যবসায়ীদের তথ্যানুযায়ী, প্রতি বছর চোরাচালানের মাধ্যমে এক হাজার কোটি টাকারও বেশি বিদেশী ওষুধ দেশে আসে। ওষুধ প্রশাসন অধিদফতর এ বিষয়ে মূল তদারকি প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিতে হবে তাদের। এই অধিদফতরের সক্ষমতা বৃদ্ধি, লোকবল নিয়োগ ও তদারকির উদ্যোগ ও মাত্রা বাড়াতে হবে। ওষুধ প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা, ওষুধ শিল্প সমিতি, কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট সমিতি ও সাংবাদিকদের সমন্বয়ে টাস্কফোর্স গঠন করে নকল ও ভেজাল ওষুধ প্রতিরোধ করা সম্ভব। তথ্য অভিজ্ঞদের মতে, ওষুধের চোরাচালান ও নকল ওষুধ রোধ করা গেলে বাড়বে দেশীয় ওষুধের অভ্যন্তরীণ বাজার চাহিদা এবং সম্প্রসারিত হবে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিধি।
১৯৪৬ সালে প্রণীত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংবিধান, ১৯৪৮ সালের সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান, অনুচ্ছেদ-১৫ এবং আদালতের বিচারিক পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও সুচিকিৎসা লাভ নাগরিকের অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। বৈশ্বিক মানদণ্ডে এই অধিকার বাস্তবায়নে বাংলাদেশ রয়েছে অনেক পিছিয়ে। ভেজাল ও মানহীন ওষুধ উৎপাদন ও বিপণন বন্ধ করা না গেলে স্বাস্থ্য সুরক্ষা, চিকিৎসাসেবা ও চিকিৎসা নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও উন্নত চিকিৎসাসেবার ওপর নির্ভর করে জীবনমানের উপযুক্ত অগ্রগতি এবং সাধন ও শারীরিক-মানসিক প্রশান্তি। আর এটি নিশ্চিত করার দায়িত্ব বর্তায় রাষ্ট্রের ওপর। বিগত ৫০ বছরে এ বিষয়ে একক ও পূর্ণাঙ্গ কোনো আইন তৈরি করা হয়নি, যদিও ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য ও আওতায় কিছু আইন প্রণীত বা সন্নিবেশিত হয়েছে। কিছু আইন অতি পুরনো এবং অপরাধের চেয়ে শাস্তির মাত্রা একেবারে লঘু। এ ঘাটতি পূরণে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ, স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ, জনস্বাস্থ্যবিদ, আইনস্কলার ও সুশীলসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। জীবন যারা মাত্রাতিরিক্ত ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে তাদের ছাড় দিলে সভ্যতা বিপন্ন হয়ে যাবে।