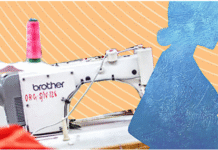- মোশাররফ আহমেদ ঠাকুর
- ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ০৭:০২

গায়েবি মামলা এক ধরনের মিথ্যা মামলা, যা দায়ের করা হয় নিছকই রাজনৈতিক কারণে। বেশির ভাগ মামলাই হয় একেবারেই বানোয়াট। এই মামলাগুলো করে পুলিশ কিংবা তার সোর্স। সাম্প্রতিককালে দেখা যায়, সরকারদলীয় নেতাকর্মীরাও এসব মামলার বাদি হন। এই মামলায় জড়ানো হয় শুধুই বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের। এতে বিপুল সংখ্যক লোককে আসামি করা হয়। যেকোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি অথবা নির্বাচনের আগে অথবা পরবর্তী সময়ে বেশির ভাগ গায়েবি বা রাজনৈতিক মামলার উদ্ভব হয়। সব মামলার এজাহারের বক্তব্য প্রায় একই, যেন কেন্দ্রীয়ভাবে কোনো ড্রাফট থানায় থানায় সরবরাহকৃত। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীদের এলাকাছাড়া করা ও ভীতসন্ত্রস্ত রাখা।
এই মামলাগুলোতে দুটো কারণে প্রচুর সংখ্যক অজ্ঞাত আসামি রাখা হয়। বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীরা যেন শঙ্কায় থাকে যে, তার নাম না থাকলেও এতে তাকে যুক্ত করা যাবে। আবার পুলিশ যদি কাউকে গ্রেফতার করে তার বিরুদ্ধে যদি কোনো মামলা নাও থাকে, অজ্ঞাত ব্যক্তি হিসেবে যেন কোনো একটি মামলায় ঢুকিয়ে দিতে পারে। প্রায় প্রত্যেকটি গায়েবি মামলায় ককটেল বিস্ফোরণের কথা বলা হয়। এক জরিপে দেখা গেছে, দায়ের করা ১৭টি মামলার মধ্যে ১৫টি মামলার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ঘটনাই ঘটেনি এবং এলাকাবাসী ককটেল বিস্ফোরণের শব্দ শোনেনি বা এমন কিছু দেখেওনি। কিন্তু প্রত্যেকটি মামলায় ককটেল বিস্ফোরণের বিষয় ঢোকানো হয়, কারণ বিস্ফোরক আইনের অধীনে মামলার বিচার দ্রুত নিষ্পত্তি করা যায় এবং সেটি জামিন অযোগ্য। এসব মামলার আসামিরা ভীত থাকেন। কারণ গ্র্রেফতার হলে সহজে জামিন মিলবে না, দ্রুত সাজা হয়ে যেতে পারে।
২০১৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান খন্দকার মাহবুব হোসেন, সাবেক মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী ও বিএনপির আইন-বিষয়ক সম্পাদক সানাউল্লাহ মিয়া হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট করেন। ২০১৮ সালে শুধু সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম ২০ দিনে ৩ হাজার ৭৩৬টি মামলা করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এতে আসামি করা হয় ৩ লাখ ১৩ হাজার ১৩০ জনকে। আসামিদের মধ্যে মৃত, বিদেশে থাকা ও গ্রেফতার হওয়া লোকও ছিল। বেঞ্চের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী রিটটি আমলে নিয়ে ৬০ দিনের মধ্যে পুলিশের আইজিপিকে প্রতিবেদন দিতে নির্দেশ দেন। শুনানির সময় আদালতে আইনজীবীরা বলেন, ১০ বছর আগে মারা গেছেন এমন মানুষকেও এসব মামলায় আসামি করা হয়েছে। কয়েকটি মামলার এজাহার পর্যবেক্ষণ করে হাইকোর্ট বলেন, ‘এ ধরনের মামলায় (গায়েবি) পুলিশের ভাবমর্যাদা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়।’ কিন্তু বেঞ্চের জুনিয়র বিচারপতি মো: আশরাফুল কামাল ভিন্নমত পোষণ করেন।
গায়েবি মামলা হলে চলাচল, সমাবেত হওয়া, সভা সমাবেশ, বাকস্বাধীনতা নষ্ট হয়, জীবন-জীবিকা হুমকির মুখে পড়ে এবং নির্বাচনের সমতল ভূমি বিপর্যস্ত হয়। গত ১৫ বছরের মামলার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সরকারের অবৈধ ক্ষমতার মেয়াদ প্রলম্বিত করার উদ্দেশ্যে এসব মিথ্যা মামলার উৎপত্তি হলেও সুস্পষ্টভাবে সংবিধানের ৩৬ অনুচ্ছেদে চলাফেরার স্বাধীনতা, ৩৭ অনুচ্ছেদে সমাবেশের স্বাধীনতা, ৩৮ অনুচ্ছেদে সংগঠনের স্বাধীনতা ও ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তা এবং বিবেক-বাকস্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী এ ধরনের মিথ্যা মামলা চলতে পারে না।
মামলার পর যে বিষয়টি আসে তা হলো গ্রেফতার ও রিমান্ড। এখন মানুষের কাছে গ্রেফতার ও রিমান্ড একটি ভীতিকর বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বেআইনি ও বেপরোয়া গ্রেফতার এবং রিমান্ড বিতর্কিত অবস্থায় পৌঁছলে অতীতে হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট সময়ে সময়ে বহু নির্দেশনা দেন। বিষয়টি রিট পিটিশন নং-৩৮০৬/১৯৯৮ মূলে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) হাইকোর্টের নজরে আনে। বিষয়টি নিয়ে বিচারপতি মো: হামিদুল হক ও বিচারপতি সালমা মাসুদ চৌধুরী ২০০৩ সালের ৭ এপ্রিল জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার সনদ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, আমেরিকা ও ভারতীয় প্রাসঙ্গিক আইনের নিরিখে বাংলাদেশের সংবিধান ও প্রচলিত বিধানের সামগ্রিক পর্যালোচনায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং ফৌজদারি আদালতের প্রতি দিক-নির্দেশনামূলক রায় দেন।
অতঃপর রিটের রেসপন্ডেন্ট পক্ষেও দায়েরকৃত সিভিল আপিল নং ৫৩/২০০৪ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে ২০১৬ সালের ২২ মার্চ শুনানি শুরু হয়। তৎকালীন প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে আপিল বিভাগের অন্যান্য বিচারপতি সমন্বিতভাবে ২০১৬ সালের ২৪ মে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জন্য ১০ দফা ও অপরাধ আমলে নেয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিচারকদের জন্য পালনীয় ৯ দফা নির্দেশনা জারি করেন। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো, ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিচারকরা এসব নির্দেশনার কিছুই মানেন না।
প্রমাণস্বরূপ ম্যাজিস্ট্রেট ও বিচারকদের জন্য নির্দেশনার কিছু অংশ উল্লেখ করা হলো :
ক. আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যদি ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৬৭ (২) অনুযায়ী মামলার কেস ডায়েরিতে সবিস্তার কিছু উল্লেখ না করেই রিমান্ডের জন্য আবেদনসহ কোনো গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে আদালতে উপস্থাপন করে, তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট অথবা আদালত সেই ব্যক্তিকে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা-১৬৯ অনুযায়ী মুচলেকা গ্রহণ করে মুক্তি দিয়ে দেবেন; খ. কোনো আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা যদি গ্রেফতার হওয়া কোনো ব্যক্তিকে বিশেষ কোনো মামলায় গ্রেফতার দেখানোর চেষ্টা করেন, যিনি ইতোমধ্যেই হেফাজতে রয়েছেন, তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট বা বিচারক বা ট্রাইব্যুনাল এ ধরনের কোনো প্রার্থনার অনুমতি দেবেন না, যদি অভিযুক্ত বা গ্র্রেফতারকৃতকে তার সামনে হাজির না করা হয়। অতঃপর এ ধরনের মামলার সাথে সম্পর্কিত কেস ডায়েরিতে এবং গ্রেফতার দেখানোর জন্য প্রার্থনা যদি সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং ভিত্তিযুক্ত না হয়, তাহলে তিনি গ্রেফতার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করবেন; গ. ম্যাজিস্ট্রেট কোনো ব্যক্তিকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে আটক রাখার আদেশ দেবেন না, যদি পুলিশ ফরওয়ার্ডিং লেটারে এমন কিছু প্রকাশ পায় যা থেকে মনে হয়, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে প্রতিরোধমূলক আটক রাখার উদ্দেশ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে।
রিমান্ড মঞ্জুর করার মাধ্যমে বস্তুত একজন বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট বা ট্্রাইব্যুনাল পুলিশের কাছে মানুষের জান ও মাল তুলে দেন। এখন সবাই জানে, এ ধরনের বিচারবিভাগীয় অনুমোদনের মাধ্যমে পুলিশ নির্যাতন ও টাকা আদায়ের লাইসেন্স পেয়ে থাকে। প্রাথমিক দৃষ্টিতে যে ক্ষেত্রে একটি মামলার কোনো গ্রহণযোগ্যতা থাকে না, ম্যাজিস্ট্রেট ইচ্ছা করলে সে ক্ষেত্রে একজন আসামির নাম এজাহার থেকে কর্তন করার জন্য আদেশ দিতে পারেন। সেই ক্ষমতা ম্যাজিস্ট্রেটকে কখনো প্রয়োগ করতে দেখা যায় না। পুলিশ হেফাজতে কোনো মৃত্যু হলে তখন পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট ও অসৎ ডাক্তারের একটি চক্র তৈরি হয়। এটিকে বিভিন্নভাবে আত্মহত্যা হিসেবে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৯৮ সালে মতিঝিল থানায় যুবদলকর্মী তুহিন পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুবরণ করলে, তা জুতার ফিতা পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়।
বাংলাদেশের বিচার বিভাগ বিশেষ করে নিম্ন আদালত একেবারেই সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে। উচ্চ আদালতের অবস্থাও একইরকম। তাই বলা যায়, গায়েবি মামলার অস্তিত্ব, পুলিশ রিমান্ড সবই চলছে বিচার বিভাগের কাঁধের ওপর ভর করে। বিচার বিভাগের এক শ্রেণীর দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও বিচারকের মাধ্যমে নানাভাবে মানুষ হয়রানির শিকার হচ্ছেন। বস্তুত বাংলাদেশে বিচারিক হয়রানি বা বিচারিক নৈরাজ্য চলছে। এ বিষয়ে সম্প্রতি শতাধিক নোবেলবিজয়ী ও বিশ^নেতার বিবৃতি বিশ^জুড়ে ছড়িয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোও একই অভিযোগ করেছে। এ প্রসঙ্গে জাতীয় পর্যায়ে বাপকভিত্তিক আলোচনা হওয়া জরুরি।
দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশের নাম আলোচিত হলেও ম্যাজিস্ট্রেট ও সরকারের ইশারায় চলা বিচারকদের নাম আলোচনায় আসে না। যারা সরকারের উদ্দেশ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে অতি দ্রুত মামলার রায় দেয়ার জন্য রাত পর্যন্ত কোর্ট পরিচালনা করেন এবং যেসব ম্যাজিস্ট্রেট অন্যায়ভাবে রিমান্ড মঞ্জুর করেন, তাদের নাম ও আদালত নম্বর প্রকাশ হওয়া উচিত। এ কাজটি অবশ্য সম্মান প্রদর্শনের সাথেও করা যায়। যেমন, এত নম্বর আদালতের অমুক ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। এটি উল্লেখ করে সাংবাদিকদের ব্রিফ করতে হবে। তাহলে বিচার বিভাগের কারা সরকারের অন্যায়-বেআইনি উদ্দেশ্য হাসিলে সহযোগিতা করছেন, তাদের চেহারাও জনগণের কাছে উন্মোচিত হবে।
বিচারিক হয়রানির রাশ টেনে ধরতে না পারলে ভবিষ্যতে গায়েবি মামলার সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বাড়বে। রিমান্ডের মাধ্যমে পুলিশি নির্যাতন বাড়বে, দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশের টাকা আদায়ের পথ আরো বেশি করে উন্মুক্ত হবে। সারা দেশে অন্যায় ও বেআইনিভাবে জনপ্রতিনিধি হওয়ার মতো নেতাকর্মীকে সাজা দিয়ে, নির্বাচনের অযোগ্য ঘোষণা করা হবে, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ আরো বেশি বিপন্ন হয়ে পড়বে। তাই নিশি ভোটের সরকারবিরোধী আন্দোলন আমাদের যেমনি করতে হবে, তেমনি গায়েবি মামলা, পুলিশি রিমান্ড ও বিচারিক হয়রানির মাধ্যমে সরকার গণতন্ত্রকে নির্বাসনে পাঠানোর যে প্রক্রিয়া চলছে তা রুখে দাঁড়াতে হবে।
প্রণিধানযোগ্য, আবদুল মান্নান খান বনাম বাংলাদেশ [৬৪ ডিএলআর (এডি) ১৬৯] মামলায় সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায়ে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি অভিমত দেন যে, ‘কোনো আইন প্রণয়নে যতই কারণ থাকুক না কেন, কোনো কারণে বা কোনো অজুহাতে, তাহা যত গুরুত্বপূর্ণই হউক না কেন, কখনই জনগণের সার্বভৌমত্ব কাড়িয়া নেয়া যায় না। জনগণের সার্বভৌমত্ব সব কারণ, প্রয়োজন এবং ওজরের উপরে অবস্থিত। জনগণের কারণে ও প্রয়োজনে সংবিধানও সংশোধন করা যায়।’ গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের এরূপ ঐতিহাসিক ভূমিকা জনগণ প্রত্যাশা করে।
লেখক : বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক