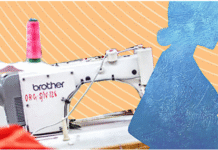দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস বিষয়ের গবেষক

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বড় সংকট—সেখানে কথা বলা যাচ্ছে না। ‘রাজনীতি’ সেখানে নিষিদ্ধ। অথচ দুনিয়ায় কেউ রাজনীতির বাইরে নেই। বুয়েটকে বাংলাদেশের অগ্রসর বিদ্যাপীঠ গণ্য করার রেওয়াজ আছে। বুয়েট কিছুকাল আগে সিদ্ধান্ত নেয় শিক্ষার্থীদের সংগঠনচর্চা থাকবে না। এর ঢেউ তোলা হয় অন্যত্রও। অন্যান্য শিক্ষাঙ্গনেও ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীদের সমাজ-ভাবনা বন্ধের আয়োজন বেগবান হয়। তাতে একের পর এক সব ক্যাম্পাসে রক্তপাতই কেবল ঘটছে।
ক্যাম্পাস গণতন্ত্রের চর্চা নিষিদ্ধ করতে অজুহাত হিসেবে হাজির করা হয় ‘মারামারি’ ও ‘সন্ত্রাস’-কে। গুটিকয় সন্ত্রাসী কাজকে ‘ছাত্ররাজনীতি’র পোশাক পরিয়ে জবাই দেওয়া হয় মানবিক ভাবনা-চিন্তাচর্চার স্বাভাবিকতাকে। আরও স্পষ্ট করে বললে তরুণ-তরুণীদের প্রশ্ন তোলা ও উত্তর খোঁজার চেষ্টাকে টার্গেট করা হচ্ছে। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) তার নিষ্ঠুর এক পরিণতি দেখলাম আমরা।
আবরার ফাহাদ হত্যার আগে-পরে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রশ্ন ও প্রতিবাদের একটা নতুন তরঙ্গ দেখা যাচ্ছিল।
বিপুল সামাজিক সংহতিও পায় সেটা। ওই সামাজিক সমর্থন দ্রুত অস্ত্র হিসেবে নিপীড়নবিরোধীদের স্তব্ধ করার কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়। তরুণ-তরুণীদের খাঁচায় পোরার জন্য আবরার হত্যাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। শিক্ষাঙ্গন বাঁচাতে ‘ক্যাম্পাস ডেমোক্রেসি’ নিষিদ্ধ রাখতে হবে—এ রকম ফর্মুলা জনসমাজে বেশ সম্মতি পেয়ে যায় তখন। কিন্তু তারপর শাবিপ্রবিতে কী দেখা গেল? এবার হয়তো আবরারের মতো কেউ মরল না, কিন্তু শিক্ষার্থীদের রক্তে ক্যাম্পাসের মাটি সিক্ত হলো। যে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে অব্যবস্থাপনার বিষয়ে বলছিল কেবল।
জ্ঞান-অর্থনীতির প্রকৃত প্রতিপক্ষ কারা
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে বড় আকারের খাঁচায় পোরার কাঠামোগত ‘কাজ’-টি রাজনৈতিক-অর্থনীতির জন্য খুব জরুরি। ক্যাম্পাসে গণতন্ত্রচর্চা বন্ধের আয়োজন একালে তাই অনেক রাষ্ট্রে অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্প। তরুণদের কথা বলা বন্ধের কাজটি প্রয়োজন মূলত ক্ষমতাবানের। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছোট ছোট অনেক কর্তৃত্বশালী তাঁদের ঊর্ধ্বতনদের মতো জবাবদিহির বাইরে থাকতে চান।
কিন্তু তরুণেরা ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের জায়গাগুলোর অন্যায্যতা ও অযৌক্তিকতা চিনে ফেলছে। দুর্নীতিকে শনাক্ত করছে। সেগুলো চ্যালেঞ্জ করছে, কথা বলছে, গান করছে, কবিতা লিখছে, গ্রাফিথি আঁকছে, প্রশ্ন তুলছে, উত্তর খুঁজছে এবং গণতন্ত্র চাইছে—যে গণতন্ত্র সবাইকে মতামত প্রকাশের সুযোগ দেয়। কিন্তু অনেকের জন্য এ পরিস্থিতি মানিয়ে নেওয়া কষ্টকর। তাঁরা ক্যাম্পাস ডেমোক্রেসিতে বাইরের ‘ইন্ধন’ দেখেন। তাঁদের মানসম্মান থাকে না তাতে।
পাকিস্তান আমলে এ দেশে এ রকম তরুণদের ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী’ গালি দেওয়া হতো। পাশের দেশ ভারতে একই ধরনের প্রতিবাদী শিক্ষার্থীদের ‘অ্যান্টি-ন্যাশনাল’ মোহর দেওয়া হয়। এ রকম মনস্তত্ত্বের মাঝেই আমরা আছি এখন।অথচ যেকোনো জ্ঞানপীঠে মেধা ও যোগ্যতার বদলে রাজনৈতিক আনুগত্যকে যদি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের মানদণ্ড করা হয়, তখন সেটাই ওই প্রতিষ্ঠানের পরিবেশের জন্য বড় সন্ত্রাস হয়ে ওঠে। এই সন্ত্রাস নির্বিঘ্নেই কি চলছে না? সেই অভিজ্ঞতাগুলো আড়াল করেই কয়েক দশক ধরে ক্যাম্পাসগুলোর সব সহিংসতার দায়ভার চাপানো হচ্ছে ছাত্রসংগঠনগুলোর ওপর এবং ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও ঐতিহ্যের ওপর।
কিন্তু ছাত্র সংসদ বা ইউনিয়ন বন্ধ হওয়ায় মোটেই সন্ত্রাস কমেনি। প্রত্যেক কালেই ক্ষমতাবানেরা সন্ত্রাস করে, এখনো ক্ষমতাবানদের দ্বারাই ছাত্রছাত্রীরা রক্তাক্ত হয়। ইউনিয়ন না থাকলে ক্ষমতাবানদের বাড়তি সুবিধা এটুকু—শিক্ষার্থীদের অনায়াসে পেটানো যায়। পিটিয়ে সাংবাদিক ডেকে বাইরের ইন্ধনের দিকে আঙুল দেখানো যায়। ক্যাম্পাসে গণতন্ত্রচর্চা করতে দেওয়া হবে না বলে বহুকাল দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীদের ইউনিয়নের নিয়মিত নির্বাচন বন্ধ।
ঔপনিবেশিক আমলেও যা হয়নি, স্বাধীনতার আমলে তা-ই সম্ভব হয়—ক্যাম্পাস, সমাজ ও দেশ নিয়ে শিক্ষার্থীদের ভাবনাচিন্তাকে ‘অপরাধ’ ও ‘সন্ত্রাস’ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়। শিক্ষার্থীদের মতামত গঠনের প্রক্রিয়া বন্ধ করা গেছে এতে। সমাজের নিচ থেকে নেতৃত্ব তৈরির পথ রুদ্ধ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিশাল বিশাল তহবিলের ওপর প্রশ্নহীন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে গুটিকয়েকের। জ্ঞান-অর্থনীতির প্রকৃত প্রতিপক্ষরা বেশ আড়ালে থাকতে পারছে এতে।
আজকে নির্মীয়মাণ পদ্মা সেতুর পিলারে একটা বার্জ ধাক্কা খেলে পুরো দেশ আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। কিন্তু দেশের সম্পদ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনাচার নিয়ে তরুণদের আকুতিতে প্রতিক্রিয়া অতি সামান্য। অথচ এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটে দেশের প্রতিটি পরিবারের হিস্যা আছে।
শিক্ষার্থীদের ইউনিয়ন না থাকায় লাভ কার
সামান্য ১-২টি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় ৩০ বছর দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচিত ইউনিয়ন নেই। কিন্তু গুন্ডা বাহিনীগুলো বাধাহীনভাবে কাজ করছে সব জায়গায়। এমন তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায় না—ইউনিয়ন থাকার সময়ের চেয়ে না থাকার সময়ে শিক্ষার পরিবেশ ও মান বেড়েছে, সন্ত্রাস কমেছে কিংবা শিক্ষার্থীদের সন্তুষ্টি বেড়েছে। এই ৩০ বছরে শিক্ষকেরা ঠিক ঠিক জাতীয় রাজনীতি করে গেছে। অফিসার-কর্মচারীরাও করেছে। বহু শিক্ষক বড় ‘নেতা’ হয়েছেন। সেই ‘নেতা’দের সহায়তায় বহু ‘ছাত্র’ কোটিপতি হয়েছে।
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ-বদলি-পদায়ন যে রাজনৈতিক বিবেচনায় হচ্ছে সেটা সবাই জানে। সবাই অভ্যস্ত এতে। এসব অনায়াসে চলতে পারছে। চলতে পারবে। কেবল চলতে পারছে না এসবের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ। কোনো কিছুতে আপত্তি তোলা, প্রশ্ন উত্থাপন, উত্তর অন্বেষণ বিপজ্জনক। সেসব তাই নিষিদ্ধ। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশ্নের জায়গা নয়, একে গড়ে তোলা হচ্ছে আনুগত্যের জায়গা হিসেবে!
কিন্তু প্রতিনিধি বাছাই, সংগঠিত হওয়ার অধিকার কিংবা ইউনিয়ন না থাকার পরও তরুণ-তরুণীদের সচেতনতাবোধ কমছে না।
এত নষ্ট একটা সমাজে সেটা সম্ভব নয়। যে ছোট একটা গোষ্ঠী সমাজের প্রায় সবকিছু দখল করে রাখে, শিক্ষাঙ্গনের ক্ষুদ্র চত্বরগুলো তাদের কাছে নতজানু হয় না দেখে স্বাভাবিকভাবেই ক্রোধ হতে পারে তাদের। এটা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাও বটে। সে জন্য তাঁরা ক্যাম্পাসে সশস্ত্র রক্ষীদের ডাকেন। কেবল এ কারণেই ক্যাম্পাস রক্তাক্ত হয়। তবে এটাকে কখনো ‘সন্ত্রাস’ বলা হয় না।
শিক্ষার্থীদের একাংশের প্রতিবাদ (পড়ুন ‘অবাধ্যতা’) চলতি রাজনৈতিক-অর্থনীতির জন্য, একচেটিয়া কারবারিদের জন্য, ভূমিদস্যু, পরিবহন মাফিয়া, নদীখেকো, ক্যাসিনো মালিক, কিছু কিছু মিডিয়া ব্যবসায়ীর জন্যও অসহনীয়। তাই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীদের খাঁচায় পোরার প্রয়াসে সবার সমর্থন থাকে। খাঁচায় পোরার কাজটি হয় কোথাও ‘সান্ধ্য আইন’-এর নামে। কোথায় ফি বাড়ানোর নামে। কোথাও ফেসবুকে লেখার কারণে। কোথাও বিশেষ বিশেষ পোশাক পরা কিংবা না পরার কারণে। হরেক অছিলায় তরুণ-তরুণীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ-নিপীড়ন-নির্যাতনের খড়্গ নেমে আসছে। কিছুদিন আগে এক বিশ্ববিদ্যালয়ে ধূমপানের কারণেও শিক্ষার্থীর ‘সিট বাতিল’-এর ঘটনা ঘটেছে।
শিক্ষার্থীদের মুখ বন্ধ করা আসলে ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকদের কথা বলা বন্ধ করা, পরিবার ও সমাজে নারীর কথা বলা নিষিদ্ধ করা, ব্রাহ্মণের সামনে দলিতের কথা বলা কমানো, প্রশাসনের সামনে করদাতার কথা বলার সুযোগ না রাখা, ১ শতাংশের সামনে ৯৯ শতাংশের কথা বলা নিষিদ্ধের থেকে আলাদা কিছু নয়। শিক্ষার্থীদের মতপ্রকাশ নিষিদ্ধ করা কার্যত অন্যান্য সামাজিক বিভাজনকেই উদোম করে মাত্র।
শিক্ষার্থী, শ্রমিক, নারী, মজলুমসহ সবাইকে কথা বলতে দিয়ে একালে আর ক্ষমতার ভরকেন্দ্রগুলো নিজের ন্যায্যতা টিকাতে পারে না। ‘ছাত্র’রা তাই উপলক্ষ, দীর্ঘ মেয়াদে লক্ষ্য কিন্তু ‘সবাই’। যদিও সবাই সেটা চট করে বোঝে না। একদল বোঝে না রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বার্থের কারণে; অন্যরা মনোজগতে উপনিবেশের কারণে।
‘রাজনীতিমুক্ত’ শিক্ষাঙ্গনগুলোর মান বেড়েছে কি?
পুরো সমাজ থেকে, বিশ্ব থেকেও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। আবার সেগুলো, নিজে এক-একটা খুদে ‘রাষ্ট্র’ও বটে। ক্যাম্পাসে গণতন্ত্র নিষিদ্ধের সঙ্গে দেশ গঠনমূলক রাজনীতি নিষিদ্ধের ফারাক ও দূরত্ব তাই সামান্য। এটা মানবসত্তার বিরুদ্ধে সরাসরি আঘাত মাত্র। সেই আঘাত নয়াদিল্লিতে যেমন, তেহরানে যেমন, পেশোয়ার এবং সিলেটেও তেমন।
যে সমাজে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান রাজনীতির খবরদারিতে রয়েছে—যেখানে ব্যক্তির জীবনের সবকিছু, এমনকি তার খাবার, পোশাক, সংস্কৃতিতে লেপটে থাকে রাজনীতি—যেখানে পাঠ্যবইয়ের গল্প-কবিতা নিয়েও গভীর রাজনীতি চলে, বিবাদ হয়; সেখানে কেবল বেছে বেছে তরুণদের ‘রাজনীতিমুক্ত’ জীবন যাপন করতে হবে কেন? কারণ, তার প্রতিবন্ধিতার বিপরীতেই কেবল গুটিকয়েকের কণ্ঠ উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠতে পারে।
এটা এক বোবাযুদ্ধ। বুয়েট থেকে শাহজালাল পর্যন্ত এই যুদ্ধের পরিসর আসলেই অনেক বড়। খেয়াল করলে আমরা দেখব বুয়েটে আবরার মারা যাওয়ার পর সারা দেশ উত্তাল হয়ে উঠেছিল,Ñকিন্তু আজ শাহজালালে শিক্ষার্থীরা মার খাওয়ার সময় বুয়েট পড়াশোনাতেই মন ডুবিয়ে আছে। বুয়েট পরিবার ‘রাজনীতি’ করতে যাচ্ছে না আর। বেখাপ্পা লাগলেও এটা আমাদের দেখাচ্ছে ক্যাম্পাসে বিবেক বন্ধের চেষ্টা পদ্ধতিগতভাবে বেশ কাজে লাগছে। ‘সিস্টেম’-এর জন্য ‘শান্তি’ খুব দরকার!
তবে ক্যাম্পাসে বিবেকে তালা লাগানোর সময় ‘সিস্টেম’ নয় ‘মান’-এর কথাই শোনা যায়। কিন্তু ‘উন্নত শিক্ষা’র সঙ্গে তথাকথিত ‘রাজনীতিমুক্ত শিক্ষাঙ্গন’-এর কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। ডাকসু-রাকসু-ইকসু না থাকায় ওই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশ্বিক সূচক এগিয়েছে কিংবা সেসব জায়গায় শিক্ষার্থীদের পেটানো, টেন্ডারবাজি কিংবা হল দখল কমেছে, এমন দেখা যায়নি। অথচ প্রবল রাজনৈতিক কলরব ধারণ করে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ) কিংবা যাদবপুরের মতো বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে বৈশ্বিক মানদণ্ডে বহু ধাপ এগিয়ে।
দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে ‘ছাত্ররাজনীতি’ বন্ধ বা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। গবেষণায়, জ্ঞানচর্চা, আবিষ্কারে সেসব প্রতিষ্ঠান এগিয়েছে এমন শোনা যায় না। হ্যাঁ, কোথাও কোথাও ‘কবরের শান্তি’ বিরাজ করছে। চরম বিপন্নতার মাঝেও সেখানে শিক্ষার্থীরা কথা বলতে পারে না। এ রকম ‘কবরের শান্তি’ এবং ‘শিক্ষার উন্নত পরিবেশ’ নিশ্চিতভাবেই আলাদা কিছু। যেমন আলাদা কিছু কারা প্রাচীরের দুই দিকের পরিসর।
বাস্তবে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে জ্ঞানচর্চার ভয়হীন পরিবেশের জন্য দরকার গণতন্ত্র তাড়ানো নয়, বরং বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সত্যিকারের স্বশাসন। আবার ‘স্বশাসন’ ও ‘গুটিকয়েকের শাসন’ মোটেই এক নয়। স্বায়ত্তশাসনের নামে কোনো ‘কর্তৃপক্ষ’ শিক্ষার্থীদের বলা ও চিন্তার স্বাধীনতাকে ছিনতাই করতে পারে না। বাংলাদেশ সংবিধান সেটা সমর্থন করে না। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সংবিধানের পরিসরের বাইরে রাখতে চাইছেন অনেকে।
গণতান্ত্রিক আবহ না থাকা এবং ইউনিয়ন না থাকার কারণে শিক্ষার্থীরা বসবাস ও অধ্যয়ন-অনুশীলনের জন্য ন্যূনতম জরুরি সুবিধাগুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের থাকার জায়গার সংকট, স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের সুবিধা নেই, বিশুদ্ধ পানি পাওয়া যায় না, বিনোদনের কিছু নেই, ভালো পরিবহন নেই, লাইব্রেরি নেই, গবেষণা তহবিল নেই, গুণগতভাবে উন্নত শিক্ষা নেই, কবে পরীক্ষা হবে আর কবে ফল পাওয়া যাবে—সেসব নিয়েও অনিশ্চয়তায় থাকতে হয়।
শিক্ষকেরা অন্যায় করলে কথা বলা যায় না। কর্মচারীদের অবহেলায় চুপ থাকতে হয়। অথচ জনগণের করের টাকাতেই এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে সুউচ্চ ভবন উঠছে। শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন বাড়ছে। তাঁদের আবাসন সুবিধা বাড়ছে। তাঁদের ভর্তিকালীন আয় বাড়ছে। সরকার তাঁদের প্লট দিচ্ছে, পদক দিচ্ছে। শিক্ষার্থীদের দেখিয়েই শিক্ষা খাতের যাবতীয় ব্যয় বৃদ্ধি।
কিন্তু শিক্ষার্থীরা অসন্তুষ্ট। তারা অসুখী। তারা বঞ্চিত। সন্ধ্যা হলে হলগুলোতে ক্যাডারদের সামনে হাজিরা দিতে হয়। দিনে মিছিলে খাটতে যেতে হয়। অনেক স্থানে যৌন হয়রানি ও নিরাপত্তাহীনতার শিকার তারা। এত সব অসন্তোষ ও অসুখী জীবনের কথা, নিরাপত্তাহীনতা ও বঞ্চনার কথা প্রকাশের নিয়মতান্ত্রিক সুযোগ রাখা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে এটা ‘রাজনীতি’। এটা নিষিদ্ধ।
দেশজুড়ে সব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমবেশি একই রকম দৃশ্য এখন। এর ফল এত ভয়াবহ যে মাঝেমধ্যে শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যা করতে দেখা যাচ্ছে। এসব মৃত্যুর কারণ কেউ খোঁজে না। এই মেধাবীদের নিশ্চয়ই কিছু বলার ছিল। তাদের সতীর্থরা কার কাছে এই মৃত্যুর জবাবদিহি চাইবে? এ রকম জবাবদিহি চাওয়াও যে ‘রাজনীতি’! ইউনিয়ন ও গণতন্ত্রহীন পরিবেশে শিক্ষার্থীরা কীভাবে আছে, আত্মহত্যার ঘটনাবলি তার বড় এক মানদণ্ড। অনুসন্ধান হলে হয়তো দেখা যেত, এসব আত্মহত্যা একধরনের পদ্ধতিগত হত্যা মাত্র।
যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জনগণের অর্থে চলছে, যেহেতু মেধাবী মানবসম্পদ দেশের ভবিষ্যতের জন্য বড় ভরসার ধন—সে কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে জনগণের সন্তানেরা কীভাবে থাকবে, কেন রক্ষীদের হাতে তারা রক্তাক্ত হচ্ছে, কেন আত্মহত্যা করছে—এই বিষয়গুলো নিয়ে বৃহত্তর পরিসরে আলাপ-আলোচনা-পর্যালোচনা দরকার।
বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল ভয়মুক্ত পরিবেশে একটা নতুন প্রজন্মের আত্মপ্রকাশের জন্য। শিক্ষার্থীরা যদি দেশের ভবিষ্যৎ হয়, তাহলে তাদের অনিরাপদ পরিবেশ থেকে বাঁচাতে হবে। তাদের কথা বলতে দিতে হবে।
আলতাফ পারভেজ লেখক ও গবেষক