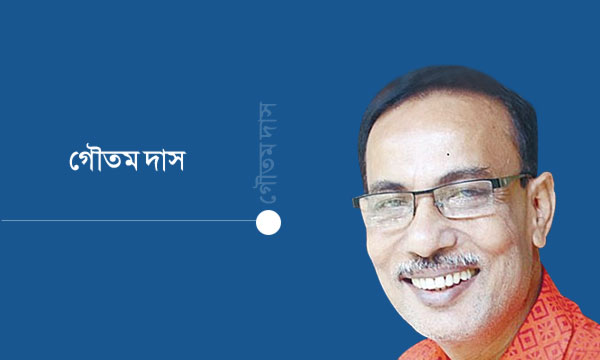- গৌতম দাস
- ০৩ অক্টোবর ২০২০
প্রতি বছর ২৫ সেপ্টেম্বরের আশপাশের সময় সাধারণত দেখা যায় সরকার প্রধানেরা নিউইয়র্কমুখী হচ্ছেন। তখন তারা জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের সভায় যোগ দেন। সাধারণ পরিষদের সভা মানে, বছরে যার এই একটাই সব সদস্যের অংশগ্রহণের জন্য উন্মুক্ত থাকে এমন অনুষ্ঠান। জাতিসঙ্ঘের সদস্য রাষ্ট্র এখন প্রায় ১৯৩ টি। এখানে সবার হাজিরা বাধ্যতামূলক না হলেও জাতিসঙ্ঘের এই জমায়েতেকে ‘বিশ্বসভা’ মানে যেখানে সব জনগোষ্ঠীর হাজির থাকার এক প্রতিনিধিত্বমূলক বিশ্বফোরাম বা বিশ্বদরবার ধরনের ধারণা, কোথাও ঘোষণা করা না থাকলেও, ক্রিয়াশীল থাকে বলে মনে করা যায়, এখানেই এর গুরুত্ব। এ বছরও সেপ্টেম্বরে এর ব্যতিক্রম হয়নি। যদিও ফারাক এতটুকুই ছিল যে এবার কোনো সরকারপ্রধানই কোভিডের কারণে নিজ সশরীরে হাজির হননি, আগাম রেকর্ড করা বক্তব্য পাঠিয়েছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদিও বক্তব্য পাঠিয়েছিলেন।
সাধারণত কোনো পাবলিক প্রতিষ্ঠান আর সাম্য ধারণাটা প্রায় হাত ধরাধরি করে চলে। এজন্য সংগঠন বা সাংগঠনিক প্রতিষ্ঠান মানেই তা মাস (ইংরেজি মাস বা বাংলায় গণ) অর্গানেইজেশন বলে ধরে নেয়া হয়। আর গণসংগঠন মানেই সেখানে সদস্যরা সবাই সমান; এমন সাম্যতার আবহাওয়া সেখানে বজায় থাকে বলে সবাই মেনে নিয়ে থাকে। গণপ্রতিষ্ঠান মানেই সবাই সেখানে সমান- এটা আধুনিক কালের ধারণা। কিন্তু এটার আসল মানে কী?
তা হলো, যখন রাজা বা সম্রাটের শাসনের দিন সমাপ্ত হয়ে পাবলিক বা জনগণের শাসন বলে ধারণার উদ্ভব ঘটেছে। কোনো ব্যক্তি বা রাজা নয়, সব রাষ্ট্রক্ষমতার উৎস পাবলিক, এ কথা যেখানে সবকিছুর শুরু। পাবলিকের রাষ্ট্র হলো সমাজের সবচেয়ে বড় বা প্রধান গণপ্রতিষ্ঠান। তাই ব্যক্তি বা রাজার খামখেয়ালি না, পাবলিক আর পাবলিকের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিত্ব দিয়ে এখানে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। অন্তত হওয়ার কথা।
এই সূত্রে যেখানে পাবলিকের রাষ্ট্র বা রিপাবলিক কথাটা এসে গেছে সেখানে রাষ্ট্রসহ যেকোনো গণপ্রতিষ্ঠান মানেই ধর্ম নির্বিশেষে নাগরিক সবাই সমান, এমন বৈষম্যহীনতার এক সাম্য ধারণা ও নীতি বজায় থাকতে হবে। এই বিচারে তাহলে ১৯৪৫ সালে জন্মের কালে জাতিসঙ্ঘ সব সদস্য রাষ্ট্রই সমান এমন ধারণার ভিত্তিতেই একটা প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিল। কিন্তু ব্যতিক্রম আছে। যেমন- সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় সবার সমান আর সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে। কিন্তু জাতিসঙ্ঘেরই আরেকটা ফোরাম আছে নিরাপত্তা পরিষদ সাম্যনীতির ফোরাম নয়। তাহলে কী এটা পাবলিক প্রতিষ্ঠানের নীতি ভঙ্গ করে গড়া হয়েছে? জবাব হবে, না। ঠিক তা নয়; আর সেটা জরুরিও নয়। তাহলে? ব্যাপারটা কী, কিভাবে এটা ব্যাখ্যা করব?
আমরা অনেক ফতোয়া পাবো এ বিষয়ে, এমনকি অনেক একাডেমিক প্রতিষ্ঠানেও; যেখানে হয়তো স্টুডেন্টরা শিখছে- জাতিসঙ্ঘ অগণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। প্রথমত ‘গণতন্ত্র’ খুব ভালো শব্দ নয়, বরং চাতুরীর শব্দ।
পাবলিকের ক্ষমতার রাষ্ট্র বা রিপাবলিক ধারণার বিকল্প বা সমতুল্য ধারণা ‘গণতন্ত্র’ নয়। যেমন এতে অনেকে ‘দেশে নির্বাচন হয় অতএব গণতন্ত্র আছে’ টাইপের কথা বলে রিপাবলিক ধারণাকে তাৎপর্যহীন করে ফেলতে পারে। তাই এখানে দুটি পয়েন্টে কথা বলব।
প্রথমত, ব্যাপারটা ব্যক্তির নয়, রাষ্ট্রবিষয়ক; আর আমরা ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে একাকার করে দেখছি। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই এক করে দেখলেও কোনো ভুল হয় না, এ কথাও সত্যি। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে মারাত্মক ভুল হয় ও হবেই। লক্ষ্যণীয়, আমরা নিরাপত্তা পরিষদ নিয়ে কথা বলছি মানে এটা রাষ্ট্রের ভিতরের বা অভ্যন্তরীণ দিক নিয়ে কথা বলছি না, বলছি রাষ্ট্রের বাইরে বা ঊর্ধ্বের বিষয় নিয়ে। রাষ্ট্রের বাইরে বা ঊর্ধ্বের বিষয় মানে এখন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের কথা খেয়াল রেখে তা লঙ্ঘন যাতে না হয় এভাবে কথা বলতে হবে। সোজা কথাটা হলো, জাতিসঙ্ঘ বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর কোনো সমিতি বা অ্যাসোসিয়েশন এমনটা বুঝে নিয়ে, এখানে নেয়া সবার সিদ্ধান্ত কী কোনও সদস্য রাষ্ট্রের ওপর প্রয়োগ করা যাবে? কারণ তা করতে গেলে তো ওই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘিত হবে? এজন্য, যেকোনো রাষ্ট্রের ওপর আরেক রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগুলোর কোনো সিদ্ধান্ত যেমন কার্যকর মনে করা যায় না, তেমন জাতিসঙ্ঘেরও। (তবে কিছু শর্ত সাপেক্ষে করা যায়।) কাজেই ব্যক্তিদের নিয়ে একটা সমিতি আর রাষ্ট্রগুলোর কোনো সমিতি একই ধরন বা মর্যাদার নয় বা সমতুল্য নয়। তাই, এখানে এসে রাষ্ট্র আর ব্যক্তি একাকার করে দেখা যাবে না, ভুল হবে।
তাহলে কী জাতিসঙ্ঘের সিদ্ধান্ত সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে সদস্য রাষ্ট্রের ওপর প্রযোজ্য নয় বা করা যাবে না? তাহলে হয়ে আছে কী করে? সেটা বুঝার জন্য সার্বভৌমত্ব কথাটা খেয়াল রেখে একটা কায়দা করা হয়েছে সেদিকে তাকাতে হবে। যেমন ধরা যাক, সব রাষ্ট্র বসে কোনো নতুন আন্তর্জাতিক আইন বা কনভেনশন তৈরি করলো। বাংলাদেশের প্রতিনিধি ধরা যাক তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী, শেষে ওই দলিলে স্বাক্ষর দিয়ে এলেন। এখন ওই আইন মানতে বাংলাদেশকে বাধ্য করানো কী যাবে? কারণ সে ক্ষেত্রে আমাদের দেশের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘিত হচ্ছে। এই জটিলতা এড়িয়ে যেতে বা এ থেকে বিরত থাকতে যা করা হয় তা হলো, ওই মিটিংয়ে গৃহীত ওই আইন বা কনভেনশনটাই এবার দেশে নিয়ে এসে সরাসরি আমাদের সংসদে পেশ করা হয়। যেন আমরা আমাদের সংসদে কোনো প্রস্তাব পেশ করছি এভাবে। সেই প্রস্তাব আমাদের সংসদে পাস হওয়ার পর সেটা আর জাতিসঙ্ঘের আইন বা কনভেনশন বলে বাংলাদেশ মেনে চলছে এমন নয়। সেটা আমাদের সংসদে পাস হওয়া আইন (এটাকেই র্যাটিফিকেশন বা অনুসমর্থন করে নেয়া বলে) বলেই আমরা তা মানতে বাধ্য হবো। আর এই হলো সার্বভৌমত্ব বাঁচিয়ে আর জাতিসঙ্ঘের সাথে দেশের সম্পর্ক রক্ষার সমাধান।
দ্বিতীয় পয়েন্ট : আমেরিকান প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ১৯৩৩-১৯৪৫ সালের এ সময়ে একনাগাড়ে চারবারের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ছিলেন। জাতিসঙ্ঘের আইডিয়া বা ইমাজিনেশনের উদ্গাতা মূলত তিনি। এর পেছনের কারণ, তিনি হলেন সেকালের কলোনি শাসন বিলুপ্ত করে দেয়ার পক্ষের লোক যাতে স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে আমেরিকান পুঁজিবাজারের ঋণখাতক বা ক্রেতা হয়ে ওঠে। যাতে দুনিয়ায় কলোনি দখল শাসনের চেয়ে এক বেটার স্বাধীন রাষ্ট্রের আন্তঃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কাজে তিনি যুদ্ধের বিপক্ষে বা আইন-কনভেনশন তৈরি করে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে স্বার্থ বিরোধ মীমাংসার ব্যবস্থা হিসেবে জাতিসঙ্ঘ ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ার পক্ষের লোক। কারণ যুদ্ধে পুঁজি-সম্পদ বিনষ্ট হয় মারাত্মক, এখান থেকে তিনি সরতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু সেকালে তার প্রস্তাব আমেরিকার অধস্তন হয়ে পড়া তখনকার ইউরোপ মেনে নিলেও সোভিয়েত ইউনিয়নের স্তালিন তা মানতে চাননি। স্তালিনের সোজা আপত্তির দিকটা ছিল, সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য রাষ্ট্রের ভিত্তিতে চলে এমন এক জাতিসঙ্ঘ গড়ার পর ওই প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হিসেবে আমেরিকা যদি তা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে তখন কী হবে?
আবার সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে সোভিয়েত রাষ্ট্র ওর ঊর্ধ্বে বা বাইরের কারো সিদ্ধান্ত (জাতিসঙ্ঘ বলে) কেন বাধ্য হয়ে মানবে? অতএব স্তালিন তা একেবারেই মানতে নারাজ।
এই জটিলতা সমাধান করতেই আসে ‘ভেটো’ সিস্টেমের আইডিয়া। এর সোজা মানে হলো, সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার আগেই ভেটোওয়ালারা একজনও যদি আপত্তি করে তবে সেটা সিদ্ধান্ত হতে পারবে না। সেজন্য এটা আলাদা করে নিরাপত্তা পরিষদ এখানে পাঁচ রাষ্ট্রের একটিও যদি আপত্তি করে তাতে আলোচনা প্রস্তাব বাতিল হয়ে যাবে। তবে এটা গেল ভেটো ব্যবস্থার নেগেটিভ দিক থেকে ব্যাখ্যা। উল্টা ইতিবাচক করে বলা যায়, দুনিয়ার ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখতে পাঁচটা পরাশক্তি বা বিশেষ রাষ্ট্র একমত না হলে সেটা নিয়ে এবার সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত হতে পারবে না। সবার আগে পাঁচটা বিশেষ রাষ্ট্রের একমত হওয়া, এক দিকে থাকাই মূল। এই আইডিয়া হাজির করেই রুজভেল্ট স্তালিনকে নিজের নৌকায় তুলতে পেরেছিলেন, জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়িত হয়েছিল।
এবারের সেপ্টেম্বরে মোদি নাকি খুবই সফল প্রধানমন্ত্রীর মতো জাতিসঙ্ঘে বক্তৃতা রেখেছেন। অন্তত কলকাতার আনন্দবাজারের চোখে। উগ্র হিন্দুজাতিবাদী অবস্থানের আনন্দবাজার এবার প্রকাশ্যেই হিন্দুত্ববাদের অবস্থান নিয়েছে। ভারতের সীমান্ত সঙ্ঘাতের এই ‘মোক্ষম সময়ে’ প্রধানমন্ত্রী মোদি নাকি ভারতের ‘নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ পাওয়ার দাবিটা আরো জোরালো ভাবে তুললেন’- এভাবে লিখেছে আনন্দবাজার।
কিন্তু জাতিসঙ্ঘের জন্মভিত্তি কী সেটা ভারতের কোনো রাজনীতিবিদ বুঝেছেন এমন প্রমাণ নেই। ফলে কেবল আনন্দবাজারও বোঝেনি তাও নয়। আসলে এখনো যারা ‘জাতিরাষ্ট্র চিন্তার’ রাজনীতিতে আছেন এটা তাদের বুঝের বাইরে থেকে যাবে, আমরা ধরে নিতে পারি। এছাড়াও এরা যদি হিটলারের মতো আরো উগ্র-জাতি চিন্তার হন তো কথাই নেই। যেমন ছিল জাতিসঙ্ঘে মোদির এই বক্তব্য। বাস্তবত জন্ম থেকেই ভারত জাতিসঙ্ঘ কী তা বুঝেইনি। অন্তত দুটো পয়েন্ট থেকে তা বলা যায়।
এক. জাতিসঙ্ঘ সেই পথচিহ্ন-মার্ক যখন ‘জাতিরাষ্ট্র’ ধারণার নিকৃষ্ট পরিণতি হিসেবে হিটলারের জার্মানির উত্থান ও যুদ্ধের ধ্বংসলীলা যা সারা ইউরোপ দেখেছিল। দেখে ইউরোপের ৪৫ রাষ্ট্র এক কনভেনশন ডেকে (১৯৫৩ সালে) জাতিরাষ্ট্রভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্র ত্যাগ করে অধিকারভিত্তিক ও নাগরিক বৈষম্যহীনতার প্রতিশ্রুতিতে সাম্যের রাষ্ট্র হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছিল। আর ভারতের কোনো রাজনীতির ধারাই বা রাজনীতিবিদ তা টেরও পায়নি। একাডেমিকরাও এর খবর এখনো পেয়েছেন এমন জানা যায় না। ভারতে ‘জাতীয় স্বার্থ’ কথাটা রীতিমতো দানবীয়। এই শব্দ দিয়ে আপনি প্রধানমন্ত্রী বা সম্পাদক যেকোনো ডাহা মিথ্যা বলে যেতে পারেন। জাতীয় স্বার্থের খাতিরে সব জায়েজ থাকবে। এমনকি মুসলমান বা দলিতের ওপর জুলুম অত্যাচার হত্যা সব করতে পারবেন। এই হলো বর্ণহিন্দুর চরম রেসিজমের একালের ভারত। হতে পারে এই জাতীয়স্বার্থ ভঙ্গের ভয়ে একাডেমিকেরাও ভারত জাতিরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কিছু বলতে চান না।
দুই. জাতিসঙ্ঘ জাতিরাষ্ট্র ধারণার ওপর কখনোই দাঁড়ানো নয়। এজন্য জাতিসঙ্ঘ কাশ্মিরের সমাধান করতে বলেছিল রাজার ইচ্ছা নয়, কাশ্মির ভূখ-ের বাসিন্দাদের ভোটের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়ার রায় দিয়েছিল। নেহেরু তা করেন নাই, মোদি পর্যন্তও কেউ না। সারা ভারতের রাজনীতি মনে করে হিন্দুত্ব ও জাতিরাষ্ট্র ধারণাটাই রাজনীতি।
তিন. একালে জাতিসঙ্ঘে ভেটো সদস্যপদ পাওয়ার লোভ জেগেছে ভারতের। আর তা জাগিয়েছে আমেরিকা। চীন ঠেকানোর খেপে ভারতকে নিয়োগ করার জন্য এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমেরিকা। তামাসা হলো ভারত সেটা বিশ্বাস করেছে।
ব্যাপার হলো, ভেটো সদস্যপদ দেয় কে? এটা ভারতের আর জানাই হলো না। একালে মোদিও তাই বলছেন, ‘আর কত দিন রাষ্ট্রপুঞ্জের সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রক্রিয়ার বাইরে থাকবে ভারত?।’ কিন্তু মোদি এটা কার কাছে চাচ্ছেন? জাতিসঙ্ঘ না আমেরিকা নাকি চীন?
প্রথম কথা, এটা রাষ্ট্রের মুরোদের প্রশ্ন যে কে কাকে সদস্যপদ দিতে পারে। আমেরিকার সে মুরোদ সত্তর বছর পরে এখন প্রায় শুকিয়ে আসছে। এটা বুঝা কী খুব কঠিন? দ্বিতীয়ত ভেটো সদস্যের পাঁচ দেশের তালিকা বদলাবে না যতক্ষণ না নতুন গ্লোবাল নেতা কেউ আসছে। এটা হবে তার ইচ্ছা এখতিয়ার। তার সাথে অন্যদের সম্পর্কের মাত্রার ওপর নির্ভর করবে আর কোন রাষ্ট্র নতুন করে ভেটো ক্ষমতা পাবে। যদি সে নেতা চীন হয়, তবে তাই।
আজকের ভারত এই হিন্দুত্ববাদী হিটলারকে চীন কেন সদস্যপদ দিতে যাবে, না অন্য কেউ দেবে? আর তবু সেজন্য অন্তত কিছু রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও কমিটমেন্ট তো ভারতের লাগবে! কেবল হিন্দুত্বের জন্য যে ভারত নিজ দেশের অন্যান্য নাগরিকের প্রতি বৈষম্যহীন আচরণ করতে পারে না সেই ভারতকে কে এবং কেন ভেটো সদস্যপদে টেনে তুলবে?
আবার মোদির ধারণা দেখেন, তিনি বক্তৃতায় বলেছেন, ‘জাতিসঙ্ঘ এবং ভারতের মূল আদর্শ নাকি এক।’ ‘বসুধৈব কুটুম্বকম (গোটা বিশ্বই আত্মীয়) এই মন্ত্র রাষ্ট্রপুঞ্জের সভায় বার বার’ নাকি জাতিসঙ্ঘে উচ্চারিত হয়ে থাকে। অথচ মোদির ভারত হলো এমন, যে হিন্দু নয় বা যার হিন্দুত্ব নেই এমন কাউকে সে সহ্য করতে পারে না। সেই মোদি এমন ফাঁপা আওয়াজ দিচ্ছে।
দেখা যাচ্ছে এটাই ভারতের জাতিসঙ্ঘ রিডিং!
লেখক : রাজনৈতিক বিশ্লেষক
goutamdas1958@hotmail.com