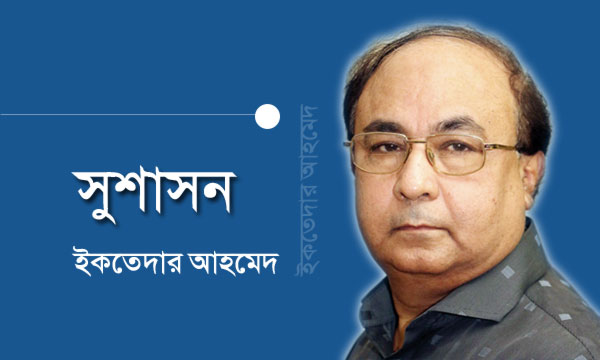- ইকতেদার আহমেদ
- ১৪ জুন ২০২১
গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা যেসব মৌলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত এর মধ্যে অন্যতম আইনের শাসন এবং দ্রুত ও সুবিচার। বাংলাদেশের সংবিধানের বিভিন্ন স্থানে এসব বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবকে বলা হয় এর প্রাণ। গণতন্ত্র ও আইনের শাসন বিষয়ে সংবিধানের প্রস্তাবনায় সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ রয়েছে, রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা; যেখানে সব নাগরিকের আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে।
আমাদের বিচারব্যবস্থায় ফৌজদারি ও দেওয়ানি দুই ধরনের আদালত রয়েছে। জেলা পর্যায়ে বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটরা এককভাবে শুধু ফৌজদারি মামলার বিচারকাজ সম্পন্ন করেন। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের ভ্রাম্যমাণ আদালত আইনের অধীন কিছু ফৌজদারি অপরাধ সংক্ষিপ্ত বিচারের মাধ্যমে নিষ্পত্তির অধিকার দেয়া হয়েছে। ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর পরবর্তী বিচার বিভাগের সহকারী জজ পদমর্যাদায় কর্মরত বিচারকরা প্রাথমিক পর্যায়ে বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন করেন। ১ নভেম্বর ২০০৭ তারিখের আগে দায়িত্বটি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার কর্মকর্তারা পালন করতেন।
সহকারী জজ ও সিনিয়র সহকারী জজরা নিজ বিভাগে স্বতন্ত্র অস্তিত্বসম্পন্ন পদে কর্মরত থাকাকালীন শুধু দেওয়ানি মামলার বিচারকার্য সম্পন্ন করেন। প্রসঙ্গত, ম্যাজিস্ট্রেট নামের স্বতন্ত্র অস্তিত্বসম্পন্ন কোনো পদ নেই। বিচার বিভাগের যুগ্ম জেলা জজ পদমর্যাদার কর্মকর্তারা দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় মামলার বিচারকাজ সম্পন্ন করেন। যুগ্ম জেলা জজরা ফৌজদারি মামলার বিচারকার্য সম্পন্ন করার সময় তাদের সহকারী দায়রা জজ নামে অভিহিত করা হয়। অনুরূপভাবে অতিরিক্ত জেলা জজ ও জেলা জজরাও ফৌজদারি ও দেওয়ানি উভয় ধরনের মামলার বিচারকাজ সম্পন্ন করেন। অতিরিক্ত জেলা জজ ও জেলা জজরা ফৌজদারি মামলার বিচারকালে অতিরিক্ত দায়রা জজ ও দায়রা জজ নামে অভিহিত হন।
বাংলাদেশের সংবিধানে যে বিচার বিভাগের উল্লেখ রয়েছে; তা উচ্চাদালত ও অধস্তন আদালত সমন্বয়ে গঠিত। সংবিধানে উচ্চাদালত শব্দটি উল্লিখিত না হলেও উচ্চাদালত বলতে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগকে বোঝায়। অন্য দিকে অধস্তন আদালত বলতে সহকারী জজ হতে জেলা জজ পর্যন্ত পদগুলো বোঝায়। সুপ্রিম কোর্টের স্থায়ী আসন রাজধানী শহর ঢাকায় স্থিত হয়। হ্ইাকোর্ট বিভাগের অধিবেশন দেশের অপর যেকোনো স্থানে অনুষ্ঠানের বিধান রয়েছে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে প্রধান বিচারপতি দেশের অন্যত্র হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে পারেন। একসময় সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, যশোর ও সিলেটে হাইকোর্ট বিভাগের ছয়টি স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন করা হয়েছিল। পরে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীকে এখতিয়ারবহির্ভূত ও অকার্যকর ঘোষণা করলে স্থায়ী বেঞ্চগুলোর পুনঃঢাকায় প্রত্যাবর্তন করানো হয়।
বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির অভ্যুদয়ের সময় দেশের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি। ওই সময় সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে যত মামলা বিচারাধীন ছিল বর্তমানে তার সংখ্যা অনেক বেশি। সংবিধানে হাইকোর্ট বিভাগকে ১০২ অনুচ্ছেদের অধীন প্রদত্ত ক্ষমতার হানি না ঘটিয়ে সংসদ প্রণীত আইন দিয়ে অন্য কোনো আদালতকে তার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক যেসব ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়; এর সব বা যেকোনো ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষমতা দান করার বিষয় উল্লেখ রয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত এরূপ আইন প্রণয়ন করে অপর কোনো আদালতকে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত সব বা যেকোনো ক্ষমতা দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়নি।
দ্রুত ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তি দেশের একজন নাগরিকের মৌলিক অধিকার। ফৌজদারি অপরাধ বিষয়ে সংবিধানে বলা আছে ফৌজদারি অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচার লাভের অধিকারী হবেন। দেওয়ানি বিচার বিষয়ে পৃথকভাবে এ-সংক্রান্ত কোনো কিছু উল্লেখ না থাকলেও দ্রুত বিচার প্রাপ্তি আইনের শাসন ও সুবিচারের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এর নিশ্চিতের দায়িত্ব রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি সবার ওপর বর্তায়।
দেশে উচ্চাদালতের আপিল ও হাইকোর্ট বিভাগে বিচারক ও বেঞ্চের সংখ্যা এবং জেলাপর্যায়ে আদালতের সংখ্যা বাড়িয়ে ফৌজদারি ও দেওয়ানি উভয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির পদক্ষেপ নিলেও এখনো বিচারপ্রার্থীদের তা পর্যন্ত সুফল দিতে পারেনি।
সংসদে প্রদত্ত আইনমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে জানা যায়, বর্তমানে দেশের বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ৩৩ লাখের বেশি। জেলা জজ হতে সহকারী জজ অবধি আদালতগুলোতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ২৮ লক্ষাধিক। আর হাইকোর্ট বিভাগে প্রায় পাঁচ লাখ। আপিল বিভাগে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ১৬ হাজারের বেশি।
বাংলাদেশের বিভিন্ন আদালতে এমন অনেক মামলা রয়েছে; যেগুলো হেতুবিহীন এবং পরিণামে যেকোনো পক্ষের জন্য হয়রানির কারণ হয়ে অহেতুক আর্থিক, মানসিক ও দৈহিক ক্ষতি ঘটায়।
অধস্তন আদালতে যেসব ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলা দায়ের হয়, এগুলো যথাযথ কারণবিহীন হয়ে থাকলে এবং দাবির সপক্ষে বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণ না থাকলে প্রাথমিক শুনানি অন্তে নিষ্পত্তির বিধান রয়েছে। তবে তা যথাযথভাবে প্রতিপালন না হওয়ায় মামলার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা পর্যালোচনায় দেখা যায়, একটি আদালতে বছরে যে সংখ্যক মামলা নিষ্পত্তি হয়; বেশির ভাগ আদালতের ক্ষেত্রেই দায়ের করা মামলার সংখ্যা তার চেয়ে বেশি। এভাবে বিভিন্ন আদালতে মামলা পুঞ্জীভূত হতে দেখা যায়।
মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিচারকদের পাশাপাশি আইনজীবীদের ভূমিকা অপরিসীম। আইনজীবীরা মামলা দায়েরকালীন যদিও অনুধাবনে সক্ষম যে, মামলাটি চূড়ান্ত বিচারে ফলদায়ক হবে কী হবে না। তবু অনেক আইনজীবী মামলা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মামলা দায়েরের অভিপ্রায় ব্যক্ত করার পর এর চূড়ান্ত পরিণতির বিষয়টি বিবেচনায় নেন না। মামলাটি দায়ের করে ফেলেন। এমন মামলা দায়ের পর দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর যখন মামলাসংশ্লিষ্ট পক্ষ কোনো সুফল প্রাপ্তির আশা দেখতে পান না; তখন অনেকের পেছনে ফিরে তাকানোর সুযোগ থাকে না।
বেশির ভাগ উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিচার প্রশাসন ও মামলা ব্যবস্থাপনার উন্নতি করে এর সংখ্যা দ্রæত কমিয়ে আদালতের জন্য সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। এসব রাষ্ট্রে প্রতি বছর যত মামলা দায়ের হয়; তা সেসর দেশের আদালতগুলো নির্ধারিত বছরেই নিষ্পত্তিতে সক্ষম। এরূপ অনেক দেশে বিকল্প পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তির বিধানের প্রচলন রয়েছে। বিকল্প পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সর্বাধিক জনপ্রিয় যে দু’টি পদ্ধতি এর একটি হলো মধ্যস্থতা এবং অপরটি সালিস। আমাদের দেশে কিছু মামলার ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা ও সালিসের বিধান রয়েছে। তবে সংশ্লিষ্ট সবার আন্তরিকতার অভাবে এর সুফল হতে মামলা সংশ্লিষ্ট অনেকেই বঞ্চিত।
আমাদের ফৌজদারি মামলার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, অভিযুক্ত ব্যক্তির খালাসের মধ্য দিয়ে মামলার নিষ্পত্তি হয়। ফৌজদারি অপরাধ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত। এ কারণে বেশির ভাগ ফৌজদারি অপরাধের বিচার পরিচালনার দায়িত্ব রাষ্ট্র পালন করে। রাষ্ট্র নিয়োজিত কৌঁসুলি এসব মামলা রাষ্ট্রের পক্ষে পরিচালনা করেন। যেসব ফৌজদারি মামলার এজাহার দায়েরের মাধ্যমে উদ্ভব ঘটে; এসব মামলার তদন্তকাজ রাষ্ট্রের পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন পদবির কর্মকর্তারা পরিচালনা করেন। এরা সবাই প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী। জনগণের প্রদত্ত কর থেকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে রক্ষিত অর্থে এদের বেতনভাতা ও সুবিধাদি দেয়া হয়। প্রজাতন্ত্রের যেকোনো কর্মচারীর কর্তব্য জনসাধারণকে নিঃস্বার্থ সেবা দেয়া। মামলার তদন্তকাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা ঠিকভাবে তদন্ত করলে বেশির ভাগ মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির খালাসের অবকাশ নেই। যেকোনো মামলা দীর্ঘ দিন চলার পর খালাসের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হলে তদন্তকাজ ও বিচার পরিচালনায় রাষ্ট্রের যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়; তা জনগণ প্রদত্ত করের অর্থের অপচয় বৈ আর কিছু নয়। পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্রগুলোতে দেখা যায়, মামলায় অভিযোগ গঠন-পরবর্তী প্রায় শতভাগ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদানের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়।
মামলার তদন্ত ও বিচারের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই দেশের দায়িত্বশীল নাগরিক। তাদের সবার নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশ ও জাতির প্রতি কর্তব্য রয়েছে। যেসব মামলা পক্ষদ্বয়ের জন্য ফলদায়ক নয়; তা যেন দায়ের না হয় এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে আইনজীবীদের। পাশাপাশি মামলা তদন্তে সংশ্লিষ্ট পুলিশ, পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট কৌঁসুলি এবং বিচারকাজে নিয়োজিত বিভিন্ন পর্যায়ের বিচারকরা যদি আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাথমিক শুনানি অন্তে হেতুবিহীন ও বস্তুনিষ্ঠ নয় এমন সব মামলা নিষ্পত্তি করেন, সে ক্ষেত্রে বর্তমানে মামলার ভারে জর্জরিত আদালতগুলোর কাঁধ থেকে বিচারাধীন মামলার বোঝা লাঘব হবে। এ ছাড়া মামলার ক্রমপুঞ্জীভূত হওয়ার অবসান হবে। এগুলোর নিশ্চয়তা বিধান করা গেলে আশা করা যায় দ্রুত বিচার প্রাপ্তির বাধাগুলো অপসারণ হবে।
লেখক : সাবেক জজ, সংবিধান, রাজনীতি ও অর্থনীতি বিশ্লেষক
E-mail: iktederahmed@yahoo.com