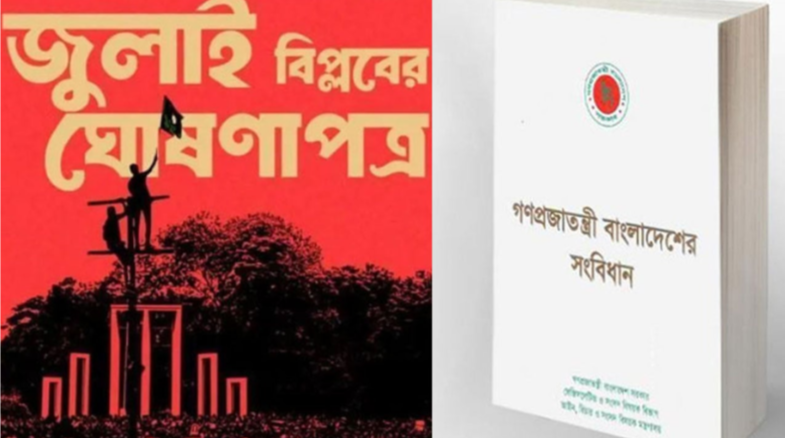চব্বিশের জুলাই অভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যাতে এক হাজার চারশ’রও বেশি শহীদ এবং ২০ হাজারেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। জুলাই ঘোষণাপত্র বা জুলাই সনদ হলো সেই দলিল যেখানে এই বিপ্লবের শহীদ ও আহতদের ত্যাগের ইতিহাস লেখা থাকবে, যা এদেশের ছাত্র-জনতার এক অবিস্মরণীয় উপাখ্যান। আর এই উপাখ্যান শুধু শহীদদের এবং আহতদের বীরোচিত গল্পই নয়, বরং তাদের এই বীরত্বগাথা বর্তমান প্রজন্মের জন্য একটি উদাহরণ এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা। একই সঙ্গে ভবিষ্যতের ফ্যাসিস্টদের জন্য এটি একটি চরম সতর্কবার্তা।
বাংলাদেশের রাজনীতিতে স্বার্থপরতা ও প্রতিহিংসাপরায়ণতার অসংখ্য ঘটনা অতীতে ঘটেছে। সংবিধান আর আইনের গ্যাঁড়াকলে ফেলে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নির্মূল করার ইতিহাস আমাদের সামনেই আছে। সেজন্যই ২০২৪ সালের মুক্তির নায়কেরা যাতে ভবিষ্যতে কোনো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতিহিংসার শিকার না হন, তা এখনই নিশ্চিত করতে হবে। এজন্যই জুলাই সনদকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তোলা হয়েছে। এটি না করলে জুলাই বিপ্লবের নেতা-কর্মীদের জন্য সাধারণ আইনের অধীনে দমনমূলক মামলা (যেমন রাষ্ট্রদ্রোহ বা সেডিশন চার্জ) এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ঝুঁকি বাড়বে, যা ১৯৭৫ সালের আগস্ট বিপ্লবের নেতাদের ভাগ্যে ঘটেছে।
সংবিধানের ৭ম, ৩৯তম, ১৪২তম ও ৭খ অনুচ্ছেদের আলোকে ভবিষ্যতে জুলাই বিপ্লবের নায়কদের প্রধান ঝুঁকিগুলো হচ্ছে—
১. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : ১৯৭৫ সালের আগস্ট বিপ্লবের নায়কদের করুণ পরিণতির পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা থেকে যাবে। ১৫ আগস্ট সামরিক অভ্যুত্থানে শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন। এই বিপ্লবকে প্রথমে ‘ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স’ (১৯৭৫) দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়, যা অভ্যুত্থানকারীদের ক্ষমা ও নিরাপত্তা দেয়। কিন্তু ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে এই অর্ডিন্যান্স বাতিল করে এবং অভ্যুত্থানে জড়িত সেনা কর্মকর্তাদের বিচার শুরু করে। বিচারে অভ্যুত্থানের প্রধান নেতা কর্নেল ফারুক রহমানসহ ১২ জনের মৃত্যুদণ্ড হয় (২০১০ সালে কার্যকর)।
এ থেকে স্পষ্ট যে, যেকোনো বিপ্লবকে সাধারণ আইনের অধীনে ‘অপরাধ’ বলে চিত্রিত করা যায়, যদি সেটি সংবিধানে সুরক্ষিত না করা হয়। সংবিধানে জুলাই ঘোষণাপত্র অন্তর্ভুক্ত না করলে ভবিষ্যতের কোনো সরকার (যেমন আওয়ামী লীগের আবার ক্ষমতায় আসা) একইভাবে জুলাই বিপ্লবকে ‘রাষ্ট্রবিরোধী’ কর্মকাণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করে এর সঙ্গে জড়িতদের বিচারের আওতায় আনতে পারে।
২. সাংবিধানিক কাঠামোতে সুরক্ষার অভাবে ঝুঁকি বৃদ্ধি : বাংলাদেশের সংবিধান (১৯৭২) বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে সরাসরি সুরক্ষা দেয় না। এটি নির্ভর করে সাধারণ আইনের ওপর, যা সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পরিবর্তনযোগ্য।
প্রধান ধারা : ধারা ৩৯ (বাকস্বাধীনতা) সবাইকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দেয়, কিন্তু ‘যুক্তিসংগত বিধিনিষেধ’ (যেমন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা) থাকতে পারে। এটি বিপ্লবকে ‘সমালোচনা’ হিসেবে দেখতে পারে, কিন্তু সশস্ত্র বা গণ-অভ্যুত্থানকে সুরক্ষা দেয় না।
ধারা ৭খ (সংবিধানের বাতিল বা স্থগিতকরণ অপরাধ) : সংবিধানের অবরোধকে ‘রাষ্ট্রদ্রোহ’ বলে, যা জুলাই বিপ্লবকে ‘সংবিধানবিরোধী’ বলে চিত্রিত করতে সাহায্য করবে।
ধারা ১৪২ (সংশোধন) : সংবিধান সংশোধন শুধু সংসদের দ্বারা, দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায়। জুলাই ঘোষণাপত্রকে ‘কনস্টিটিউশনাল অর্ডার’ দিয়ে চাপিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব (ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে) বিতর্কিত, কারণ এটি ‘বেসিক স্ট্রাকচার ডকট্রিন’-এর ফাঁদে পড়লে (যেমন ৫ম/৭ম সংশোধন মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়) তা সংবিধান লঙ্ঘনের কাতারে পড়তে পারে।
জুলাই ঘোষণাপত্রকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করলে (যেমন প্রস্তাবনা বা নতুন অধ্যায় হিসেবে), এটি ‘মৌলিক নীতি’ হয়ে উঠবে, যা পরিবর্তনযোগ্য নয় এবং বিচারিক সুরক্ষাও পাবে। না হলে এটি শুধু একটি ‘পলিটিক্যাল ডকুমেন্টই’ থেকে যাবে, যা ভবিষ্যতে আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে।
৩. জুলাই বিপ্লবীদের প্রধান ঝুঁকিগুলো : জুলাই ঘোষণাপত্র সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত না করলে বিপ্লবকে ‘অপরাধমূলক’ কাজ হিসেবে দেখানো সহজ হয়ে যাবে। এর ফলে নিম্নলিখিত ঝুঁকি দেখা দেবে—
- রাষ্ট্রদ্রোহ এবং বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগের ঝুঁকি : পেনাল কোডের ধারা ১২৪(ক) অনুসারে, সরকারের প্রতি ‘ঘৃণা বা অবজ্ঞা’ সৃষ্টি করলে তিন বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা হয়। জুলাই বিপ্লবকে ‘সরকারবিরোধী গণ-অভ্যুত্থান’ হিসেবে চিত্রিত করে এই ধারা ব্যবহার করা যাবে। এরই মধ্যে ২০২৪ সালের নভেম্বরে জুলাই আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। ১৯৭৫ সালের মতো ভবিষ্যতে পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া সরকার এই অভিযোগ দিয়ে নেতাদের গ্রেপ্তার করতে পারে।
- ক্ষমা বা ইমিউনিটির অভাব : সংবিধানে জুলাই সনদ অন্তর্ভুক্ত না হলে বিপ্লবীদের কাজকে ‘আইনি সুরক্ষা’ দেওয়া যাবে না। ১৯৭৫ সালের ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্সের মতো কোনো অস্থায়ী সুরক্ষা স্থায়ী নয়, সংসদ এটি কলমের এক খোঁচায় বাতিল করতে পারে। ফলে নেতারা (যেমন ছাত্রনেতা বা সাধারণ অংশগ্রহণকারী) মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মুখোমুখি হতে পারেন, যেমন ১৯৯৬ সালের ট্রায়ালে হয়েছে।
- রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঝুঁকি : সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার বিপ্লবকে ‘অবৈধ’ বলে ঘোষণা করে স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট বা অ্যান্টি-টেরোরিজম আইন ব্যবহার করতে পারে। এতে গ্রেপ্তার, নির্যাতন বা জোরপূর্বক গুম হওয়ার ঝুঁকি বাড়বে, যা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্টে এরই মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে। জুলাই বিপ্লবের পাঁচ লাখেরও বেশি অভিযোগীকে টার্গেট করা যেতে পারে।
- বিচারিক এবং আইনি অস্থিরতা : ‘বেসিক স্ট্রাকচার ডকট্রিন’ অনুসারে, সংবিধানের মূল অংশ (যেমন গণতন্ত্র, মানবাধিকার) পরিবর্তনযোগ্য নয়। কিন্তু জুলাই ঘোষণাপত্র ছাড়া বিপ্লবকে ‘সংবিধানবিরোধী’ বলে চ্যালেঞ্জ করা যাবে, যা সুপ্রিম কোর্টে মামলায় পরিণত হবে। এতে বিপ্লবের নেতাদের দীর্ঘমেয়াদি আইনি লড়াইয়ে পড়তে হবে এবং রাজনৈতিকভাবে দুর্বলতা তৈরি হবে।
৪. জুলাই সনদ সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির সুবিধা ও সুপারিশ : জুলাই ঘোষণাপত্রকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করলে এটি ‘প্রস্তাবনার মতো’ হয়ে উঠবে, যা বিপ্লবকে ‘জাতীয় ঐতিহ্য’ হিসেবে সুরক্ষিত করবে এবং ভবিষ্যতের স্বৈরাচার রোধ করবে। বিতর্ক সত্ত্বেও (যেমন বিএনপির বিরোধিতা), রেফারেন্ডাম বা কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির মাধ্যমে এটি সম্ভব। ইন্টারিম গভর্নমেন্টকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে সংসদীয় নির্বাচনের আগে এটি নিশ্চিত হয়।
সতর্কবার্তা : ১৯৭৫ সালের পুনরাবৃত্তি এড়াতে জুলাই ঘোষণাপত্রের সাংবিধানিক সুরক্ষা অপরিহার্য। তাছাড়া রাজনৈতিক জিঘাংসা এদেশে নতুন কিছু নয়। জুলাই সনদের সংবিধানে সন্নিবেশ করার বিপক্ষে যারা, তাদের মনে রাখতে হবে, জুলাই সনদকে সংবিধানের নিরাপত্তা না দিলে ছাত্র-যুবক-জনতার রক্তদান বৃথা যাবে।
জীবন বাজি রেখে যারা দেশকে ফ্যাসিস্টমুক্ত করেছেন, তাদের দেশবাসী ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে দেখবে, এই দুঃস্বপ্ন এদেশে আর না আসুক—সেটাই জুলাই বিপ্লবের সব শহীদ ও আহতদের পরিবার ও দেশবাসীর চাওয়া অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে।
লেখক : সাবেক সেনা কর্মকর্তা